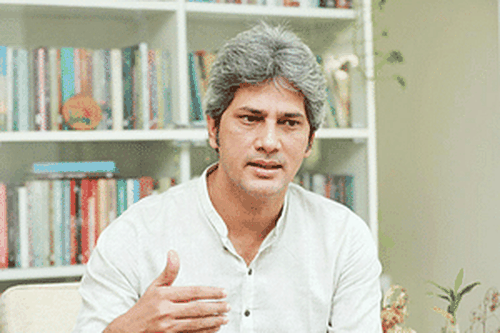
ক্ষমতায় থেকে রাজনৈতিক দল গঠন মানুষ ভালোভাবে নেয় না
একদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিশনগুলো তাদের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে এনেছে। অন্যদিকে জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র দেওয়ার দাবি করছেন শিক্ষার্থীরা। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে কী মনে হচ্ছে?
জোনায়েদ সাকি: অসাধারণ আত্মত্যাগ ও রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে একটা অভ্যুত্থান হয়েছে। এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশে একটা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছে। অভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, তার কাজ হচ্ছে, একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক উত্তরণপ্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে সহায়তা করা। নতুন বন্দোবস্ত বলি, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর বলি, সংস্কার বলি, সেটা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলোকেই সেটা করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের সংস্কার হতে পারে, সে বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে।
আমরা এখন পর্যন্ত মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার সঠিক পথে আছে। কমিশনগুলো থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেলেই অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করবেন বলে তারা বলেছেন। আমরা আশা করি, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সহ সংস্কারের একটা রোডম্যাপ দ্রুত তৈরি হবে।
অন্যদিকে জুলাই অভ্যুত্থানের একটা ঘোষণা নিয়ে কথা উঠেছে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে। অভ্যুত্থানের পরপরই এটা নিয়ে আলাপ শুরু হয়েছিল। সে সময় অভ্যুত্থানের ঘোষণার বিষয়টি বেশি দূর না এগোলেও ডিসেম্বরের শেষে এসে শিক্ষার্থীরা একটা ঘোষণা তৈরির ব্যাপারে নিজেরা উদ্যোগ নেয়। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘোষণাপত্র তৈরির দায়িত্ব নিয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের যে প্রেক্ষাপট ও এর মধ্য দিয়ে যে জন–আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে এবং এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য যে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। অভ্যুত্থানের সব অংশীজন বা পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ঘোষণা তৈরি হওয়া শ্রেয়।
অভ্যুত্থানের একটা বড় স্পিরিট অন্তর্ভুক্তিমূলকতা, বহুত্ববাদ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমরা দেখছি, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক স্বরগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বাদ পড়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আক্রান্তও হচ্ছে। অভ্যুত্থানের স্পিরিটের সঙ্গে এটা কি সাংঘর্ষিক নয়?
জোনায়েদ সাকি: জুলাই অভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, তার সঙ্গে এগুলো সরাসরি সাংঘর্ষিক। প্রতিটি বড় আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রবণতা থাকে। একটা প্রবণতা থাকে গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে ইতিবাচক একটা দিকে যাওয়া। অন্যদিকে আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছিল, যেসব প্রবণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছিল, বিপরীত পক্ষ হিসেবে কেউ কেউ সেই চর্চাগুলোকেই সামনে নিয়ে আসে। অভ্যুত্থান একটা গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষাকে সামনে এনেছে। মানুষ আশা করছে এমন একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা পাবে যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জীবনচর্চা, লিঙ্গীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে প্রত্যেকে নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং রাষ্ট্র তার নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার গ্যারান্টি দেবে।
অন্যদিকে আমরা দেখছি, নানা ধরনের উগ্রতার একটা প্রকাশ ঘটছে। অভ্যুত্থান–পরবর্তী যে রাজনৈতিক বাস্তবতা, সেটাকে কাজে লাগিয়ে একটা গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে। মাজারের ওপর হামলা হচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়, পাহাড়ের বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হচ্ছে, নারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, এটা সত্যি। একই সঙ্গে আবার এ ঘটনাগুলোকে সংখ্যায় অনেক দেখিয়ে, অনেক রং চড়িয়ে, সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। এখানে আমরা পতিত ফ্যাস্টিস্টদের ভূমিকা দেখছি; আবার ভারতের মিডিয়ার একাংশ ও তাদের শাসক দলের দিক থেকেও এ প্রচারণা দেখছি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- রাজনৈতিক দল
- রাজনীতি
- গণঅভ্যুত্থান


