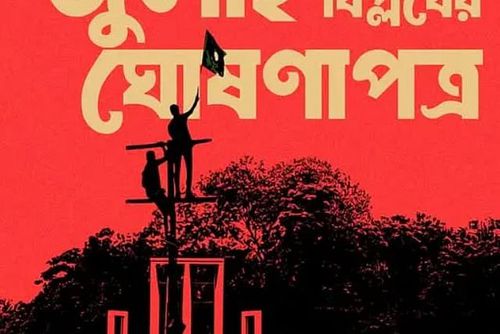
‘বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে’ নিম্নবর্গের চাওয়া কি পাত্তা পাবে?
জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতা যে প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে পাল্টে দিয়েছে, তাকে কী নামে ডাকা উচিত, তা নিয়ে ভ্রান্তি আছে। বিভ্রান্তি আছে। এই পরিবর্তনপ্রক্রিয়ার প্রথম পক্ষ ছিল একটি ফ্যাসিবাদী সরকার। দ্বিতীয় পক্ষ ছিল ছাত্র–জনতা। কিন্তু এখন দৃশ্যত সেই দ্বিতীয় পক্ষ বা বৃহত্তর পক্ষ তথা জনগণকে দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তনপ্রক্রিয়ার ঠিক অংশীজন বলে মনে হচ্ছে না।
তা না হলে সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বোঝাতে ‘বিপ্লব’ শব্দটি ব্যবহার করতে এত অনীহা থাকবে কেন?
সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শহুরে শ্রমজীবী, নিম্ন আয়ের মানুষ, সচেতন গ্রামবাসী, পদহীন রাজনৈতিক কর্মী, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠতার পক্ষের অ্যাকটিভিস্ট এবং একই সঙ্গে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তানেরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাকে ‘অভ্যুত্থান’ বললে তা তো কেবল তিন সপ্তাহের ঘটনার একটি সংকীর্ণ ফ্রেমে আটকা পড়ে যায়। এটিকে পরিকল্পিতভাবে বিপ্লব না বলে অভ্যুত্থান বলা হচ্ছে বলে যে কারও সন্দেহ হতে পারে। মনে হতে পারে, সাড়ে ১১ বছরের গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকারের সংগ্রাম, লাখো মানুষের ভোগান্তি ও ত্যাগ এবং গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনো ছাপ যাতে এই সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় না থাকে, সে জন্য এটিকে ‘অভ্যুত্থান’ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
অনেকে ভাবতে পারেন ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীরা তো হয় রাজা-রানি এবং আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রনায়ক, ধনকুবের ও এলিটরা। সেখানে নিম্নবর্গের (সাবঅল্টার্ন) মানুষের জায়গা কোথায়?
আছে, জায়গা আছে বন্ধুরা। গত দেড় হাজার বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংস্কার ও পরিবর্তন এবং শিল্পবিপ্লব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সর্বশেষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অগ্রগতিতে ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এরাই সম্মিলিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে হাসিনার আরোপিত অন্যায়-অবিচারের ফ্যাসিবাদী আওয়ামী ব্যবস্থাকে।
তার পরও বাংলাদেশে বিপ্লব সংঘটিত করানো জনতাকে রাষ্ট্র পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা একটু মুশকিলই। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক দলগুলো, ছাত্র নেতৃত্ব এবং সিভিল সোসাইটির বাইরে কারও কণ্ঠস্বর ততটা উচ্চকিত নয়।

তাই জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের বিলম্বিত ইশতেহার বা ঘোষণাপত্র প্রদানের দাবি যখন সামনে এসেছে, তখন দেখা যাচ্ছে, জনতা ইতিমধ্যেই বাড়ি ফিরে গেছে।
সাধারণ মানুষ যা চেয়েছিল, ঘোষণাপত্রে তার প্রতিফলন ঘটানোর দায়িত্ব এখন তাহলে কার বা কাদের?
মানুষ নির্দ্বিধায় রক্ত দিয়েছে শুধু ব্যক্তি হাসিনার যথেচ্ছাচার শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওই ধাঁচের আরেকটি ব্যবস্থা কায়েমের জন্য নয়।
সাংবিধানিক ব্যবস্থার সংস্কার, ক্ষমতার ভারসাম্য, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, নাগরিক অধিকার সুসংহতকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, এ–জাতীয় কঠিন কঠিন কথা যত বেশি উচ্চারিত হবে, বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ততই সাধারণ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে এবং কাগজের লেখা কাগজেই থেকে যাবে।
ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, চীনা কমিউনিস্ট বিপ্লব বা ইরানি ইসলামিক বিপ্লব—ওই দেশগুলোর জনগণের চেতনা এবং সে সময়ের আকাঙ্ক্ষা মোটামুটিভাবে ধারণা করতে পেরেছিল বলেই তখন সাফল্য পেয়েছিল।
তাই বলে ওই সব বিপ্লবের সাহিত্য থেকে ‘এ ধারকা মাল ওধার’ করে ২০২৪-এর বাংলাদেশ বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রতিস্থাপিত করলে কতটা যথাযথ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ না থাকার কারণ নেই।
‘প্রজাতন্ত্র’ ও ‘প্রধানমন্ত্রীর’ মতো নিত্যব্যবহার্য শব্দেরও নিহিতার্থ আমাদের অনেকের কাছেই যেমন বোধগম্য নয়; তেমনি সময়ের পরিক্রমায় এসব শব্দের প্রাসঙ্গিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ। আজকের জনগণ নিজেদের ‘প্রজা’ মানতে চাইবে না কারণ, রাজার যুগ অস্ত গেছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজের পরিধিও প্রধান মন্ত্রকের ভূমিকাসদৃশ নেই। ঔপনিবেশিক আমলের ‘শাসন’-এর ধারণাও আজ একেবারেই অচল।
গত ৩১ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যে ঘোষণাপত্র ঘোষণা করতে যাচ্ছিল, তা হয়তো তাদের তারুণ্যের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হতো।
- ট্যাগ:
- মতামত
- গণঅভ্যুত্থান
- ঘোষণাপত্র


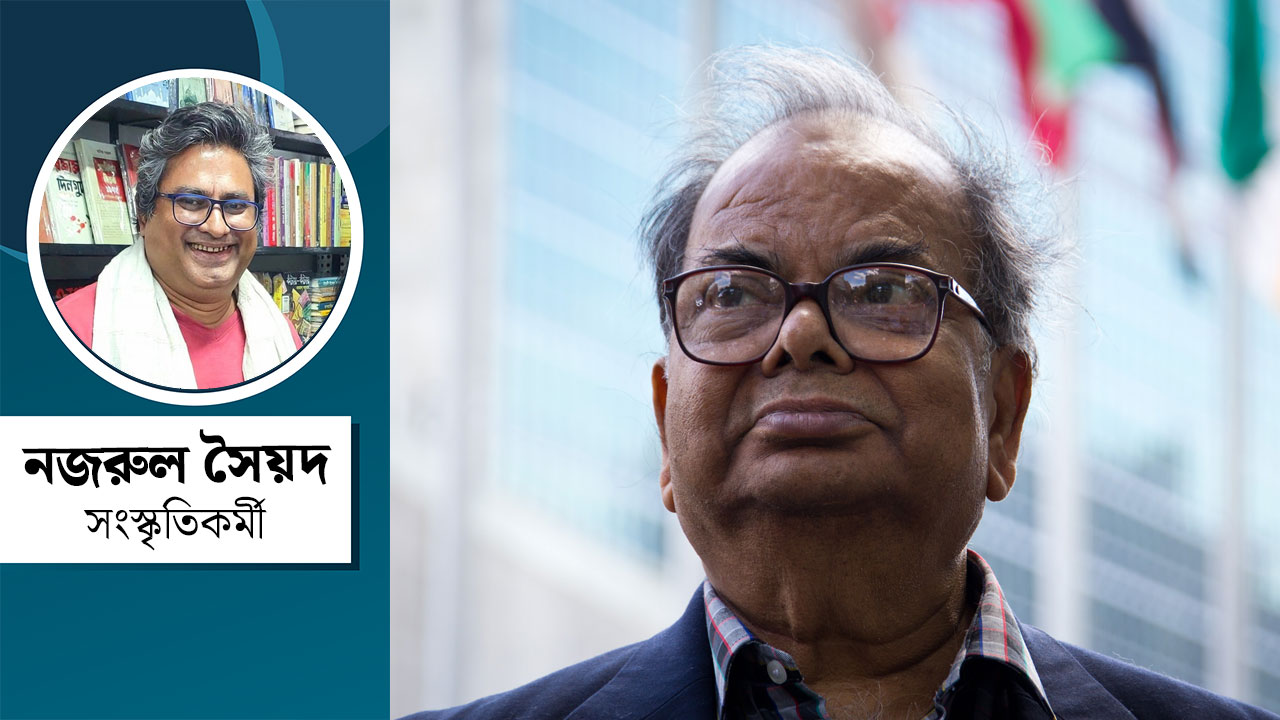
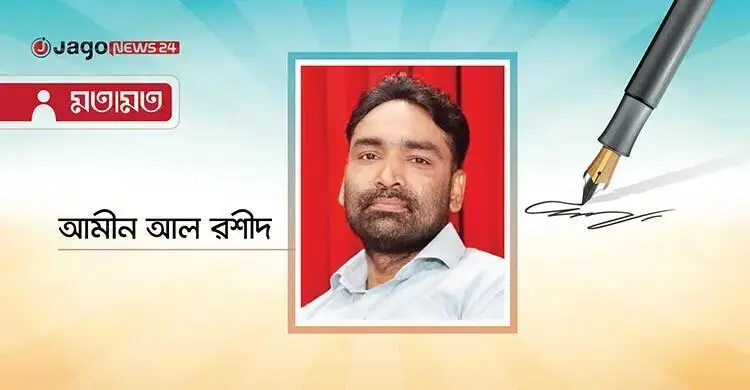

-699b8e6511dac.jpg)









