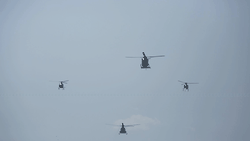ছবি সংগৃহীত
বিয়ের বয়স সমাচার
প্রকাশিত: ২৩ অক্টোবর ২০১৪, ০৬:৫৭
আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০১৪, ০৬:৫৭
আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০১৪, ০৬:৫৭
(সাপ্তাহিক ‘সাপ্তাহিক’) - কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হবার নীতি সামাজিক এবং ধর্মজাত। এসব সংস্কার বা রীতি মেনেই সুধী সমাজ চলেছেন। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু এই রীতি আধুনিক শিক্ষা এবং আধুনিক জীবন যাপনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা নারীর অধিকার এমনকি মানুষের অধিকার, তার উন্নততর জীবনেরও নানান নতুন ধারা তৈরি করেছি। নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছি। সে বিবেচনায় মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানো খুব যৌক্তিক কোনো কর্ম নয়। সামাজিক, ধর্মীয় এসব রীতি এক অর্থে নারীকে পেছনে টেনেছে। ইতিহাসের লড়াইটা ছিল, সেই রীতির গতিপথ আটকে ভবিষ্যৎমুখীন হবার। মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর চেষ্টা, সেই ভবিষ্যৎমুখী চাকাকে আবার পেছনে ঠেলার নামান্তর।
‘আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার-তের বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, ‘তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।’ রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরুব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাত বছর বয়সে মারা যান। তারপর, সে আমার মা’র কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়। ... যদিও আমাদের বিবাহ হয়েছে ছোটবেলায়। ১৯৪২ সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়’।-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত বছর বয়স পর্যন্ত কাউকে শিশু গণ্য করা হবে, এ বিষয়ে কোনো একক সংজ্ঞা নেই। বাংলাদেশে প্রচলিত কমপক্ষে পঁচিশটি আইনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে শিশুদের কথা উল্লেখ আছে। ‘শিশুর’ সংজ্ঞা একেক আইনে ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। প্রত্যেকটি আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন ধরনের। ফলে, সংজ্ঞা নির্ধারণে বয়সের ভিন্নতা তৈরি হয়েছে। তবে সম্প্রতি বিয়ের বয়স কমানো নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সে বিষয়টির গভীরে যাওয়া দরকার। কেননা, বাল্যবিবাহের কুফলজনিত সমস্যার চরিত্রটি গভীরভাবে সামাজিক, শুধুই চিকিৎসা সংক্রান্ত বা স্বাস্থ্যগত নয়। তবে কেন বাল্যবিবাহ উচিত নয়, এর কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো স্বাস্থ্যঝুঁকিগত। অর্থাৎ কম বয়সে বিয়ে মানেই কম বয়সে সন্তান জন্ম দান এবং এর পুরো স্বাস্থ্যহানিকর ও মানসিক আঘাতজনিত প্রভাব পড়ে মেয়েটির ওপর। যারা বলেছেন মেয়েদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিয়ের বয়স আঠারোর কম হওয়া উচিত নয়, তারা ধরে নিচ্ছেন যে, আঠারোর কম বয়সে বিয়ে হলেই যে-কোনো মেয়ের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পড়াটা অবশ্যম্ভাবী। বয়স কমিয়ে ষোলো করলে মেয়েদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে কি না এ বিষয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত চূড়ান্ত বলে গণ্য হওয়া উচিত। তবে পুরো বিতর্কের স্বাস্থ্যগত উপাদান ছাড়াও এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদানও জড়িত রয়েছে। ২. ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বয়স সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম আইন প্রণীত হয় আজ থেকে প্রায় ৮৫ বছর আগে। ১৯২৯ সালে প্রণীত এই আইনের নাম ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন’। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয় ১৪ এবং ছেলেদের ১৮। ১৯৮৪ সালে এই আইনে পরিবর্তন এনে বিয়ের ন্যূনতম বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য করা হয় ২১। তবে এর আগেও কমপক্ষে দুইবার বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণমূলক আইন পাস করা হয়েছিল, যদিও ভিন্ন উদ্দেশ্যে। যেমন ১৮৭২ সালে ‘স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট’ নামে একটি আইন করা হয়। এই আইনেও বিয়ের ন্যূনতম বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ নির্ধারণ করা হয়। এই আইনটি কোনো বিশেষ ধর্মানুসারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে নিজেরা বিয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, তাদের ওপর বিয়ের বয়সের উল্লিখিত নিম্নতম সীমা আরোপের বিধান ছিল। এ আইনটি ছিল কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং বিদ্যাসাগরের বহুদিনের আন্দোলনের ফল। তবে, উনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৬০-১৯০০) বঙ্গে তুমুল বিতর্কিত অন্য একটি বিষয় ছিল সহবাসের সম্মতির বয়স নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা। তখন বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও সহবাসের ন্যূনতম বয়সকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হতো। ১৮৯১ সালে ‘সম্মতির বয়স’ বিল নামে একটি আইন পাস করা হয়। এর ফলে যৌনসঙ্গমে অনুমতিদানের বয়স স্ত্রীর জন্য ১০ থেকে ১২ বছরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে দুইটি আইন দ্বারা বিয়ের বয়স নির্ধারিত হয়ে আছে। প্রথমটি হলো, ১৯২৯ সালে প্রণীত ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন’ ও দ্বিতীয়টি হলো ১৯৬১ সালের ‘মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ’। এই দুই আইন অনুসারে মেয়েদের বিয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮ এবং ছেলেদের ২১। ৩. যারা ১৮ থেকে কমিয়ে বিয়ের বয়স ১৬ বছর করার পক্ষ সমর্থন করেন তারা সাধারণত দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির ওপর জোর দেন। প্রথমত, সমাজে বর্তমানে শিক্ষার হার বাড়ছে। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। ফলে, শিক্ষার হার যখন বাড়ে তখন সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী মেয়েদের বাল্যবিবাহ কমে যায়। দ্বিতীয়ত, বয়স কমানোর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো আইনগত প্রশ্ন। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেয়ার প্রবণতা আমাদের সমাজ মানসের গভীরে প্রোথিত রয়েছে। ফলে, অনেকেই গোপনে বা কাজীর কাছে বয়স লুকিয়ে হলেও মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। ফলে, যে আইন অনুযায়ী বিয়েটি বেআইনি (ইললিগ্যাল) হচ্ছে, কিন্তু সেই একই আইন অনুযায়ী আবার বিয়েটি অবৈধ (ইনভ্যালিড) বা বাতিলযোগ্য (ভয়েডেবল) হচ্ছে না। কেননা, আইনে বলা আছে যে, বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের ন্যূনতম সীমা যদি কোনো পক্ষ লঙ্ঘন করে সেজন্য তাদের শাস্তি হবে। কেননা, তারা একটি বেআইনি কাজ করেছে। কিন্তু তাই বলে তাদের বিয়েটি বাতিল হয়ে যাবে না। এটাই বর্তমান আইনের বিধান। ফলে, বিয়ের বয়স যখন কমিয়ে ১৬ করা হবে তখন অন্তত বয়সের কারণে বিয়ে ‘অবৈধ’ হয়ে যাওয়ার সমস্যা হ্রাস পাবে। এ যুক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে খুবই দুর্বল। তবে সামাজিক বাস্তবতা এই দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রবল সমর্থক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৯ লাখ কিশোরী অপ্রাপ্ত বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে দেয়া হয় গড়ে ১৩/১৪ বছর বয়সে। বিয়ের আইনসম্মত বৈধ বয়সে (১৮ বছর) পৌঁছাবার আগেই প্রায় অর্ধেক মেয়েশিশুর বিয়ে হয়ে যায়। ফলে তার শরীর সন্তান ধারণের উপযোগী হওয়ার আগেই তাকে গর্ভধারণ করতে হয়। প্রতিবছর বাংলাদেশে ১০-১৫ বছরের ৮ লাখ ৫০ হাজার কিশোরী বিবাহিত ও সন্তানের জননী হয়। ১৯৯৬ সালে যশোরে চৌগাছা থানায় একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ১,১৭৮টি বিয়ের মধ্যে ৫৬.৬%ই বাল্যবিবাহ। অথচ এখন বাংলাদেশে ১০-১৪ বছর বয়সী কোনো ছেলেশিশুর বিয়ে হয় না বললেই চলে। এক হাজার জনে এ হার মাত্র ০.১। অন্যদিকে প্রতি হাজারে এ বয়সী ১১.৬ জন মেয়েশিশুর বিয়ে হয়। ১৫-১৯ বছর বয়সী ছেলেদের বিয়ের হার যেখানে প্রতি হাজারে ৮.৫, সেখানে মেয়েদের বেলায় এ হার ১৯৪.৮ জন। ৪. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯-এ ধারা ৪ অনুসারে ১৮ বছর বয়সের নিচে মেয়ে এবং ২১ বছর বয়সের নিচে ছেলেদের বিয়ে হওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় অঞ্চলে মেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যায়, ১৬৫ জন মেয়ের মধ্যে ৫৫.৯০%-এর বিয়ে ১৩-১৫ বছরের মধ্যে হয়েছে। ৯৫ জন অভিভাবকও অপ্রাপ্ত বয়সে তাদের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। অপরদিকে স্বামীর বর্তমান বয়সের তালিকায় ৩৮.১৮% পাত্র ১৫-২২ বছর বয়সী। এরাও বিয়ের জন্যে প্রাপ্তবয়স্ক নয়। মেয়েদের কয়েকজনের ১ বছর, ৬ মাস, ৩ মাস, ৭ দিনের মাথায় বিয়ে হয়েছিল বলেও কন্যা ও অভিভাবক পক্ষ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মেয়ে এবং স্বামীর বয়স উল্লেখের ক্ষেত্রে সত্যিকার বয়সটি লুকানোর প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। গবেষণাটি উপকূলীয় গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত হলেও এই বাস্তবতা সারা বাংলাদেশে একই রকম। গবেষণায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন বিয়ে রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত সূত্রে জানা যায়, এসব এলাকায় ১৬৫টি বিয়ের মধ্যে ৩১.৫২% মেয়ের বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। এ জন্য তারা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন রেজিস্ট্রিতে মেয়ের শ্বশুর রাজি ছিলেন না; মেয়ে নাবালিকা হওয়ায় আইনগত সমস্যা, দুইপক্ষের যৌতুকসংক্রান্ত মতভেদে বাবা-ভাই প্রয়োজন বোধ করেননি, ছেলের চাকরির সমস্যা, কাজী অফিস দূরে হওয়া, বিবাহ রেজিস্ট্রির ব্যাপারে কেউ উদ্যোগ না নেয়া, এবং প্রয়োজনীয়তা না বোঝা, অজ্ঞতা, অসচেতনার কারণে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন হয়নি। ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) কর্তৃক পরিচালিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত ওই জরিপে অভিভাবকদের জন্যে একটি প্রশ্ন ছিল, অল্প বয়সে মেয়ে বিয়ে দেয়ার ফলে তাদের অনুশোচনা হয় কি-না? এ প্রশ্নের উত্তরে ৬৬.৮৭% বলেছেন অনুশোচনা হয়, ২৫.৪৫% বলেছেন হয় না, ০৬.৬৮% এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। যারা বলেছেন অনুশোচনা হয় তাদের অনেকের মতে, মেয়েকে ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে নিজের হাতে মেয়ের সর্বনাশ করেছেন, মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছেন। বিয়ে পরবর্তী সময়ে যৌতুকের জন্যে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং অনাদায়ে কন্যাশিশুদের মধ্যে ৫৮.১৮% নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এখনো বাংলাদেশে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়ার যে উচ্চ হার জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে এর কারণ গভীরভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। আমাদের ইতিহাসে এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। ৫. উনিশ শতকেও বঙ্গদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বাল্যবিবাহ। দশ বছর হবার আগেই সাধারণ মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হতো। এমন কি, তিন-চার বছরের অথবা কয়েক মাস বয়সের মেয়ের বিয়ে হওয়াও একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না। হিন্দুশাস্ত্র পরাশরসংহিতায় গৌরীদান অর্থাৎ আট বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। অপর পক্ষে, মনুসংহিতায় কোনো মেয়ের মাসিক দেখা দেয়ার পর বিয়ে হলে সেই পিতামাতার নরকে যাওয়ার বিধান রয়েছে। বারো বছর বয়সে পাছে মাসিক দেখা দেয়, সেই আশঙ্কায় পিতামাতারা তার আগেই বিয়ে দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতেন। একেবারে উঁচুশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণরাই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। যেহেতু মেয়েদের বিয়ে অত কম বয়সে হতো, সে জন্যে বিয়ের পর বালিকা-স্ত্রীকে কখনো কখনো বাপের বাড়িতেই রেখে দেয়া হতো (যেমনটি ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর বিয়েতে)। তারপর সেই স্ত্রী প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হতো। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বালিকা-বধূ শ্বশুরবাড়িতেই বড়ো হতো। ঋতুমতী হওয়া উপলক্ষে পুনর্বিবাহ নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হতো। এত কম বয়সে বিয়ে হলে স্বভাবতই নানা ধরনের সমস্যা হতো। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। ১৮২০ সালের দিকে রাসসুন্দরী দেবীর বিয়ে হয় দশ বছর বয়সে। বিয়ের পর তাকে যখন স্বামীর বাড়িতে পাঠানো হয়, তখন তিনি কেমন মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন এবং কী রকম ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, আত্মজীবনীতে নিজেই তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বালিকা-বধূকে গ্রহণ করা হতো এক ধরনের শত্রুতার মনোভাবের সঙ্গে। ঘরের ছেলেকে এই ডাইনি দখল করতে এসেছে-এই মনোভাব থেকে। এবং সেই আট-দশ বছর থেকেই বালিকা-বধূদের সংসারের কাজ করার আদেশ দেয়া হতো। বাল্যবিবাহের আর-একটা কুফল ছিল বৈধব্য। তখন শিশুমৃত্যুর হার ছিল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো যে-স্বামীদের স্ত্রী সেই বাল্যবয়সেই মারা যেত, তাদের কোনো অসুবিধে হতো না, কারণ তারা অচিরে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করতেন। কিন্তু যে-বালিকা বধূদের স্বামী মারা যেত, তাদের সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে হতো। শুধু তা-ই নয়, বৈধব্যের তাবৎ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো বাকি জীবন ধরে। বাল্যবিবাহের এই রীতি কত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উনিশ শতকের বিখ্যাত লোকদের জীবনী থেকে। রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন পনেরো বছর বয়সে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি সে যুগের তুলনায় খুব আধুনিক হলেও তার পুত্র অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে, আর রবীন্দ্রনাথের মায়ের বা পাত্রীর বয়স ছিল এগারো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত- সেকালের বিখ্যাত এই ব্যক্তিরা সবাই বিয়ে করেছিলেন তাদের বয়স সতেরো হবার মধ্যেই। তাদের পাত্রীদের বয়স ছিল আরও কম। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বিয়ে করেছিলেন, তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। দেবেন্দ্রনাথ এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রীর বয়স ছিলো ছয় বছর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর বয়স ছিল সাত বছর, বিদ্যাসাগরের আট, কেশব সেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয়, শিবনাথ শাস্ত্রীর দশ আর রাজনারায়ণ বসুর স্ত্রীর বয়স ছিল এগারো বছর। এসব বিচারে বলতে হয়, আদর্শ পাত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৩ বছর বয়সে অভিভাবকদের ইচ্ছায় একটি নিরক্ষর ও মাত্র এগারো বছর বয়সের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল।৬ ৬. বাল্যবিবাহসংক্রান্ত এই যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তা খুব গভীরভাবে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। মনুসংহিতা হলো হিন্দুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আইনগ্রন্থ। মেয়েদের বিয়ের বয়স মনুসংহিতা থেকে শুরু করে মহাভারতেও সাত থেকে দশের বেশি নয়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, # ‘কন্যা বিবাহ উপযুক্ত কাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পিতৃগৃহেই অবস্থান করবে সেও ভালো, তবুও গুণহীন বরের (অর্থাৎ বিদ্যা, শৌর্য, সুন্দর চেহারা, উপযুক্ত বয়স, মহত্ত্ব, লোক ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বর্জন এবং কন্যার প্রতি অনুরাগ- এগুলো নেই যে পাত্রের) হাতে কন্যাকে দান করবে না।’ (৯/৮৯) # ‘কুমারী কন্যা ঋতুমতী হলেও তিন বৎসর পর্যন্ত গুণবান বরের অপেক্ষা করবে; এ পরিমাণ কাল অপেক্ষার পরও যদি পিতা তার বিবাহ না দেন তা হলে কন্যা নিজসদৃশ পতি নিজেই বেছে নেবেন।’ (৯/৯০) # ‘ঋতুমতী হওয়ার তিন বৎসর পরেও যদি ঐ কন্যা পাত্রস্থ করা না হয়, তা হলে সে যদি নিজেই পতি বরণ করে নেয়, তার জন্য সে কোনো পাপের ভাগী হবে না। কিংবা সেই পতিরও কোনো পাপ হবে না।’ (৯/৯১) # ‘কন্যা বিবাহযোগ্য না হলেও তাকে উৎকৃষ্ট, সুরূপ, সুবর্ণ বরের কাছে বিধি অনুসারে সম্প্রদান করবে।’ (৯/৮৮) বাল্যবিবাহ তখন অভিশাপের মতো গ্রাস করত নারীজীবনকে। কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন পুরুষের আজীবন অতৃপ্ত ও প্রখর যৌনবাসনার জন্যই মেয়েদের বাল্যকালে বিয়ে দিয়ে তাদের রক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হতো ও একই কারণে বহুবিবাহও সমাজে চালু ছিল এবং সমাজস্বীকৃত কর্ম বলে পরিগণিত হতো। ৭. বাল্যবিবাহের একই চিত্র পাওয়া যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লানার বিয়ের চেষ্টা চলছিল যখন তার বয়স ছয়। কালকেতু এগার বছর বয়সে বিয়ে করেছিল যখন ফুল্লুরার বয়স আরো কম। মেয়েদের বাল্যবিবাহের জন্য বর-বধূর বয়সের পার্থক্য হতো প্রচুর যা সব সময় সংসার বা সমাজের জন্য কল্যাণকর ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে কৃষ্ণ যখন প্রেম নিবেদন করে, তখন রাধার বয়স ছিল এগার, কিন্তু সে তখন রীতিমতো বিবাহিত। কিশোরী রাধা প্রথম প্রথম কৃষ্ণের এই দেহজ প্রেমে সাড়া না দিয়ে বরং বিরক্তি প্রকাশ করেছে। বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বয়স ছিল আট, যখন তাকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। রঘুনন্দনের (মধ্যযুগের বিখ্যাত আইনবিদ) বাণী অনুসারে রজঃ দর্শনের আগে কন্যাকে পাত্রস্থ না করতে পারলে পিতা নরকবাসী নন। রঘুনন্দনের মতে, পাত্রীর বয়স আট বছরের কম ও বারো বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়। পিতৃগৃহে রজঃ দর্শন করা কন্যা বিয়ে দিয়ে শুধু পিতাই নরকবাসী হবেন না, যে পুরুষ সেই নারীকে বিয়ে করবে সেও শূদ্রতুল্য বলে সমাজে পরিচিত হবে। অষ্টম বর্ষে কন্যার বিয়েকে গৌরীদান, নবম বর্ষে বিয়েকে পৃথ্বীদান বলে, দশম বর্ষে বিয়ে হলে পবিত্রালোকপ্রাপ্তির মতো পুণ্য সঞ্চয় হয় মর্মে বিধান ছিল তখন। ধর্মীয় আচরণে নিজেদের পৃথক দাবি করলেও বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ও হুবহু প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথাই অনুসরণ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। -আরিফ খান
এসংক্রান্ত পুরনো সংবাদ-
- ট্যাগ:
- বাংলাদেশ
- বাল্য বিবাহ
- বাল্যবিবাহ
৪ ঘণ্টা, ২৬ মিনিট আগে
জাগো নিউজ ২৪
| নেপাল
৫ ঘণ্টা, ৩২ মিনিট আগে
বিডি নিউজ ২৪
| নরসিংদী সদর
৫ ঘণ্টা, ৩৯ মিনিট আগে
৫ ঘণ্টা, ৪২ মিনিট আগে
৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট আগে
বিডি নিউজ ২৪
| নরসিংদী সদর
৫ ঘণ্টা, ৩৯ মিনিট আগে
৬ ঘণ্টা, ৪৯ মিনিট আগে
ডেইলি স্টার
| মোহাম্মদপুর, ঢাকা
১২ ঘণ্টা, ১২ মিনিট আগে
ঢাকা পোষ্ট
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
১৪ ঘণ্টা, ১২ মিনিট আগে
ডেইলি স্টার
| বাগেরহাট
১৪ ঘণ্টা, ২০ মিনিট আগে
১৪ ঘণ্টা, ৫৮ মিনিট আগে
১৫ ঘণ্টা, ১ মিনিট আগে
বিডি নিউজ ২৪
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ ঘণ্টা, ৫ মিনিট আগে