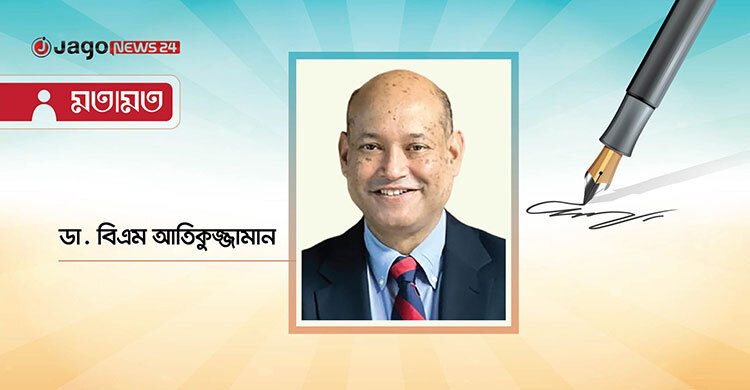নতুন প্রজন্ম কি কেবলই একটি 'বন্দি' প্রজন্ম?
বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক ডিজিটাল রূপান্তর এবং দ্রুত নগরায়ণের এক চমকপ্রদ পর্যায়ে অবস্থান করছে। বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত এই অগ্রগতির চিত্রটি একদিকে যেমন আশার সঞ্চার করে, তেমনি এর নেপথ্যে জমে উঠছে এক নীরব এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক সংকট—তা হলো প্রজন্মগত বৈষম্য। এই প্রজন্মগত বৈষম্যের শিকার হলো দেশের যুব সমাজ, যারা প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ, উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্বজনীন চিন্তাধারায় অভ্যস্ত। কিন্তু তারা ক্রমশ অনুভব করছে যে সমাজের সিঁড়িতে আরোহণ করা তাঁদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন, এমনকি অসম্ভব।
শিক্ষা, কর্মসংস্থান, এবং সম্পত্তি মালিকানার ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত বাধাগুলো দৃঢ়মূল হয়েছে, তা নতুন প্রজন্মকে এক প্রকার অদৃশ্য 'ফাঁদে বন্দি' করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অসঙ্গতি নয়; এটি একটি গভীর সমাজতাত্ত্বিক সঙ্কট, যেখানে পিয়ের বুরদিয়ু ও কার্ল মার্কসের সামাজিক পুনরুৎপাদনের তত্ত্বসমূহ বাস্তবের মাটিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।
সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বুরদিয়ুর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সমাজে বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক পুঁজির মাধ্যমে টিকে থাকে না, বরং এটি সাংস্কৃতিক পুঁজি এবং সামাজিক পুঁজির মাধ্যমেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এই পুঁজিগুলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে সুযোগের ক্ষেত্রকে সীমিত করে দেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও দেশের শিক্ষা খাত প্রভূত সম্প্রসারিত হয়েছে, সেই শিক্ষা কিন্তু সকলের জন্য সমান সুযোগের দরজা উন্মুক্ত করতে পারেনি।
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যম এবং বিদেশি ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অদৃশ্য শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাজন বুরদিয়ুর 'সাংস্কৃতিক পুঁজি'র ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে—যেখানে শুধুমাত্র মেধা বা একাডেমিক ফলাফল নয়, বরং 'সঠিক ধরণের শিক্ষা', 'সুবিধাজনক সামাজিক সংযোগ' এবং প্রাতিষ্ঠানিক 'সঠিক অভ্যাস' বা আচরণবিধি নির্ধারণ করে কে সফল হবে এবং কে প্রান্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রান্তিক অঞ্চল বা দুর্বল সামাজিক পটভূমি থেকে আসা শিক্ষার্থীরা তথাকথিত 'উচ্চ সাংস্কৃতিক পুঁজি'-র অভাবের কারণে প্রথম থেকেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে, যা বৈষম্যের সূচনা করে।
এই কাঠামোগত শিক্ষা বৈষম্য সরাসরি কর্মসংস্থান বাজারের উপর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রতিবছর লাখো তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, কিন্তু তাঁদের মেধা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী পর্যাপ্ত এবং মর্যাদাপূর্ণ চাকরির সুযোগ নেই। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এখনো দেশের বৃহৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র, কিন্তু এই খাত অনিরাপদ, অস্থায়ী, শোষণমূলক এবং প্রায়শই নিম্ন মজুরিভিত্তিক। অপরদিকে, দেশের আনুষ্ঠানিক বেসরকারি খাত এখনো পারিবারিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য ন্যায্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগকে সীমিত করে তুলেছে।
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দীর্ঘসূত্রিতা তরুণদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা সৃষ্টি করেছে। ২০২৪ সালে কোটাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তরুণদের নেতৃত্বে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, তা কেবল একটি নিয়োগ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না, বরং প্রজন্মগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের এক গভীর সামাজিক ও প্রতীকী অভ্যুত্থান ছিল।