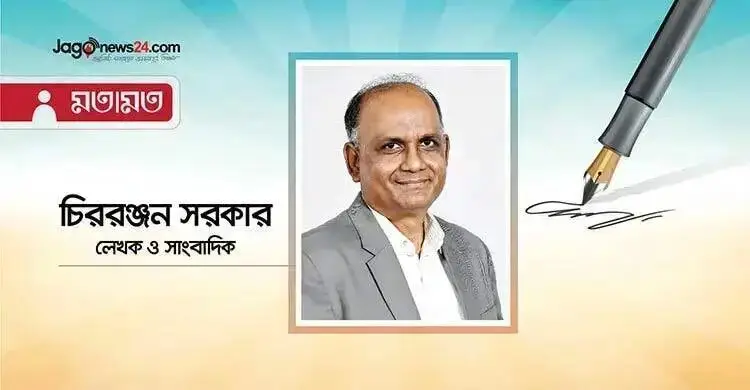
উদ্ভাবনের গল্পে অর্থনীতির নোবেল
নোবেল পুরস্কার নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে নামী ও দামী পুরস্কার। এ পুরস্কার যারা পান, তাদের নিয়ে দুনিয়াজুড়ে আলোচনা হয়। তবে চিকিৎসা, সাহিত্য, কিংবা শান্তিতে নোবেল নিয়ে যতটা আলোচনা হয়, ফিজিক্স, রসায়ন কিংবা অর্থশাস্ত্রের নোবেল নিয়ে ততটা আলোচনা হয় না। সবচেয়ে কম আলোচনায় আসে সম্ভবত অর্থনীতিতে নোবেল। অথচ এই পুরস্কার আমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ‘অর্থনৈতিক উন্নতি’ নিয়ে কাজ করা গবেষকদের দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ১৮৯৫ সালে বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল যে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যময় চুক্তিনামায় সই করে গেছেন, সেখানে রসায়নশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান (ফিজিক্স), চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও বিশ্বশান্তিতে পুরস্কার দেওয়ার কথা বলা হলেও অর্থশাস্ত্রে নোবেলের কোনো বিধান ছিল না। সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ব্যাংক অব সুইডেন’ ১৯৬৮ সালে এ পুরস্কারের সূচনা করে। এর পোশাকি নাম হলো ‘আলফ্রেড নোবেল স্মরণে অর্থনীতিতে ব্যাংক অব সুইডেন পুরস্কার’, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘ব্যাংক অফ সুইডেন প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্সেস ইন মেমোরি অফ আলফ্রেড নোবেল’ বা ‘নোবেল মোমোরিয়াল প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্সেস।’ তবে ধীরে ধীরে এটিও নোবেল পুরস্কারের মধ্যে আত্মীকরণ ঘটে।
২০২৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন তিনজন বিখ্যাত গবেষক: জোয়েল মোকির (যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি); ফিলিপ অ্যাঘিয়ন (ফ্রান্সের কলেজ দ্য ফ্রান্স এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স); পিটার হাউইট (যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি)। নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা’ করার জন্য এ বছরের নোবেল প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার অর্ধেক মোকিরকে ‘প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি’ নির্ধারণের জন্য। বাকি অর্ধেক যৌথভাবে পেয়েছেন অ্যাঘিয়ন ও হাউইট, যারা ‘সৃজনশীল ধ্বংসের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব উপস্থাপন করার জন্য।
উদ্ভাবন মানে হলো নতুন কিছু তৈরি করা। যেমন: নতুন মেশিন, নতুন প্রযুক্তি, নতুন ধারণা বা আইডিয়া, নতুন ব্যবসা। যেমন, মোবাইল ফোন একসময় ছিল না। এখন এটা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। এটি একটি বড় উদ্ভাবন। আবার ধরুন, বিদ্যুৎচালিত গাড়ি, অনলাইন ব্যাংকিং, কিংবা ঘরে বসে ভিডিও কল—এসবই উদ্ভাবনের ফল। এসব উদ্ভাবন আমাদের জীবন যেমন সহজ করেছে, তেমনি দেশের অর্থনীতিতেও এনেছে গতি।
তাহলে নোবেল বিজয়ীরা কী কাজ করেছেন? তাদের গবেষণা মূলত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে: ‘একটি দেশ কীভাবে উন্নতি করে? কীভাবে টেকসই (দীর্ঘদিন চলতে পারে এমন) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসে?”
জোয়েল মোকির একজন ইতিহাসবিদ। তিনি অতীত ঘেঁটে দেখেছেন, কেন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব হলো, আর চীন বা ইসলামি দুনিয়ায় হলো না, যদিও সেখানেও উদ্ভাবন ছিল।
তার গবেষণায় দেখা যায়: ইউরোপে লেখক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবকরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা বিনিময় করতেন। তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে শিখতেন, যুক্তি দিয়ে তর্ক করতেন। রাজারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।
এর ফলে ইউরোপে একটি “উদ্ভাবনবান্ধব পরিবেশ” তৈরি হয়। এই কারণেই সেখানে শিল্পবিপ্লব হলো, কলকারখানা গড়ে উঠল, আর শুরু হলো টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
মোকিরের বিখ্যাত বই ‘এ কালচার অফ গ্রোথ’-এ এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ফিলিপ অ্যাঘিয়ন ও পিটার হাউইট এই দুজন মিলে একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করেছেন, যার নাম ক্রিয়েটিভ ডিসট্রাকশন মডেল (সৃজনশীল ধ্বংস) ।







