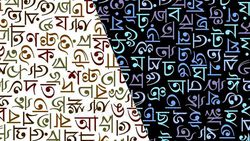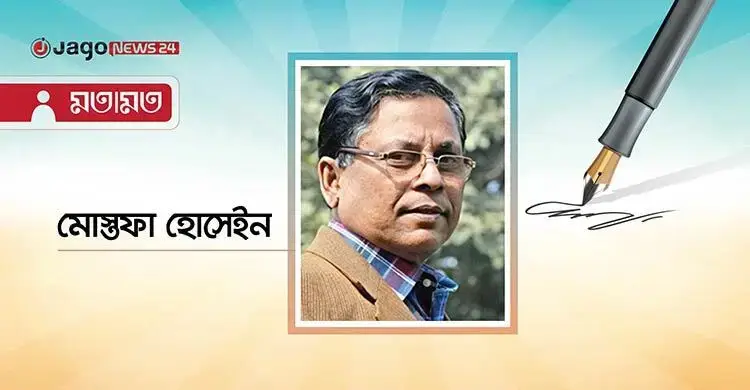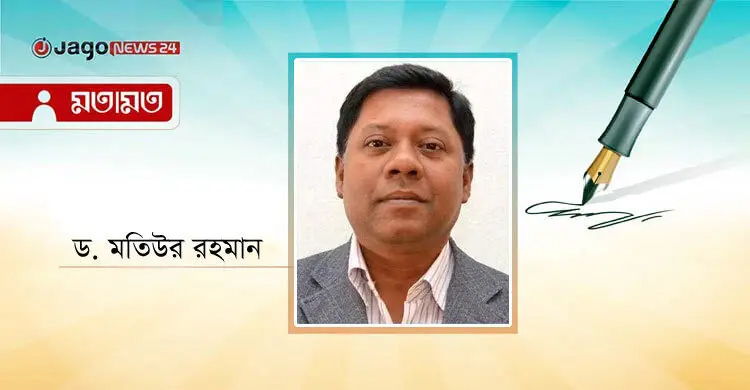কণ্ঠরোধ মানেই রাজনৈতিক আত্মহত্যা
যাঁরা হরর বা ভয়ের চলচ্চিত্র পছন্দ করেন, তাঁরা সম্ভবত এ ধরনের চলচ্চিত্রের একটি প্যাটার্ন বুঝতে পারেন। বিশেষ করে প্রেতাত্মানির্ভর সিনেমাগুলোয় এই প্যাটার্ন খুব স্পষ্ট। গল্প আর প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না কেন, এসব চলচ্চিত্রে ঘাড়ে চেপে বসা প্রেতাত্মাকে বিদায় করতে গিয়ে রোগী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যায়। এমনকি যারা প্রেতাত্মা ছাড়াতে উঠেপড়ে লাগে, তাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে ওঠে।
বাস্তব জীবনেও কিন্তু মানুষের ঘাড়ে ‘প্রেতাত্মা’ চেপে বসে। সেই ‘প্রেতাত্মার’ নাম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থা জনগণের ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসে যে, তাকে বিদায় করতে বিক্ষোভে নামতে হয়, রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। এর উদাহরণ আমরা শ্রীলঙ্কায় দেখেছি, অতিসম্প্রতি নেপালেও দেখলাম। নেপালের ক্ষেত্রে অবশ্য সরাসরি বলে দেওয়া যায় না যে সেখানে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভিত্তি গেড়ে বসেছিল। তবে শাসনব্যবস্থা ক্রমেই স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠছিল—এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, সেখানেও কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টাই আগুনে ঘি ঢেলেছে, সরকারের পতন ঘটেছে।
বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে বিগত এক শতাব্দীতে চেপে বসা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলোর উপসর্গ কিন্তু একই রকম। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকেরা ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে দমন-পীড়নের নানা কৌশল আঁটেন, বিরুদ্ধমত ও বিরোধী দল দমনে উঠেপড়ে লাগেন। এই কাজ করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে দুর্নীতিতে ছেয়ে যায় পুরো দেশ, ধসে পড়ে অর্থনীতি। একদিকে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস, অন্যদিকে রাজনীতিক ও সরকারের নিয়ন্ত্রক মন্ত্রী-এমপি-আমলা ও তাঁদের পরিবারের বিলাসবহুল জীবন প্রকট আকারে প্রকাশ্যে আসতে থাকে। এই অবস্থায় সরকার কণ্ঠরোধের পথ বেছে নেয়। প্রথমেই সে সংবাদমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরে, সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করে। এ কাজ করতে গিয়ে গুম-খুন বেড়ে যায়। জনগণ ও রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিতে প্রণীত আইন ব্যবহৃত হয় জনগণকে দমনে।
গত তিন দশকে অবশ্য টুঁটি চেপে ধরা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, পুরো বিশ্বই এখন ইন্টারনেটের আওতায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর কল্যাণে মানুষ এখন অনেকটাই বিশ্ব নাগরিক। সেখানে তাৎক্ষণিক নিজের মতামত প্রকাশ করা যাচ্ছে, বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ হিসেবে ছবি-ভিডিও প্রকাশ করে ছড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে। কাজেই স্বৈরাচার হয়ে ওঠা সরকারব্যবস্থাকে সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি ইন্টারনেটেরও টুঁটি চেপে ধরতে হচ্ছে। বিক্ষোভ দমনের এখন প্রধানতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া।
অতিসম্প্রতি নেপালেও আমরা একই ধরনের উপসর্গ প্রত্যক্ষ করলাম। দুর্নীতিতে এতটাই ছেয়ে গিয়েছিল দেশটি যে সাধারণ মানুষের না খেয়ে থাকার উপক্রম হয়েছিল। এ কারণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু সরকার কণ্ঠরোধের পথ বেছে নিয়েছিল। মাত্র সাত দিন নিবন্ধনের সময় দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বন্ধের কৌশল নিয়েছিল তারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে না পারায় বেশির ভাগ সামাজিক মাধ্যম বন্ধও করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে ফল উল্টো হয়েছে। ফুঁসে উঠেছে জেন-জি। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সাধারণ মানুষও। বিক্ষোভ এতটাই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে শুরু করেন মন্ত্রীরা। একটা পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয় সরকারকে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। এমনকি পদত্যাগের পর জীবন বাঁচাতে তাঁকে আত্মগোপনও করতে হয়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথমে শ্রীলঙ্কা, তারপর নানা ঘটনাপ্রবাহের পর নেপালে প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটল। এগুলো কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। অনেকেই হয়তো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজবেন। কিন্তু মোটা দাগে স্বীকার করতেই হবে, ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ক্ষেত্রে কণ্ঠরোধের কৌশল আর কাজে আসছে না। কারণ, এখনকার তরুণেরা জেন-জি প্রজন্ম। এই প্রজন্ম হয়তো স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটারে মুখ গুঁজে থাকে, আগের মতো রাজনীতির মাঠ দাপিয়ে বেড়ায় না, তাই বলে এরা যে রাজনীতির বিষয়ে অসচেতন, তা বলা যাবে না। বরং এই প্রজন্ম ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর কল্যাণে আগের যেকোনো প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি বিশ্ব নাগরিক। এই প্রজন্মের কণ্ঠরোধের চেষ্টা মানেই রাজনৈতিক আত্মহনন। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে রাজনীতিকদের প্রকৃত অর্থেই এখন জনমানুষের বন্ধু হতে হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে আখের গোছানোর স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতিতে আসার পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যাঁদের আমরা আমলা বলে চিনি, তাঁদেরও তোষামোদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারকে স্বৈরাচার হয়ে ওঠার পথ রচনার সংস্কৃতি থেকে সরে আসতে হবে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- কণ্ঠরোধ
- গণঅভ্যুত্থান