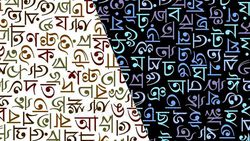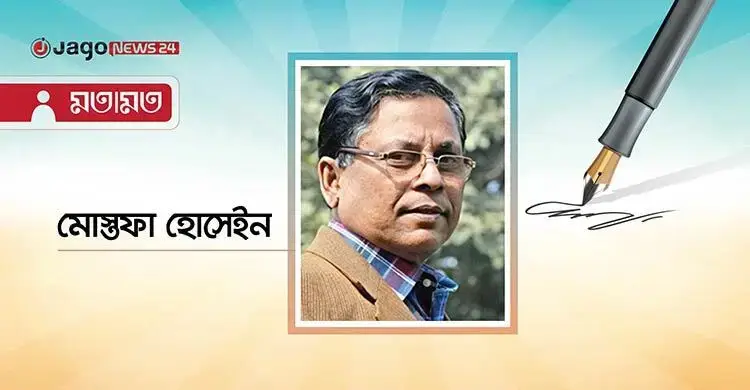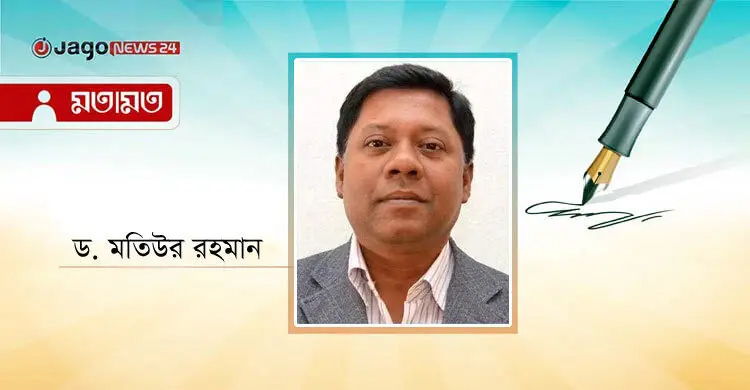জনতার আদালতের বিচার অত্যন্ত কঠিন
বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। গত কয়েক বছরে হাঁকডাক করে বলা হচ্ছিল দেশটি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে। আরও বলা হয়েছে উত্তরণটি ঘটবে আগামী বছর ২০২৬ সালে। কিন্তু এখন বিতর্ক হচ্ছে-২০২৬ সালেই এ উত্তরণ মেনে নেওয়া ঠিক হবে কিনা। কারণ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপান্তরিত হলে দেশটি আন্তর্জাতিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসব ছাড় উপভোগ করছে, সেগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। ইতোমধ্যে ব্যবসায়ী মহলের পক্ষ থেকে এ উত্তরণের রোডম্যাপ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকার এ ব্যাপারে দোদুল্যমানতায় থাকার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী বছরেই উত্তরণটি ঘটবে।
বাংলাদেশের মতো একটি দেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা, তা নিরূপিত হয় বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও সূচকের দ্বারা। দেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান, বিশেষ করে শেখ হাসিনার আমলের পরিসংখ্যানের ওপর আদৌ বিশ্বাস রাখে না। এ সময় অর্থনীতি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগই বানোয়াট এবং বিভ্রান্তিকর। সত্যিকার পরিসংখ্যানকে দুমড়ে-মুচড়ে নিজেদের ইচ্ছামাফিক প্রচারণার স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য হেন অপচেষ্টা নেই, যা আওয়ামী লীগ সরকার করেনি। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের দুজন মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং মহীউদ্দীন খান আলমগীর অত্যন্ত নোংরা ভূমিকা পালন করেছেন। এ কারণে বিবিএসের মতো প্রতিষ্ঠানের ডেটা চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাস্তব অবস্থা ছিল সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যানের বিপরীত। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিবিএস দারিদ্র্যের ওপর একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশের ২৭.৯৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ৯.৩৫ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)। বিশ্বব্যাংকও প্রক্ষেপণ থেকে জানিয়েছে, চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে ১৫.৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী এবং অতিরিক্ত ৩ মিলিয়ন মানুষ এ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীরগতি এবং দুর্বল শ্রমবাজার পরিস্থিতির কারণে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য শিশুদের ওপর আনুপাতিক হারের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলেছে। ২৮.৯ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে রয়েছে ২০২৫-এ। শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অধিকতর দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে।
শেখ হাসিনার আমলে দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে বলে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল। ওই সরকার গণতন্ত্র নয় বরং উন্নয়নের ওপরই গুরুত্বারোপ করেছিল। তাদের ভাষায় এটা ছিল উন্নয়নের গণতন্ত্র। এতই যদি উন্নয়ন হয়ে থাকে, তাহলে সে সরকার বিদায় নেওয়ার এক বছরের মধ্যে দারিদ্র্যের এই হাল হলো কেন?
শেখ হাসিনার আমলে অনেক মেগা প্রকল্প ও আধামেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের কথা বলে প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল, সে প্রকল্প শেষ হয়েছে দেড়গুণ বা দুইগুণ অর্থ ব্যয় দিয়ে। এর একটি বড় কারণ হলো, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা। বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণে আওয়ামী আমলে ভারত, ইউরোপ ও চীনের তুলনায় প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় হয়েছে দেড় থেকে দুইগুণ অধিক অর্থ। কারণটি বোঝার জন্য রকেট বিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই। স্ফীত প্রকল্প ব্যয় ও বর্ধিত প্রকল্প ব্যয়ের অর্থের একটি বড় অংশ লুটেপুটে খেয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং অন্য স্বার্থবাদীরা। শেখ হাসিনার আমলে একটি পরিপোষণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয়েছে শেখ হাসিনার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি ও আজ্ঞাবহরা। এ ব্যবস্থাকে অনেকেই আখ্যা দিয়েছেন crony capitalism. শেখ হাসিনার আমলে অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, যেগুলো এখন শ্বেতহস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এগুলো থেকে কোনো ধরনের বেনিফিট তো আসছেই না, বরং এগুলোর অবকাঠামো কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে। অনেক প্রকল্পই হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে কোনো ধরনের কস্ট-বেনিফিট এনালাইসিস না করে। প্রকল্পের যথার্থতা প্রমাণের জন্য যদি কোনো কস্ট-বেনিফিট এনালাইসিস করা হয়ে থাকে, তাও ছিল সম্পূর্ণ ভুয়া। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশ কোনোক্রমেই বিলাসিতা ও অপচয়কে প্রশ্রয় দিতে পারে না। অর্থনীতিবিদ পল এ. বারান বলেছিলেন, উন্নয়নশীল দেশে দুই ধরনের উদ্বৃত্ত থাকতে পারে, যা দিয়ে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা সম্ভব। এর একটি হলো বাস্তব উদ্বৃত্ত বা Actual surplus, অন্যটি হলো সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত বা Potential surplus. এসব দেশের ধনিক-বণিক ও ভূস্বামীরা বিলাসব্যসনে যে অর্থ ব্যয় করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যয় করতে গিয়ে যত রকমের অপচয় হয়, সেগুলো যদি ঠেকানো যায় এবং উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করা যায়, তাহলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরও জোরদার হবে। দেখা যাবে অপচয়কৃত অর্থ দিয়ে ভিন্ন একটি বা একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। অগ্রাধিকার নির্ণয় যদি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়, তাহলে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছে উন্নয়ন সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু, এসব কথা শুনবে কারা? যাদের উদ্দেশ্য হলো জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে নিজের পকেট ভর্তি করা, তাদের কাছ থেকে সদাচরণ আশা করা যায় না।
- ট্যাগ:
- মতামত
- স্বল্পোন্নত দেশ
- গণঅভ্যুত্থান