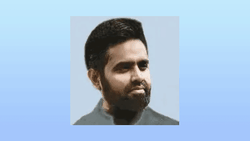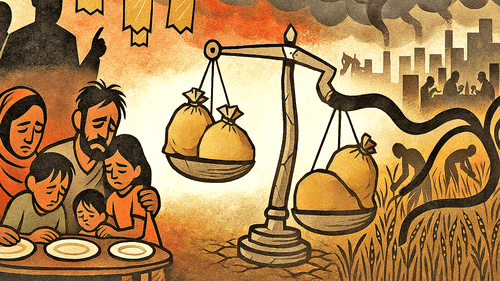
তথ্যের চেয়েও অধিক করুণ
বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) পরিচালিত ‘২০২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি’ শীর্ষক সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে যে তিন বছরে (২০২২-২৫) দেশে দারিদ্র্যের হার ৯ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে এখন ২৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০ দশকের গোড়া থেকে কোভিড-পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দেশে দারিদ্র্যের হার ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকলেও তিন বছর ধরে তা যে আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পড়েছে, সেটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। অবশ্য মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দিয়ে এমনিতেও উপলব্ধি করছিল যে তার অর্থকষ্ট দিন দিনই লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে পিপিআরসি জরিপের ফলাফল বস্তুত সাধারণ মানুষের সে উপলব্ধিকেই পরিসংখ্যান দিয়ে প্রত্যয়ন করল। তবে প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে পিপিআরসি জরিপের তথ্যে জনগণের আর্থিক দুরবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, বাস্তব পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক বেশি করুণ।
উল্লিখিত জরিপে দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমা সন্নিহিত মানুষের হিসাব দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির হিসাবনিকাশও এতে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে মানুষের জীবনযাপন যে এখন কতটা কষ্টকর ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা বা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তবে এর মাধ্যমে কিছুতেই সে দুর্বিষহ কষ্টের গভীরতা ও এর বাস্তব পীড়নকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ জন্য আসলে প্রয়োজন সত্যিকার মানবিক উপলব্ধি এবং পীড়িত মানুষের প্রতি গভীরতাপূর্ণ নিঃস্বার্থ মমতা, যা আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালক, রাজনীতিক কিংবা আমলা—কারও মধ্যেই নেই।
জরিপের তথ্য থেকে রাষ্ট্র তথা এর জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রবণতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার বেশির ভাগটাই অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তদুপরি সেখানে এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা না করলে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়াটা একেবারেই অনিবার্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে কয়েকটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।
এক. মানুষকে যে তার আয়ের সিংহভাগই (৫৪.৯৯ শতাংশ) খাদ্যের পেছনে ব্যয় করতে হচ্ছে, তার জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে অসৎ, অদক্ষ ও দুর্বল বাজারব্যবস্থাপনা, যা আসলে দুর্বল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-সংস্কৃতিরই ফল। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন এবং সে দুর্বৃত্ত রাজনীতির আওতায় চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও যখন-তখন মব সৃষ্টির মতো সংস্কৃতি বন্ধ না হলে হঠাৎ হঠাৎ ও সাময়িকভাবে আরোপিত বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার আওতায় খাদ্যব্যয় কখনোই কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বাজারে খাদ্যপণ্যের যে মূল্য, তা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় খাদ্য-উচ্চমূল্যসম্পন্ন দেশগুলোর প্রায় কাছাকাছি। বিষয়টি অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বাজারে খাদ্যপণ্যের সরবরাহ ও মূল্য ঠিক রাখার নামে রয়েছে কর-শুল্ক মওকুফের আরেক চতুর ও লুক্কায়িত মহাবাণিজ্যব্যবস্থা। বাজারে কোনো পণ্যের ঘাটতির (আসলে কৃত্রিম ঘাটতি) আশঙ্কা দেখা দিলেই সরকার সঙ্গে সঙ্গে ওই পণ্যের আমদানি শুল্ক মওকুফ করে দেয়। তাতে রাষ্ট্র বিপুল রাজস্ব হারালেও সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য প্রায় কখনোই কমে না। অথচ এ প্রক্রিয়ায় মাঝখান থেকে লাভবান হন ওই চতুর আমদানিকারকেরা, যাঁরা জুজুর ভয় দেখিয়ে শুল্ক মওকুফ কৌশল গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করেন। আসলে শুল্ক-কর কমিয়ে কিংবা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে পণ্যমূল্য কমানো কখনোই সম্ভব নয়। পণ্যমূল্য কমাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষক ও খাদ্যের অন্যান্য উৎপাদককে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারসাজি থেকে রক্ষা করে সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা।
দুই. পিপিআরসির জরিপ অনুযায়ী শিক্ষার পেছনে নাগরিকেরা ব্যয় করতে পারছে তাদের আয়ের মাত্র ৭ দশমিক ২৯ শতাংশ, যা তাদের চিকিৎসা-ব্যয়ের চেয়েও কম। বিষয়টি এমন নয় যে শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয় রাষ্ট্র বহন করছে বিধায় ব্যক্তিকে শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। বরং রাষ্ট্র ও ব্যক্তি কারও কাছেই শিক্ষাব্যয় তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। যে রাষ্ট্র বা তার জনগণের কাছে শিক্ষা একটি অগ্রাধিকারমূলক খাত নয়, সে দেশ যে শিগগিরই পিছিয়ে পড়বে, তাতে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই। আমার মতে পিপিআরসি জরিপ থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যের মধ্যে শিক্ষার পেছনে এত অল্প ব্যয়ের চিত্রটিই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক। সদিচ্ছা থাকলে খাদ্যমূল্য হয়তো নানা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কমিয়ে বা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষা ছাড়া মাথা গুনতির মানবসম্পদ বাড়িয়ে একটি জাতিকে কখনোই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মানহীন সনদসর্বস্ব শিক্ষায় শিক্ষিত জাতির সদস্যদের একটি বড় অংশের কাজই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা ও রাজনৈতিক কলহবিবাদে লিপ্ত থাকা। দেশে ৫৪ বছর ধরে চলে আসা ক্ষমতা কাড়াকাড়ির এই যে বিবাদ, তা বহুলাংশে বস্তুত এই শিক্ষাহীনতা বা মানহীন শিক্ষারই ফল। শিক্ষায় ব্যয় বাড়িয়ে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ব্যয়, গুণগত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে না পারলে বাংলাদেশের পক্ষে তার চলমান ধারার হানাহানি থেকে বেরিয়ে আসা কখনোই সম্ভব হবে না।
তিন. জরিপ বলছে, চিকিৎসার পেছনে মানুষ ভগ্নাংশের হিসাবে শিক্ষার চেয়ে কিছুটা বেশি ব্যয় করলেও তা শিক্ষাব্যয়ের মতোই অপ্রতুল—মাত্র ৭ দশমিক ৫১ শতাংশ। তবে এ ক্ষেত্রে জরিপে যেটি উঠে আসেনি তা হচ্ছে, এই স্বল্প চিকিৎসাব্যয়েরও একটি বড় অংশই আবার মূল চিকিৎসাব্যয় নয়—আনুষঙ্গিক ব্যয়, যার মধ্যে রয়েছে যাতায়াত, সাময়িক আবাসন, রোগী-সহযোগীর আহার ও অন্যান্য। অর্থাৎ নাগরিকের প্রকৃত চিকিৎসাব্যয় জরিপে উঠে আসা পরিমাণের চেয়েও অনেক কম। চিকিৎসার পেছনে এত যৎসামান্য অর্থ ব্যয় করে গড়ে ওঠা একটি রুগ্ণ জাতির পক্ষে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনাময় চিন্তাভাবনায় যুক্ত হওয়া, জ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়া, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ মাত্রার অবদান রাখা ইত্যাদি কি কোনো দিনও সম্ভব?
চার. আলোচ্য জরিপের তথ্যে জনগণের জীবনযাপনের ব্যয় ও এতৎসংক্রান্ত পরিস্থিতি শহরের তুলনায় গ্রামে কিছুটা ভালো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ নগদ অর্থ ব্যয়ের বাইরে নিজের উৎপাদিত যে খাদ্য ভোগ করে, ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে তার সবটাই ও সঠিক পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর সঙ্গে লুক্কায়িত ব্যয় যোগ করা হলে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপনের প্রকৃত ব্যয় আরও অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তদুপরি গ্রামীণ পরিবারগুলোকে তার শহুরে সদস্যরা যে পরিমাণে পরোক্ষ আর্থিক সহায়তা (খাদ্য, জামাকাপড়, শহরে অবস্থানকালীন চিকিৎসাব্যয় ইত্যাদি) প্রদান করে, সেটিও এখানে ব্যয়ের হিসাবে যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। মোটকথা, গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের চেয়ে কোনো অংশেই ভালো নেই।
- ট্যাগ:
- মতামত
- অর্থনৈতিক অবস্থা
- দারিদ্র্য হার