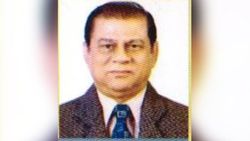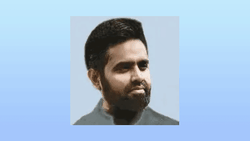ফেসবুকে যা দেখছি সব কি বিশ্বাসযোগ্য নাকি ইমপোস্টার কনটেন্ট?
১৬ জানুয়ারি ২০১৯। বুধবার। ওইদিন সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন ডিসিতে অফিস ফেরত অনেকেই এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাগলাটে শাসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন চরম নৈরাজ্য চলছিল।
শার্টডাউন কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের প্রায় অচলাবস্থা, পদত্যাগ করেছেন হাউজের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি, লস এজেলেস-এ শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলছে, নারীদের প্রতিবাদী মার্চ চলছে শহরে শহরে, হঠাৎ বেড়ে গেছে নির্বিচার গুলিবর্ষণে প্রাণহানির ঘটনা ইত্যাদি।
ট্রাম্পের এমন খামখেয়ালি কার্যক্রমে ত্যক্তবিরক্ত তিনজন প্রতিবাদকারী সংগঠক ওইদিন একটি সংবাদপত্রের ২৫ হাজার কপি বিলি করেছিলেন। এই সংবাদপত্রটি শুধু ওয়াশিংটন ডিসির বিভিন্ন সড়কেই নয় বিলি করা হয়েছিল হোয়াইট হাউজের সামনেও। বিলির সময় বলা হয়েছিলো, এটা ওয়াশিংটন পোস্ট এর বিশেষ সংখ্যা।
বিশেষ এই সংখ্যাটির আট কলামে প্রধান শিরোনাম ছিল UNPRESIDENTED। সাব-হেড ছিল TRUMP HASTILY DEPARTS WHITE HOUSE, ENDING CRISIS। এই সংবাদটি শুধু অফিস ফেরত মার্কিনিদের আকৃষ্ট করেনি, এই কপিটি আগুনের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল অনলাইন পরিসরে। চরিত্রগতভাবে যা ছিল ছদ্মবেশী ভুয়া সংবাদপত্র। যাতে প্রকাশিত হয়েছিল ভুয়া সংবাদ। একাডেমিক ভাষায় যা পরিচিত Imposter Content নামে।
জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক সংস্থা-ইউনেস্কোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই প্রকারের ভুয়া সংবাদে মূলত একটি প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যমের লোগো, রং, লেখার আকৃতি (ফন্ট) ও কাঠামো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যাতে পাঠক বা দর্শক-শ্রোতা সহজেই তা বিশ্বাস করে। যার মূল লক্ষ্য থাকে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের বিভ্রান্ত করা। সম্ভব হলে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করা।
ওয়াশিংটনবাসী ও অনলাইনে এই কপিগুলো এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রটির মুখপাত্র ক্রিস কোরাট্টি (Kris Coratti) বিশেষ বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্রিস কোরাট্টি (Kris Coratti) বলেছিলেন, We will not tolerate others misrepresenting themselves as The Washington Post, and we are deeply concerned about the confusion it causes among readers. (Washington Post online, January 17, 2019)
অর্থাৎ, আমরা অন্য কাউকে ওয়াশিংটন পোস্ট হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপন করা সহ্য করব না। এর ফলে পাঠকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
২০০৮ সালেও এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। তখন প্রভাবশালী আরেক দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর একটি সংখ্যা বেরিয়েছিল ১২ নভেম্বর ২০০৮। তখন বারাক ওবামা দেশটির প্রেসিডেন্ট এবং ইরাক যুদ্ধের অবসান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছিল।
এরমধ্যে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর ভুয়া সংখ্যা বের করা হয়। যার শিরোনাম ছিল ‘Iraq War Ends’। এই সংখ্যাটি বের করেছিলেন একদল অধিকারকর্মী, যারা কিছুটা মজার ছলেই এই কাজটি করেছিলেন। যে বিষয়কে একাডেমিক ভাষায় বলা হয় ‘Spoof Content’ বা মজার ছলে তৈরি করা Disinformation বা অপতথ্য।
- ট্যাগ:
- মতামত
- গভর্নমেন্ট শাটডাউন
- নৈরাজ্য
- ফেসবুক