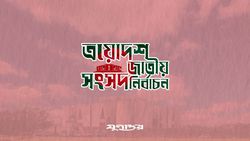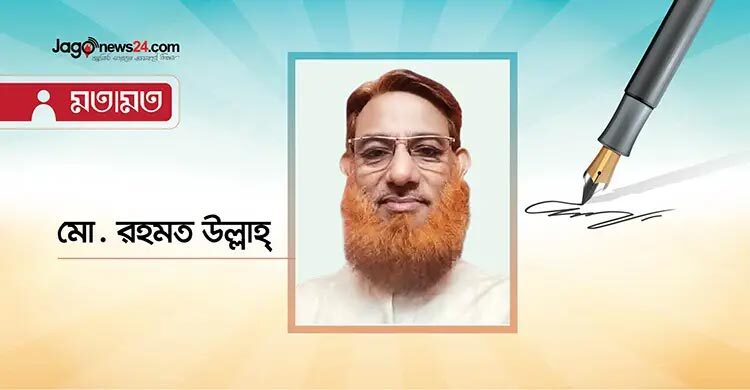প্রাকৃতিক গ্যাস কি সোনালি হাতছানি?
এক সময়ে আমরা জেনেছিলাম, ‘বাংলাদেশ গ্যাসের উপর ভাসছে’। তখন, অর্থাৎ আশি-নব্বইয়ের দশকে, এমনটি ভাবার যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। আমরা দেখছিলাম, সিলেট ও অন্যান্য টিলা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় গ্যাসের খনি পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেনে যেতে যেতে গ্যাসখনির উঁচু টাওয়ারের মাথায় আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে।
এমন চিত্র, কিংবা ভাবচিত্র, আমাদের মাথায় গেঁথে ছিল। আমরা দগ্ধ গ্যাস টিলাও দেখেছি এবং তা নিয়ে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নিরন্তর প্রতিবেদনও দেখেছি। এই ভাবনা-গাঁথার পেছনে কাজ করতো গণমাধ্যমের প্রতিবেদন। জ্বালানিবিদ্যা নিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তারা আমাদের জন্য কদাচিৎ বই লিখেছেন।
আমি জানি, ড. আ মু জহুরুল হক ‘মানুষের শক্তি’ এবং ‘শক্তি চাই’ কিংবা ড. মফিজ চৌধুরী ‘দুর্নীতি: বিপ্লব ও সমকালীন প্রসঙ্গ’ বই লিখেছিলেন আশির দশকে, যেখানে বাংলাদেশের জ্বালানি চিন্তার কিছু আলোচনা ছিল। জ্বালানি চিন্তায় দীক্ষিত করার তাগিদ সরকারের তেমন দেখা যায়নি, আজও দেখা যায় তেমন নয়। ভাবখানা এমন—যত কম জানে, তত ভক্তি, তত ভাল। জ্ঞানের শূন্যতায় অজ্ঞানতা প্রস্ফুটিত হয়—জ্বালানি-বিদ্যার জগতে বাংলাদেশে একথা সত্য।
জ্বালানি শুধু যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপার তাও নয়। এর রাজনীতিক মূল্য অপরিসীম। জ্বালানি-রাজনীতি দিয়ে সারা বিশ্ব পরিচালিত হয়। একথা এখন সবার জানা। মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেনের একটি সুলিখিত গ্রন্থ আছে, ‘গ্যাস বাংলাদেশ’, সেখানে তিনি ২০০৩ সালের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কোট করে লিখেছেন, “ওয়াশিংটন চাইছে ঢাকা গ্যাস রফতানি করুক যাতে এটি মধ্য-আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হতে পারে। এটা বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে”।
১৭ আগস্ট করা এই উক্তির মধ্য দিয়ে পরোক্ষে যে নির্দেশ প্রদানই করা হচ্ছে সেটা বুঝতে রকেট-বিজ্ঞানী হতে হয় না। ‘জিওপলিটিকস’ বলে যে জিনিসটা আমরা সচরাচর শুনে থাকি, তার একটা বড় অংশই হলো জ্বালানির বৈশ্বিক চাহিদা ও পরাশক্তিসমূহের লোভ ও নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছা। আর রয়েছে বৈশ্বিক কর্পোরেট কৌশল। এসব কৌশল আবার বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আর গবেষণার সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিঃসৃত হয়ে থাকে।
এসবের কিছু না জেনেই বাংলার মানুষ এই ভেবে স্বস্তিতে ছিল যে বিধাতা তাদের খুব কিছু না দিলেও দিয়েছেন অবারিত মাঠ, উর্বর মাটি, নদী আর পলি, দুর্বার ফসল আর মাটি-ভরা গ্যাস। কিন্তু আমাদের তেমন কেউ জোর করে বলেওনি যে, প্রাকৃতিক সম্পদ সব সময়েই সীমিত এবং তার একটা শেষ থাকে।
১৯৫৬ সালে মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ হিউবার্ট (১৯০৩-১৯৮৯) একটি পর্যবেক্ষণে বলেন যে, সব রকমের জীবাশ্ম-জ্বালানিরই উৎপাদনের একটি সর্বোচ্চ চূড়া থাকে, এরপর থেকে উৎপাদন কমতে থাকে। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মেই সঞ্চয় কমতে থাকে। অনেক দেশেই তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে কমে যাওয়া শুরু করেছে বলে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে জানা যায়।
তবে ‘হিউবার্টের পিক’ ব্যাপারটা কিন্তু প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। সেখানে সত্তরের দশকে তেলের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে (১০ মিলিয়ন ব্যারেল প্রতিদিন), এরপর ৩৫ বছর ধরে তা কমতে থাকে। কিন্তু বিশ শতকের শেষের দিকে উত্তোলন প্রযুক্তির (extraction technology) নয়া উদ্ভাবনে ‘টাইট অয়েল’ বা পরে ‘শেল অয়েল’ ইত্যাদি নানাবিধ উৎস থেকে পুনরায় তেলোৎপাদন শুরু হয় এবং তা ওই ১০ মিলিয়ন ব্যারেলের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ফলে যদি নতুন প্রযুক্তি আসে, তবে হিউবার্টের চূড়া বদলে যাবে।
কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন হিউবার্টের চূড়া ছুঁয়ে গেছে। ফলে এখন তার উৎপাদন ক্রমশ কমতির দিকে থাকবে। তাছাড়া নতুন গ্যাসক্ষেত্রের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। দুই একটির খবর শোনা গেলেও, নতুন ক্ষেত্রগুলোর ক্ষমতা, বড় গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উৎপাদনের ক্রম-অধোগতির চেয়ে বেশি নয়।
সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যাপার হচ্ছে, প্রায় এক দশক আগে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্র-সীমানা নির্ধারিত হলেও এ অঞ্চলে অফশোর প্রাকৃতিক তেল বা গ্যাসের অনুসন্ধানের কোনো দৃষ্টান্ত আমরা দেখিনি। কয়েকবার প্রচেষ্টার পর সেসব উদ্যোগ থেমে গেছে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- প্রাকৃতিক গ্যাস