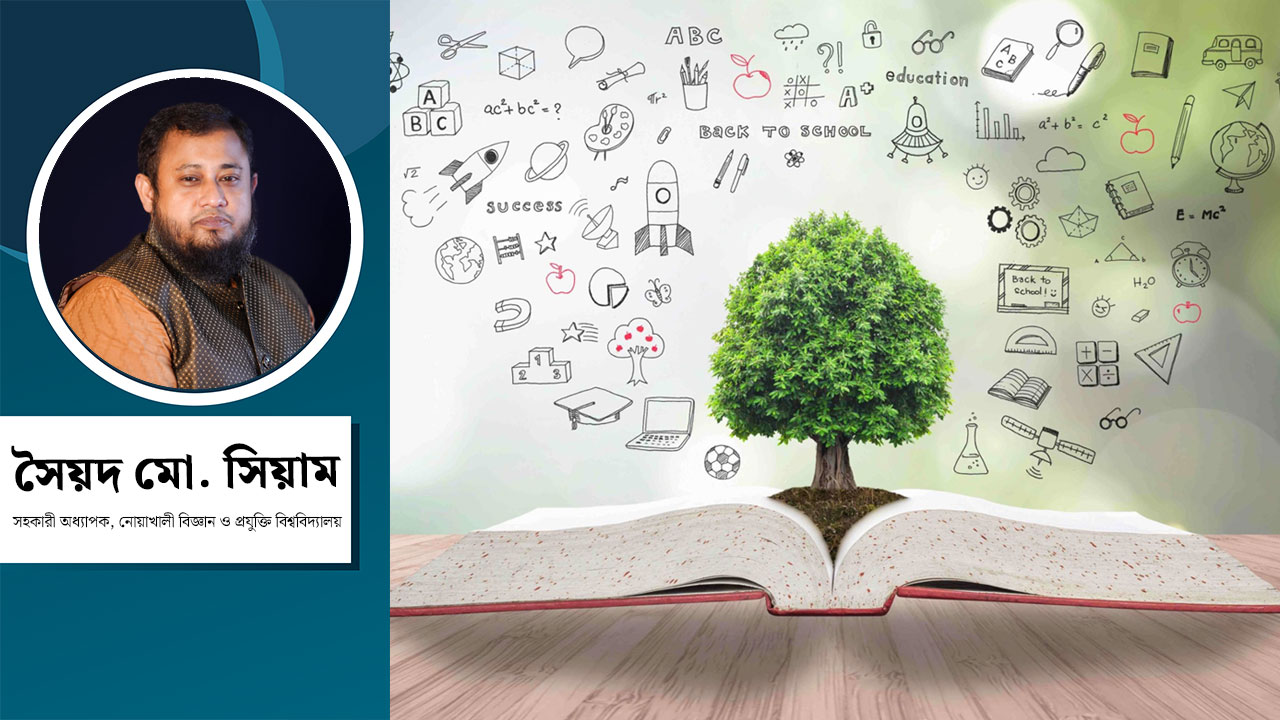কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি রাজনৈতিক কৌশল নিয়ন্ত্রণ করবে?
রাজনীতি মানব সমাজের পুরোনো ক্ষেত্রগুলোর একটি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্ষমতার বণ্টন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ—সবই রাজনীতির মূল আলোচ্য বিষয়। রাজনীতির উৎপত্তি হয়ে থাকে সংঘাত এবং অপর্যাপ্ততা থেকে। আর এই সংঘাত এবং অপর্যাপ্ততার ধারণাটি রাজনীতিকে নানাভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।
চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পর থেকে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি আজ রাজনীতিকে এক নতুন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) এখন শুধু বিজ্ঞান বা অর্থনীতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নয় বরং রাজনীতির কাঠামো, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং এমনকি রাজনৈতিক দর্শনের ভেতরেও প্রবলভাবে প্রবেশ করছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, নাকি কেবল প্রভাব বিস্তার করছে? আর এই প্রভাবকে আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করব? সেই আলোচনা এবং দর্শন নিয়েই আজকের এই লেখা।
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, রাজনীতির মূল শক্তি হলো তথ্য ও মতাদর্শ। অতীতে রাজনৈতিক প্রচারণা সীমিত ছিল সমাবেশ, পোস্টার, লিফলেট বা সংবাদমাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল যোগাযোগমাধ্যম রাজনৈতিক বার্তা প্রচারের প্রধান হাতিয়ার।
এ জায়গায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে নাগরিকদের কল্যাণে নানামুখী প্রয়োগ ঘটাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আসামি শনাক্ত করার ক্ষেত্রেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাচ্ছে।
ফেসবুক, টুইটার, টিকটক কিংবা ইউটিউবের অ্যালগরিদম নির্ধারণ করে দেয় কোন বার্তা কোন শ্রোতার কাছে পৌঁছাবে। এই অ্যালগরিদমগুলো আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তৈরি গাণিতিক মডেল। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই অ্যালগরিদম বুঝতে পারে, তারা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী লক্ষ্য করে বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে। এভাবে ভোটারদের মনোভাব নিয়ন্ত্রণের এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে।
আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কিংবা ব্রেক্সিট গণভোটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ডেটা বিশ্লেষণ (যেমন কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারি) কীভাবে নির্বাচনী ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের অনলাইন আচরণ বিশ্লেষণ করে তাদের রাজনৈতিক পছন্দ অনুমান করতে সক্ষম এবং সেই অনুযায়ী ‘মাইক্রো-টার্গেটিং’ করা সম্ভব হয়। শুধু ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, ক্রমাগতভাবে এ ধরনের প্রভাব আজকের দিন পর্যন্ত অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে—এমনকি বেড়েই চলেছে।