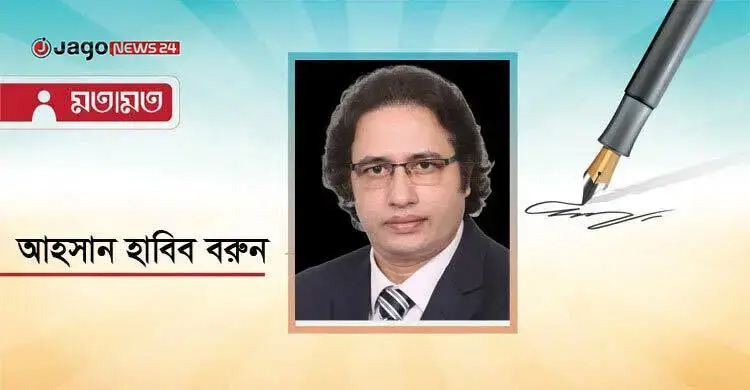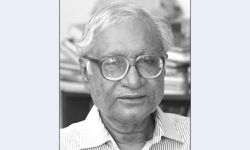মনোযোগ অর্থনীতি ও বাংলাদেশের বাস্তবতা
মানুষের মনোযোগকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখার ধারণাটি নতুন কিছু নয়, তবে ডিজিটাল যুগে এটি এক ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। অ্যাটেনশন ইকোনমি বা ‘মনোযোগ অর্থনীতি’, এমন একটি কাঠামো যেখানে মানুষের মনোযোগকে একটি দুষ্প্রাপ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং একে ব্যবহার করে মূল্য তৈরির চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশে এ ধারণাটি দিন দিন আরও গভীরভাবে প্রসারিত হচ্ছে, যেখানে অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, প্রযুক্তি এবং গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এক জটিল সংকটে পরিণত হয়েছে।
অ্যাটেনশন ইকোনমির গোড়াপত্তনে বেশ কয়েকজন চিন্তাবিদের নাম উঠে আসে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও মনোবিজ্ঞানী হেরবার্ট সাইমন, যিনি ১৯৭১ সালে বলেছিলেন, ‘একটি তথ্যসমৃদ্ধ সমাজ মনোযোগের দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, যেখানে মনোযোগই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।’ তার এই দূরদর্শী উক্তিটি আজকের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। সাইমনের মতে, মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত, এবং এই সীমাবদ্ধতার মাঝে যখন অতিরিক্ত তথ্য প্রবাহিত হয়, তখন মনোযোগ একটি দুর্লভ সম্পদে পরিণত হয়।
এ ধারণার ভিত্তিতেই আজকের ফেসবুক, টিকটক বা ইউটিউবের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো গড়ে উঠেছে, যাদের মূল লক্ষ্যই হলো যত বেশি সম্ভব ব্যবহারকারীর সময় ও মনোযোগ দখল করে রাখা। এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহারকারীর মনোযোগ কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে তাদের পণ্যের প্রচার করে, যা তাদের আয়ের প্রধান উৎস।
এই ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করেন অর্থনীতিবিদ থিওডোর স্কিৎজিন, যিনি ১৯৭৬ সালে তার "Attention and the Structure of Consumption" গ্রন্থে মনোযোগকে একটি ভোগ্য সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার ভাবনা আজকের বাংলাদেশে স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেখানে ব্যবহারকারীদের সময় কার্যত বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি হচ্ছে এবং এই বিক্রি থেকেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর আর্থিক সাফল্য আসছে।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রির আকার ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যেখানে "ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং" একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। ব্র্যান্ডগুলো তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য বিপুল সংখ্যক ফলোয়ার থাকা ব্যক্তিদের ব্যবহার করে, যারা তাদের দর্শকদের মনোযোগকে পণ্যে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ব্যবহারকারীর মনোযোগ একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়, যা সরাসরি অর্থনৈতিক মূল্যে পরিমাপ করা যায়।
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যাটেনশন ইকোনমির ভিত্তি গড়ে উঠেছে বি.এফ. স্কিনারের অপারেন্ট কন্ডিশনিং থিওরির (১৯৩৭) ওপর। স্কিনার বলেন, যখন কোনো আচরণের পর ফলাফল ইতিবাচক হয়, তখন সেই আচরণ বারবার পুনরাবৃত্তি হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীদের 'লাইক', 'শেয়ার', 'কমেন্ট', 'নোটিফিকেশন'-এর মাধ্যমে এক ধরনের ডোপামিন রিওয়ার্ড লুপ তৈরি করে। এই লুপ ব্যবহারকারীদের ক্রমাগত প্ল্যাটফর্মে নিযুক্ত রাখে, কারণ তারা প্রতিটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য এক ধরনের মানসিক সন্তুষ্টি অনুভব করে।
বাংলাদেশের তরুণ সমাজের একটি বড় অংশ এই রিওয়ার্ড সাইকেলে আটকে পড়েছে, যার ফলে গড়ে প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সময় ৫-৭ ঘণ্টায় পৌঁছেছে। এই অতিরিক্ত সময় ব্যয় কর্মক্ষমতা, ঘুম, মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যুবকদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাদের শেখার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের সামগ্রিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
অর্থনীতির প্রথাগত তত্ত্ব অনুযায়ী, উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূল্যবান উৎপাদন উপাদানগুলোর মধ্যে শ্রম, মূলধন ও ভূমি প্রধান। কিন্তু অ্যাটেনশন ইকোনমি এই কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আজকের দিনে মনোযোগ নিজেই একটি উৎপাদন উপাদানে পরিণত হয়েছে, যার মূল্য নির্ধারণ করে ক্লিক রেট, এনগেজমেন্ট টাইম এবং কনভার্সন রেশিও। অর্থাৎ, একজন ব্যবহারকারী কতক্ষণ একটি প্ল্যাটফর্মে সময় কাটাচ্ছেন, কতবার ক্লিক করছেন, এবং একটি বিজ্ঞাপনে কতজন ব্যবহারকারী সাড়া দিচ্ছেন, তার ওপর ভিত্তি করে মনোযোগের মূল্য নির্ধারিত হয়।
- ট্যাগ:
- মতামত
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি