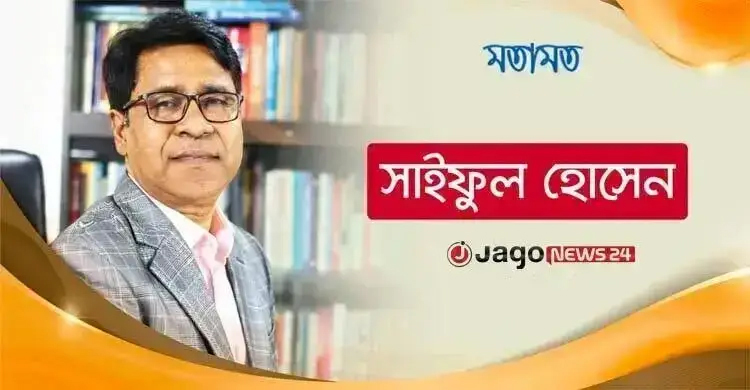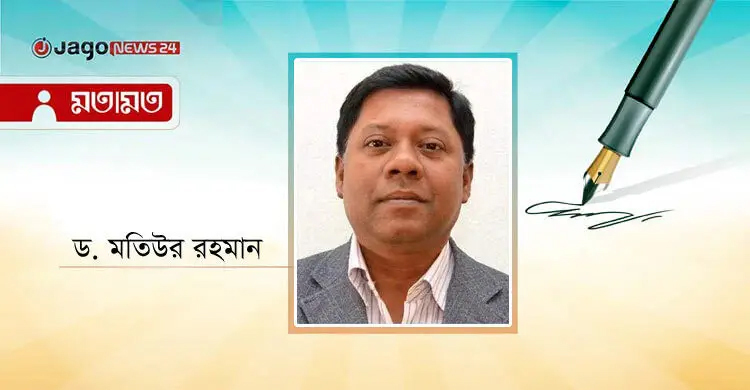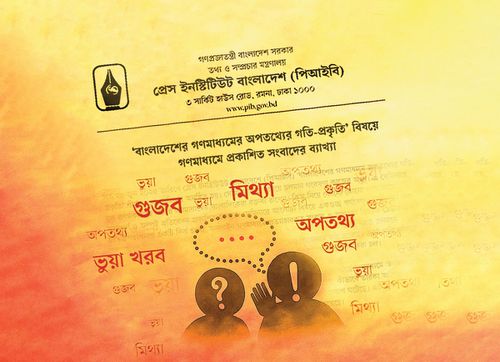
সংবাদ প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে ‘বিভ্রান্তি’ কেন
আমরা যাঁরা একাডেমিক গবেষণা করছি, তাঁরা সব সময় বিজ্ঞান সাময়িকী চর্চার মধ্যে থাকি। বলতে গেলে দিনের শুরুটা হয় এসব সাময়িকীতে কী কী গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, কী কী ডেটা উপস্থাপন হচ্ছে, তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে।
এর কারণ হলো, অনেক সময় দেখা যায়, নিজেদের গবেষণার বিষয় পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তের গবেষকদের সঙ্গে ‘ওভারল্যাপ’ হয়ে যায়। তাই নিজেদের কাজগুলো এগিয়ে নিতে ও গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করতে একাডেমিশিয়ানদের ‘বিজ্ঞান সাময়িকী’ চর্চার কোনো বিকল্প নেই।
এসব সাময়িকী চর্চা করতে গেলে অধিকাংশ সংস্করণে আমরা কিছু গবেষণার সংশোধনী অথবা রিট্রাকশন দেখতে পাই। দেখা গেল, বেশ কয়েক বছর আগে এক ব্যক্তি গবেষণা করেছেন, তা প্রকাশিতও হয়েছে; কিন্তু পরবর্তী সময় অন্য কোনো গবেষক সেই গবেষণায় ভুল পান।
যদি শব্দগত ভুলের মাত্রা কম হয়, সে ক্ষেত্রে সেসব শব্দ সংশোধন করে ওই সাময়িকীর সম্পাদক বরাবর চিঠি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তা সংশোধনের জন্য নতুন ওয়েবসাইটের লিংক জার্নালগুলোয় পাঠকের কাছে তুলে ধরা হয় ‘কৈফিয়ত’ আকারে।
অন্যদিকে যদি গবেষণাপ্রবন্ধটিতে প্লেজিয়ারিজম হয়, অর্থাৎ অন্যের গবেষণার আইডিয়া, ডেটা কিংবা বাক্য হুবহু বা আংশিক কৃতিত্ব দেওয়া ছাড়া চুরি করা হয়, ঘষামাজা করা হয়; তাহলে সেটি একাডেমিক ‘ডিজইন্টেগ্রিটি’র মধ্যে পড়ে এবং সেই প্রবন্ধ প্রত্যাহার বা রিট্রাকশনের জন্য জার্নালগুলোয় আবেদন জানানো হয়।
পরবর্তী সময় বেশ কিছু ধাপ পেরিয়ে, জার্নালগুলো সেই প্রবন্ধ প্রত্যাহারের জন্য তাদের স্বীয় ওয়েবসাইটে নোটিশ দেয়, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের কৈফিয়তনামাও থাকে। এসব ভুলের জন্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলো নৈতিকতার দণ্ডে শাস্তি প্রদান করে।
এগুলোই হলো গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণার ভুলভ্রান্তি নিয়ে একাডেমিক নৈতিকতার সংক্ষিপ্ত আকারের আলোচনা। সারা দুনিয়ার গবেষকেরা এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গবেষণা করে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করছেন।

একাডেমিক গবেষণাপ্রবন্ধ ও প্রতিদিনের সংবাদগুলোর মধ্যে মূল তফাত হলো ‘পাঠক’। একাডেমিক প্রকাশনাগুলোর টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। যে কারণে এসব প্রবন্ধের ভাষা ও শব্দশৈলী অনেকটাই পাঠ্যপুস্তকের ভাষার মতো হয়ে থাকে। কারণ, এসব গবেষণার নির্যাসই পাঠ্যবইয়ে চলে আসে।
অন্যদিকে সংবাদপত্র কিংবা সংবাদমাধ্যমগুলোর ভোক্তা হচ্ছেন সাধারণ পাঠক। এখানে সব শ্রেণির পাঠকদের মনোবৃত্তকে ধারণ করে সংবাদ তৈরি করা হয়, প্রকাশও করা হয়।
তাই সংবাদমাধ্যমগুলো সহজবোধ্য ও প্রাসঙ্গিক বাক্যে ঘটনাপ্রবাহ পাঠকদের জানায়। এটা জানাতে গিয়ে সংবাদকর্মীদের যেমন ঘটনাস্থলে থাকতে হচ্ছে, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ভুক্তভোগী, অভিযুক্ত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে, তেমনি দ্রুততার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করতে হচ্ছে।
এই পরিবেশনায় অনেক সময় দেখা যায়, সংবাদটিতে ‘তথ্যগত’ ভুল থাকছে কিংবা মূল ঘটনার সঙ্গে উপস্থাপনায় ত্রুটি থাকছে। পেশাদার সংবাদমাধ্যমগুলো যখনই সেই ভুল নিজেদের নজরে আনতে পারছে কিংবা পাঠক বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে জানতে পারছে যে পরিবেশিত সংবাদটিতে ত্রুটি আছে, তখন তা সংশোধন করে পুনরায় প্রকাশ করছে।
ছাপা পত্রিকায় কিছুটা ঝক্কিঝামেলা থাকলেও অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলোয় সংবাদ সংশোধনের অবারিত সুযোগ থাকায়, সেই ভুলগুলো অনায়াসে সংশোধন করা যায়। তথ্যসচেতন পাঠকেরা মূল সংবাদ উত্থাপনের সময় আর সর্বশেষ ‘আপডেট করার সময়’ মিলিয়ে বুঝতে পারেন সংবাদটি কখন সংশোধিত কিংবা সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইন গণমাধ্যমগুলো এভাবে চলছে।
তবে এসব পরিবেশিত সংবাদের বিষয়ে যদি ‘গুরুতর’ ত্রুটি থেকে যায় কিংবা কেউ অভিযোগ করে যে সংবাদটি ভুল কিংবা মিথ্যা পরিবেশিত হয়েছে, তাহলে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমগুলো সেই সংবাদ সংশোধনের পাশাপাশি একটি ‘এডিটরিয়াল নোট’ বা সম্পাদকীয় বক্তব্য জুড়ে দেয়, যাতে পরবর্তী সময়ে যে পাঠক সংবাদটি পড়বেন, তিনি সংবাদটির বিষয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ বুঝতে সক্ষম হবেন।
- ট্যাগ:
- মতামত
- প্রত্যাহার
- সংবাদ
- বিভ্রান্তি