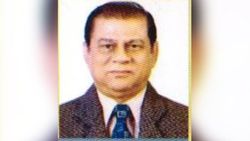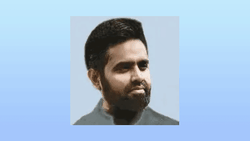পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার কেন দরকার
সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়—শুধু গবেষণায় নয়, মানবিক দায়বদ্ধতায়ও। যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখিয়ে দিয়েছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল জ্ঞানচর্চার স্থান নয়; বরং তা ন্যায়, স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বেরও প্রতীক। অথচ আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একের পর এক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার উদাহরণে পরিণত হচ্ছে।
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়—তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণ ভিন্ন হলেও উৎস একটাই: চরম অব্যবস্থাপনা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং দীর্ঘদিনের সংস্কারহীনতা। শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হওয়া উচিত ছিল যেসব প্রতিষ্ঠানের, সেগুলো যেন রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি ও পছন্দনির্ভর নিয়োগের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় সংকট হলো শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগপ্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। প্রায় দেড় দশকে ৪৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮,৮০০ জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন, যার উল্লেখযোগ্য অংশেই দলীয় পরিচয় ও স্থানীয় রাজনীতিকদের সুপারিশই হয়েছে নিয়োগের প্রধান ভিত্তি। আজকের বাংলাদেশে মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও তাঁদের অদৃশ্য শর্ত পূরণ করতে হয়—তাঁকে এমন শিক্ষকের অধীনে পড়তে হবে, যিনি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী; তারপর চাই সেই শিক্ষকের সুপারিশ এবং স্থানীয় রাজনীতিকের অনুমোদন। এটি একধরনের অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

চূড়ান্ত অবক্ষয়ের চিত্র উঠে এসেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক উপাচার্যের ঘটনায়ও, যিনি শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা নিজস্ব প্রয়োজনে বদলে তাঁর মেয়ে ও জামাতাকে নিয়োগ দিয়েছেন। এটি শুধু একজন উপাচার্যের নৈতিক অবনমন নয়—এটি একটি প্রজন্ম, একটি জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে এমন পারিবারিক সুবিধা আর স্বজনপ্রীতি কেবল প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজকে পুরোপুরি তলিয়ে দিতে পারে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বেড়েছে, কিন্তু মান ও প্রয়োজনীয় সংস্কার নেই। নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে কর্মবাজারের চাহিদা না দেখে, বরং পছন্দের ব্যক্তিকে চাকরি দিতে। অনেক বিভাগের পাঠ্যসূচি অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। ফলে পাস করা শিক্ষার্থীরা শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না, বাড়ছে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা।
গবেষণার পরিবেশ আরও শোচনীয়। গত বছর ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮৮ কোটি টাকা। দেশের জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বিবেচনায় এ বরাদ্দ এককথায় হাস্যকর। অথচ বিটিভির আধুনিকায়নে সরকার ১,৮৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করে। বাজেটের অপ্রতুলতার অজুহাতে গবেষণায় অব্যাহত দুর্বলতা চলছে; আর সরকারের তরফ থেকে এ দুরবস্থা কাটানোর তেমন কোনো কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়নি।
শিক্ষাব্যবস্থার একধরনের নৈতিক ও আদর্শগত দেউলিয়াপনা এখন সর্বত্র। প্রশ্ন জাগে, আমরা সংস্কার বলতে আসলে কী বুঝি? শুধুই কিছু পদক্ষেপ, নাকি আদর্শিক এক বিপ্লব? সংস্কার মানে কেবল পদক্ষেপ নয়, এটি হতে হবে দর্শনভিত্তিক এবং জবাবদিহিমূলক।
- ট্যাগ:
- মতামত
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়