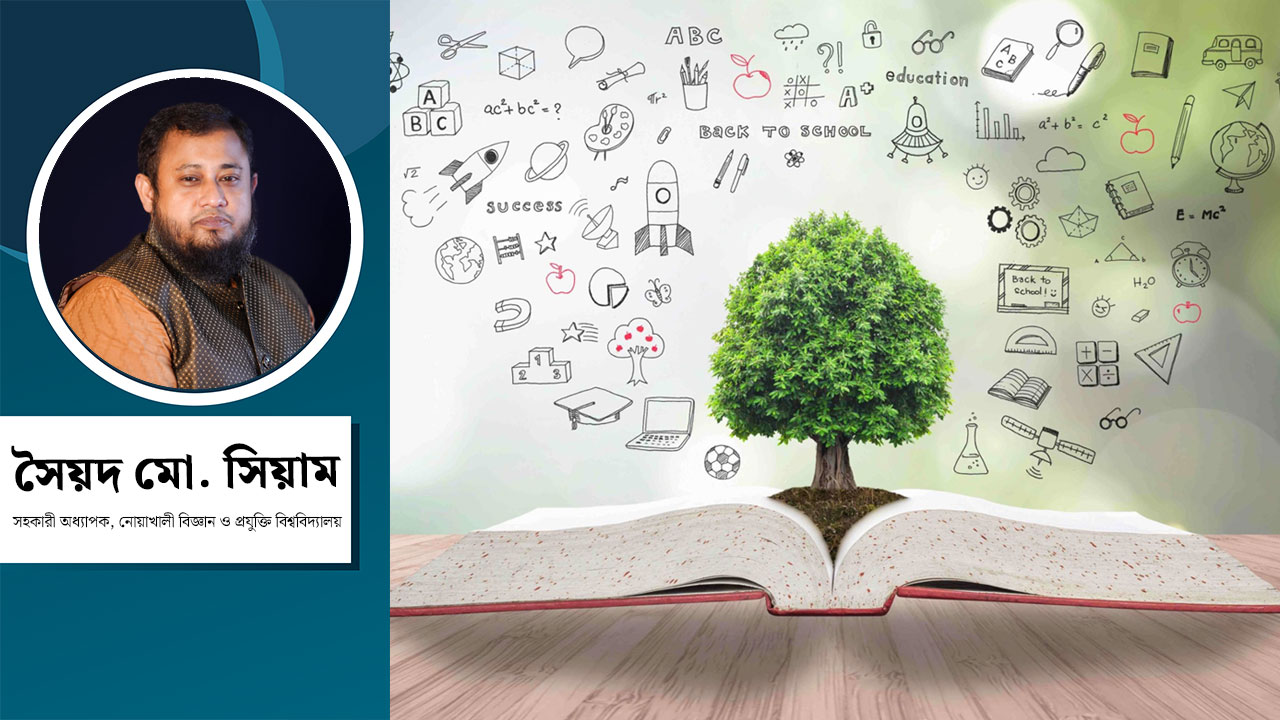প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে অর্থনৈতিক খাতের দায়
পঞ্চাশের দশকে আবিষ্কৃত প্লাস্টিক একসময় আধুনিকতার প্রতীক ছিল। সাশ্রয়ী, বহুমুখী ও টেকসই এই উপাদান বিশ্বজুড়ে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা থেকে শুরু করে ঘরোয়া ব্যবহারে এক অনিবার্য জায়গা করে নেয়। কিন্তু কৃত্রিম এই বস্তু যখন বিপুল হারে উৎপাদিত হয়ে ব্যবহারের পর ব্যবস্থাহীনভাবে পরিবেশে মিশতে থাকে, তখন সেটি এক বৈশ্বিক সংকটে রূপ নেয়।
প্লাস্টিক এখন শুধু শহরের ড্রেন বা সাগরের পাড়েই নয়, মানুষের খাদ্যচক্রে, এমনকি রক্ত ও হৃৎপিণ্ডে জায়গা করে নিচ্ছে। ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) তাই ‘প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করুন’ শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে আহ্বান জানিয়েছে, তা নিছক প্রতীকী কোনো আয়োজন নয়, বরং এটি সময়ের এক কঠিন বাস্তবতা।
বিগত সাত দশকে বিশ্বে প্লাস্টিক উৎপাদন বেড়েছে কয়েক শ গুণ। প্রতিবছর প্রায় ৪৫ কোটি টন প্লাস্টিক উৎপন্ন হচ্ছে, যার ৪০ শতাংশই একবার ব্যবহারযোগ্য। সেগুলোর বিরাট অংশই শেষ পর্যন্ত জমা হয় প্রকৃতিতে—নদী, সাগর, বন কিংবা উন্মুক্ত জমিতে—যেখানে তা শত শত বছর অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এসব প্লাস্টিক ক্ষয়ে ক্ষয়ে পরিণত হয় মাইক্রোপ্লাস্টিকে এবং তা সহজেই জলজ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে এবং খাদ্যচক্র পেরিয়ে মানুষের শরীরেও ঢুকে পড়ে।
গবেষণা বলছে, একজন মার্কিন নাগরিক বছরে প্রায় এক লাখ মাইক্রোপ্লাস্টিক–কণা গ্রহণ করেন খাবার ও শ্বাসের মাধ্যমে। এসব কণায় থাকা রাসায়নিক পদার্থ, যেমন বিসফেনল বা থ্যালেটস শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, বন্ধ্যত্ব, স্নায়বিক ব্যাধি এমনকি ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এসব কণা মানুষের রক্ত, প্ল্যাসেন্টা এমনকি হৃদ্যন্ত্রেও শনাক্ত হয়েছে। এটি একটি ভয়ংকর স্বাস্থ্যঝুঁকির সংকেত।
তবে মানবদেহের ঝুঁকি ছাড়াও প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব পড়ছে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে। ইউনেসকোর হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর অন্তত ১০ লাখ সামুদ্রিক পাখি এবং ১ লাখ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাস্টিক খেয়ে বা প্লাস্টিকে জড়িয়ে মারা যাচ্ছে। বৃহৎ সমুদ্রের ওপর দিয়ে একেকটি ‘প্লাস্টিক দ্বীপ’ ভেসে বেড়াচ্ছে, যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে ৮০ হাজার টনের এক বিশাল আবর্জনার স্তূপ, যাতে রয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিকের টুকরা।
প্লাস্টিক দূষণের একটি বড় পরোক্ষ ক্ষতি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। প্লাস্টিক মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে তৈরি হয় এবং এর উৎপাদন, পরিবহন ও ধ্বংসের প্রতিটি স্তরেই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়।
গবেষণা বলছে, বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক উৎপাদন থেকে বছরে ২ দশমিক ৮ গিগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হবে, যা বৈশ্বিক কার্বন সীমা (৪২০-৫৭০ গিগাটন) বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
এ সংকট থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। দেশে প্রতিবছর প্রায় আট লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি উৎপন্ন হয় শুধু ঢাকা শহরে। এসব বর্জ্যের অর্ধেকেরও কম পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থায় ফিরে আসে, বাকিগুলো শহরের ড্রেন, খাল, নদীতে জমা হয়ে পানিনিষ্কাশন ব্যাহত করে এবং বন্যা বা জলাবদ্ধতার জন্য দায়ী হয়ে ওঠে।
জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এখনো অনেক পথ বাকি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- প্লাস্টিক দূষণ


-69890d3d62cc6.jpg)