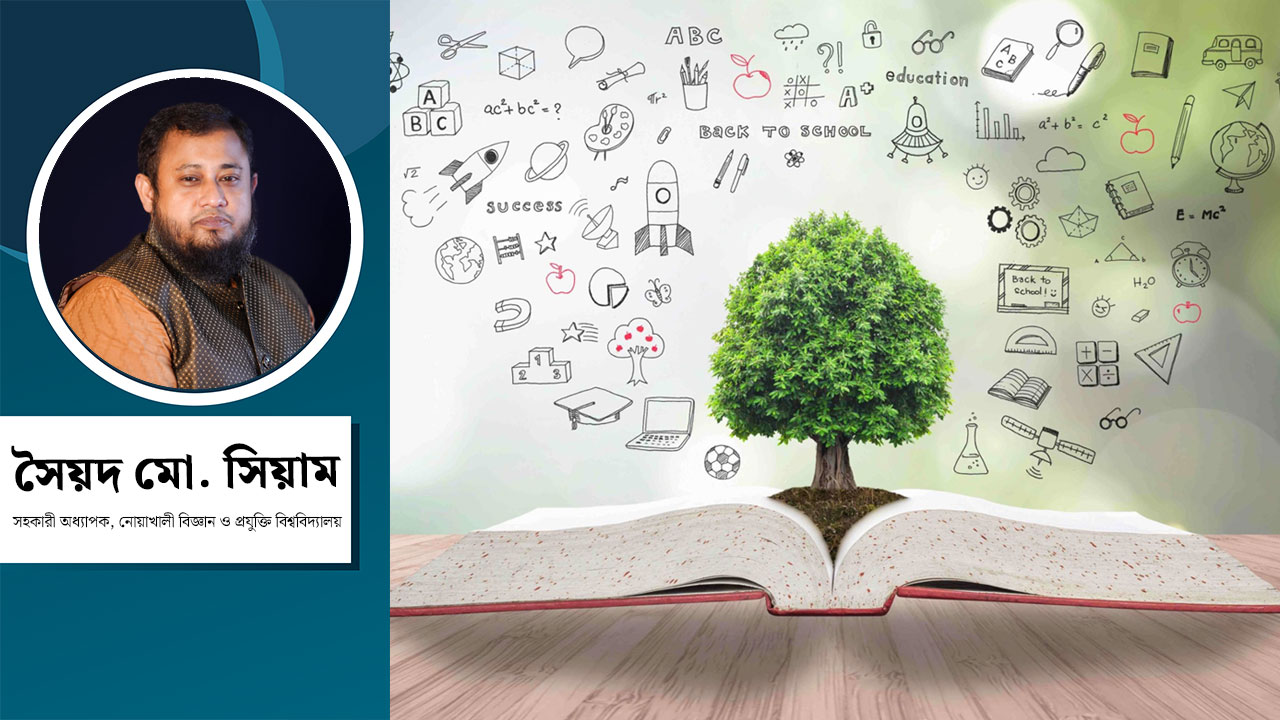চাহিদাকে যেন বদঅভ্যাস বানিয়ে না ফেলি
গত দুঃসহ রেজিমের পতনের আগে ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সেই ঐক্য যে বিজয় অর্জনের পর আর আগের মতো থাকল না, এর কারণ এবং কী হওয়া উচিত ছিল, সেসব বিষয় একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।
দ্বন্দ্বতত্ত্বের (dialectics) নিয়মে বিজয়ের পর রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য কেন ভাঙল? দ্বন্দ্বতত্ত্ব বলছে, একটি বিশেষ সময়ে সমাজে একটা প্রধান দ্বন্দ্ব (Principal contradiction) থাকে এবং থাকে অনেক অপ্রধান দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব ছাড়া শুধু সমাজ নয়, বস্তুরও অস্তিত্ব থাকে না। দ্বন্দ্ব না থাকলে বরং সংশ্লিষ্ট সমাজটি হাঁসফাঁস করতে থাকে-দ্বন্দ্ব কই, দ্বন্দ্ব কই? এবং সবচেয়ে বড় কথা, দ্বন্দ্বই বিকাশের শর্ত, দ্বন্দ্ব ছাড়া সমাজ বিকশিত হতে পারে না।
তো গত বছরের ৫ আগস্টের আগে সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কর্তৃত্ববাদী শাসন বনাম বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র-জনতার ঐক্য। ৫ আগস্টের অপরাহ্নে এই দ্বন্দ্বের নিরসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি নতুন সমাজে রূপ নেয়। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে এই নতুন সমাজে নতুন করে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে হবে। ফলে বিজয় অর্জন হতে না হতেই রাজনৈতিক দলগুলো, এমনকি ছাত্রসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল। অসুবিধা ছিল না, যদি এসব দ্বন্দ্ব অবৈরীমূলক (non-antagonistic) হতো। কিন্তু দ্বন্দ্বগুলো এত বৈরীমূলক হয়ে পড়ল যে, সমাজে দেখা দিল অস্থিরতা এবং এই অস্থিরতা উঠে গেল চরমে। আমরা যারা রাজনীতিনিরপেক্ষ মানুষ, তারা তো চাইলেই দ্বন্দ্বহীন সমাজ পাব না, তবে আমরা দ্বন্দ্বগুলো অবৈরীমূলক দেখতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর সব উন্নত দেশ, এমনকি অনেক অনুন্নত দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব থাকে, তা অবৈরীমূলক। আমাদেরটা হয়ে গেল বৈরীমূলক। বৈরীমূলক দ্বন্দ্বের কারণেই রাজনীতি থেকে উঠে যাচ্ছে যুক্তি, বিবেচনাবোধ ও শুভচিন্তা। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের, এমনকি ছাত্রসমাজও নানা অংশে বিভক্ত হয়ে পরস্পর সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।
আমার কাছে কখনো কখনো মনে হয়, আমাদের কোনো রাজনৈতিক সংকট নেই, সংকটটা আসলে নৃতাত্ত্বিক (anthropological)। আমরা সম্ভবত মিলেমিশে থাকার জন্য জন্ম নিই না, হয়তো নিজের স্বার্থ না থাকলে ভালো কিছু গ্রহণ করার মানসিকতাও জন্মসূত্রে পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্তা, বাংলার গভর্নর জেনারেল জন শোর আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসংবলিত একটি গোপন চিঠি বা দলিল পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে, যেখানে আমাদের সম্পর্কে লেখা ছিল একগাদা নেতিবাচক মন্তব্য। আমরা হয়তো বলতে পারি, ঔপনিবেশিক একজন শাসকের কী অধিকার আছে আমাদের মতো একটি মহান জাতি সম্পর্কে বাজে কথা বলার! কিন্তু সেই দলিলের কথাগুলো যদি আজ এত বছর পরও আমরা মিলিয়ে দেখি, তাহলে কেউ সহজে সেসব কথাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। অথবা আমাদের স্বল্পকালীন ভালোত্বকেই (৫ আগস্টের পূর্ববর্তী কয়েক দিন) কি রবীন্দ্রনাথ ছন্দবদ্ধ করেছেন এভাবে : স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারি আনন্দ! তবে কি একটি সুসভ্য জাতি দেখার জন্য আমাদের ডাচ ও ডেনিশদের মতো অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েক শতাব্দী? হ্যাঁ, এককালের জলদস্যু ও অপরাধপ্রবণ এ দুই জাতি এখন হিংসা করার মতো সুসভ্য।
গত রেজিমের পতনের পর একটা শব্দ খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে : সংস্কার। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমরা যাতে আগামী দিনগুলোয় মোটামুটি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশে বাস করতে পারি, সেই লক্ষ্যে এই সংস্কারের কাজ চলছেও বটে। কিন্তু এটা এক বড় প্রশ্নই বলতে হবে, কী লাভ হবে এই সংস্কার দিয়ে, যদি না আমাদের রাজনৈতিক মানস ঠিক হয়। দেখুন, আমরা চেয়েছি একটি গণতান্ত্রিক রংধনু (rainbow) সমাজ, যেখানে রংধনুর সাত রঙের মতো বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে সমাজটাকে এগিয়ে নেবে, মতাদর্শের ভিন্নতা কাউকে আগ্রাসী করে তুলবে না; অর্থাৎ পলিটিক্স অব অ্যাকোমোডেশন অথবা পলিটিক্স অব অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে সবাই সহনশীল আচরণ করবে। এই সহনশীলতা গড়ে তুলবে একটি রংধনু পার্লামেন্ট। সংস্কারগুলোর লক্ষ্যও ছিল তাই। কিন্তু এখন বিশ্বাস করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে যে, সাংঘর্ষিক রাজনীতির মধ্য থেকে সংস্কার কার্যক্রম দিয়ে রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে মেরামত করা যাবে। অন্যকে যত কঠিন গালিই দিই না কেন আমরা, আমার কাছে অন্যকে বলা সবচেয়ে খারাপ কথাটি হলো, ‘আমি তোমার ওপর নির্ভর করি না।’ ছাত্রসমাজের ওপর আমরা অশেষ নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু এ এক বড় ট্র্যাজেডি, তাদের ওপর নির্ভরতার সূচক ক্রমেই নিুগামী হয়ে পড়ছে।
এ কলাম যখন লিখছি, তখন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সেনাপ্রধানের একটা ‘মন খারাপ করা’ দূরত্ব লক্ষ করছি আমরা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের চেয়ে এই দূরত্ব আরও বেশি বিপজ্জনক। এটাকে এখন আমরা সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব বলতে পারি। কেউ কেউ বলছেন, সেনাপ্রধান এমন একটি বক্তৃতা করতে পারেন কিনা, তিনি তার এখতিয়ারের বাইরে চলে গেছেন বলেও মন্তব্য করছেন অনেকে। তাদের মতে, সেনাপ্রধান যখন বলছেন তিনি অভিভাবকহীন, তখন তিনি সরকারকেই অস্বীকার করছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে যেহেতু সেনাবাহিনী ছিল এক বড় স্টেকহোল্ডার এবং সেনাপ্রধান জনগণকে তার ওপর আস্থা রাখার কথা বলেছিলেন, তাই সমাজ যখন চরমভাবে অস্থির হয়ে পড়েছে, অভ্যুত্থানের স্পিরিট এখন আর কেউ ধারণ করছে না, তাই তার বর্তমান অবস্থানকে যৌক্তিক মেনে নেওয়া যেতে পারে। সেনাপ্রধানের বক্তব্যের পর প্রধান উপদেষ্টা নাকি অভিমানের সুরে পদত্যাগেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বরং করিডর, নির্বাচন ও মব সন্ত্রাস, এই তিন বিষয়ে সেনাপ্রধানের অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারেন। এই মতবিনিময়ে সেনাপ্রধানও থাকতে পারেন বৈকি। সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর বৈরীমূলক সম্পর্ক উন্নত দেশগুলোয় আমরা কল্পনাও করতে পারি না।
একটা জাতি কোনোভাবেই সার্বক্ষণিক টেনশনে থাকতে পারে না। মতপার্থক্য একটা সমাজের প্রাণ; কিন্তু পার্থক্যটা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সমাজের চতুর্দিকে বিপদের সাইরেন বাজতে থাকে। পানি প্রয়োজনীয়; কিন্তু বন্যা? বাতাস প্রয়োজনীয়; কিন্তু ঘূর্ণিঝড়? আগুন প্রয়োজনীয়; কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত? চাহিদাকে আমরা যেন বদঅভ্যাসে পরিণত না করি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- রাজনৈতিক দল
- সরকার পতন
- জাতীয় ঐক্য


-69890d3d62cc6.jpg)