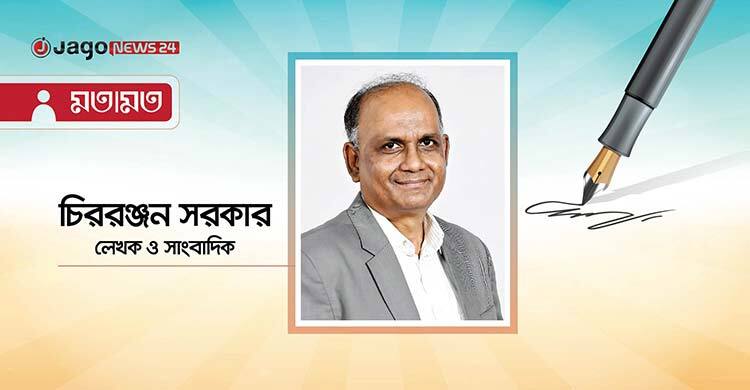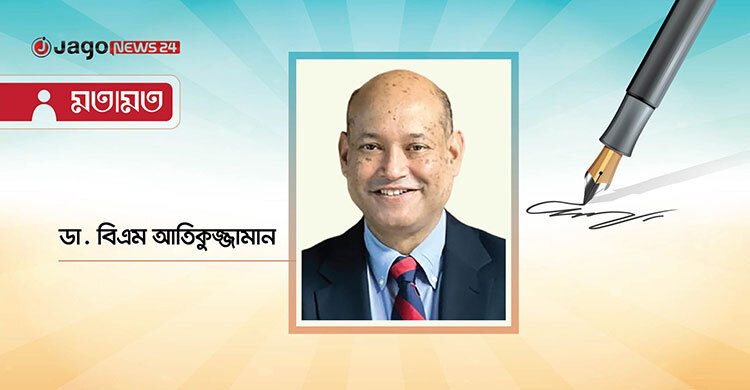ভোটের রাজনীতি বনাম শিক্ষাব্যবস্থা
অশিক্ষিত ভোটার স্বার্থান্বেষী শাসকদের প্রথম পছন্দ। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে এই ভূখণ্ডে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াস কখনোই কাউকে নিতে দেখা যায়নি। না ক্ষমতাসীন শাসক, না ক্ষমতাবান সেনাবাহিনী, না বিপুল জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল কেউ এগিয়ে আসেনি দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে অন্তত একটি নিরপেক্ষ ও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। এ দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই কোনো না কোনোভাবে বিতর্কিত আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানটির নাম নির্বাচন কমিশন। ক্ষমতায় আসতে হলে, নির্বাচনে জিততেই হবে এবং জিততে হবে ভোটারদের সরাসরি ভোটে। কোনোভাবেই জনগণের ম্যান্ডেটকে পাশ কাটানো যাবে না এই বাধ্যবাধকতা না থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বেচ্ছাচারিতার কোনো লাগাম থাকে না। সেই লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা তথা স্বৈরতন্ত্রের একমাত্র প্রতিকার হলো অভ্যুত্থান গণঅভ্যুত্থান। আর সেটা তখনই হতে পারে, যখন আপামর জনগণ পথে নেমে আসে।
ভোটকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক শাসনে ভোটার যত সচেতন হবে, শাসকের ততই সমস্যা। প্রত্যেক কথায় তাদের জবাবদিহি করতে হবে, কাজে-কর্মে স্বচ্ছতা আনতে হবে, নিয়ম মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। এ দেশের রাজনীতির এমনই পরিস্থিতি, যেখানে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ-পর্যন্ত নেতার পেছনে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থেকেও, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে নেতা কোন ঘোষণাটি দেবেন, তা জানেন না নেতার সেকেন্ড পার্সন। এমন একটা অনুমান-অযোগ্য, সদা-অনিশ্চিত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার নয়। আর এই কঠিন কাজটা আরও বেশি কঠিন হয়ে যায়, যখন জনগণ যথেষ্ট সচেতন থাকে। সেই সচেতনতার বীজ হলো শিক্ষা। অধিকাংশ মূর্খ প্রান্তিক জনগণ প্রতিবাদই করতে পারে না, অভ্যুত্থান তো দূরের কথা। ফলে যুগে যুগে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কলকাঠি নাড়তে সামান্যতম দ্বিধা করেনি এই ভূখণ্ডের কোনো সরকার। সেটা সেই সাতচল্লিশের পরের পাকিস্তান সরকারই হোক কিংবা হোক স্বাধীন দেশের সরকারগুলো। ছাত্রসমাজকে অচেতন করে রাখতে সম্ভাব্য কোনো ব্যবস্থাই বাদ রাখেনি, এ দেশের বিভিন্ন আমলের সরকার।
বিশে^র সবচেয়ে নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নেই। ক্যাম্পাসভিত্তিক স্টুডেন্ট ইউনিয়ন নেই। একেকটা হল/হোস্টেল/ডরমিটরিতে কমনরুম সম্পাদক, রান্নাঘর সম্পাদক, গণবাথরুম সম্পাদক নেই। সেসব প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি শিখতে চাইলে ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি শিক্ষার কোর্স নেয়, সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তি হয়; ভিসি-প্রফেসরদের শার্টের কলার ধরে ব্যবহারিক পরীক্ষা দেয় না– এই দেখুন স্যার, আমি কতটা রাজনীতি শিখতে পেরেছি, তার হাতেকলমে প্রমাণ দিয়ে দিলাম! উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতির বিষবৃক্ষের চাষ, সন্ত্রাস, মাদক, চাঁদাবাজি, হল দখল, নিয়োগ-বাণিজ্য, টেন্ডার-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা প্রলোভনে শিক্ষা-পরিবেশ ধ্বংস করা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষায় নকল, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, সিলেবাস নিয়ে বারবার কাটাছেঁড়া, পরীক্ষা পদ্ধতিতেই একটা গোলমাল বাধিয়ে রাখা, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অনধিকার হস্তক্ষেপ, কোচিং বাণিজ্য... নানান রকম ইন্ধন! তারপরও যারা মাটি-কামড়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে, স্কুলে যাবে, কলেজে যাবে, তাদের কীভাবে ঠেকানো যায়? পেটাতে হবে। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের, তারপর তাদের শিক্ষকদের। এর পরিণতি হিসেবে, শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক নিম্নগতির ফলাফল আমাদের দেশে অতি-উৎকটরূপে দৃশ্যমান। আমরা হয় কোনো কিছু বিশ্বাস করি না, নয়তো সবকিছু বিশ্বাস করি; কারণ আমরা কোনো কিছুই তলিয়ে দেখি না। যেকোনো বিষয়কে বিশ্বাস করার জন্য যেমন, অবিশ্বাস করার জন্যও ন্যূনতম যতটুকু বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার, আমরা সেটুকু করি না। কারণ সেই পদ্ধতিটাই আমরা জানি না। আমাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় এমন কোনো বিষয় ছিল না, কিংবা থেকে থাকলেও আমরা সযত্নে তা এড়িয়ে গেছি। কারণ উচ্চ-নম্বর বা গ্রেড পাওয়ার পথে এই বিষয়টার সম্ভবত কোনো ভূমিকা ছিল না। আমরা ততটুকুই পড়েছি, যতটুকু নম্বর পাওয়ার জন্য আবশ্যক ছিল।
আমরা কারও প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ করি, অথবা প্রশংসা তারই করি, যার সঙ্গে সরাসরি আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। কারও প্রশংসা করার জন্য তাকে জানা প্রয়োজন, তার অবদানকে মূল্যায়ন করতে জানা দরকার। আমরা এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক যে, ঠিক পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের চিনি না, জানি না; গত শতাব্দীর কীর্তিমান ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানব কীভাবে? আমরা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান, শঙ্কিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রস্তুত, বিব্রত, লজ্জিত, হতাশ, ক্ষুব্ধ। যা হতে চেয়েছি, তা হতে পারিনি। যা হয়েছি, তা হতে চাইনি। কী হতে চেয়েছি, তা জানতাম না। অধিকাংশই লক্ষ্যহীনভাবে ‘যা হয় একটা কিছু’ হয়ে গেছি। অনিচ্ছায় অর্জিত অবস্থান আমাদের মনে ইতিবাচক কোনো অভিব্যক্তি আনে না– বিবেচ্য নয় যে, সে অবস্থান প্রত্যাশিত অবস্থানের চেয়ে শ্রেয়তর অথবা নয়। আসলে, শ্রেয়তর কি না তা জানার জন্য তো প্রত্যাশিত অবস্থানটি জানা প্রয়োজন। আমাদের এ জাতীয় কোনো প্রত্যাশা যেহেতু ছিলই না, তাই আমাদের অধিকাংশের ধারণাতেই নেই, আমাদের প্রত্যাশিত অবস্থানটি কেমন। আর এই অনিশ্চয়তা, অসন্তোষ, দ্বিধা ও হতাশা আমাদের মস্তিষ্কে যে ভয়ানক ক্ষতিকর অবস্থাটির সৃষ্টি করে, তার নাম হীনমন্যতা। আমরা অধিকাংশ অপরাধমূলক, অনৈতিক এবং অন্যায় কর্মকাণ্ড করে থাকি হীনমন্যতার বশবর্তী হয়ে। আমরা যেহেতু নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবগত নই, তাই এ সংক্রান্ত যে ধারণাটি আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে, সেটি সম্পর্কেও আমরা সন্দিহান। ফলে আমরা নিজের কাছে নিজে সম্মানিত কি না, তা নিয়েও সন্দিহান। এই দ্বন্দ্ব থেকেই সম্ভবত, আমরা প্রথম সুযোগেই আমাদের সামনে আসা যেকোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ঘটনাকে প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিই এবং তাকে অসম্মানিত করতে উঠেপড়ে লেগে যাই। ধরুন, আমি সন্দিহান যে, আমার নম্বর ৫০ নাকি ৬০ নাকি ৪০। তাহলে আমার প্রতিপক্ষের চেয়ে আমার এগিয়ে থাকার একটাই উপায়, যেকোনো মূল্যে তার নম্বর ৪০-এর চেয়ে কম বলে প্রমাণ করা। সম্ভবত এই প্রবণতা থেকেই, আমাদের চারপাশে ঘৃণার চর্চা মহামারী আকার ধারণ করেছে। শিক্ষার মান এতটাই কমে গেছে যে, আমরা ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করতে পারি না। আমরা শিখিইনি, এসব দ্বান্দ্বিক মতবাদের চর্চা। বিবেক নামক একটি ‘নিত্য-ইতিবাচক’ ধারণা আমাদের ভেতর থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। ফলে যা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটবার কথা, কদাচিৎ তা ঘটতে দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি, তাকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিই, অথচ সেই ব্যতিক্রমকেই আবার উদাহরণ হিসেবে সামনে রাখতে সচেষ্ট হই।... আমরা আসলে স্ব-চরিত্র সম্পর্কেই সামান্যতম সচেতন নই।
পড়াশোনার চর্চা এতটাই নিম্নগামী যে, আমরা জ্ঞান আহরণ, তথা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের জন্যও সঠিক উৎস সন্ধান করতে পারি না। যে তথ্য বইয়ে পাওয়া যাওয়ার কথা, সেই তথ্য আমরা বাজারে খুঁজি; যে তত্ত্ব গবেষণাগারে প্রমাণিত হওয়ার কথা, তা প্রমাণে তুমুল তর্ক জুড়ে দিই পথের মোড়ের আড্ডায়। যে বিদ্যা শ্রেণিকক্ষে অর্জিত হওয়ার কথা, তার চর্চা করি কান কথা, উড়ো কথা কিংবা গুজবের ডানায় হাওয়া লাগিয়ে। এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে চলেছি, যে শিক্ষা আমাদের না দেয় ফলতে, না দেয় ফল। উচ্চশিক্ষিত হয়েও আমাদের মানসিকতার সামান্যতম পরিবর্তন হয় না। আমরা পূর্বনির্ধারিত ধারণা, সংস্কার-কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ছাঁচে ঢালা চিন্তাধারার ঊর্ধে উঠতে পারি না। শিক্ষার লক্ষ্য যদি ব্যক্তির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন হয়ে থাকে, তাহলে এমন শিক্ষা পুরোপুরিই ব্যর্থ। কেননা এই শিক্ষা আমাদের মধ্যে নীতিগত, গুণগত, অবস্থানগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, বাহ্যিক, নিদেনপক্ষে বৃত্তিমূলক পরিবর্তনটুকুও ঘটাতে পারে না। অশিক্ষিত জনতা রাষ্ট্রের জন্য বোঝা, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হতে বঞ্চিত ছদ্মশিক্ষিত নাগরিক শুধু রাষ্ট্রই নয়, সমাজের প্রতিও অভিশাপ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বছরের পর বছর কিছু সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে একদল ছদ্মশিক্ষিত পণ্য উৎপাদন করে চলেছে। যারা নিজেরাও জানে না, তারা শিক্ষিত নয়, তারা আসলে নানাভাবে, নানা হাতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অতি সস্তা কাঁচামাল!
- ট্যাগ:
- মতামত
- ভোটের রাজনীতি