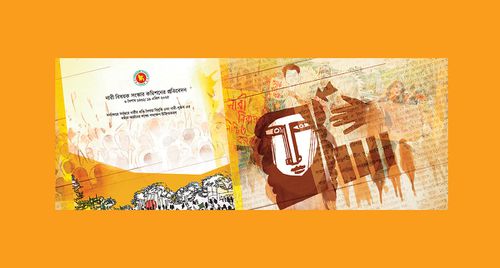
নারী কমিশনের সংস্কার-ভাবনা কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক
গত ৩ মে, শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চার দফা দাবিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চার দাবির একটি দাবি হচ্ছে নারী সংস্কার কমিশন বাতিল বিষয়ে। গত ১৯ এপ্রিল কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেশ করার পর থেকে আলোচনার চেয়ে সমালোচনা বেশি হচ্ছে প্রতিবেদনটি ঘিরে। কিন্তু সমালোচনাতেই শুধু তা থেমে থাকেনি বরং হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশে তারা চার দফা দাবিতে ২৩ মে দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচিরও ঘোষণা দিয়েছে। নারী সংস্কার কমিশন নিয়ে তাদের তীব্র সমালোচনা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা আলোচনার পাশাপাশি নারী কমিশনের প্রতিবেদনটি আসলে কেমন হয়েছে তা পর্যালোচনা করাও জরুরি।
২.
৩১৮ পৃষ্ঠা সংবলিত ৪৩৩টি সুপারিশের এই প্রতিবেদনটির ভূমিকায় কমিশনের সদস্যরা আশা করেছেন যে প্রতিবেদনটি জনমানসে নাড়া দেবে, মানুষকে ভাবাবে এবং তর্কবিতর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারীর সমতা অর্জনে সহায়ক হবে। তবে ১৭ অধ্যায়ের এই দীর্ঘ ও জটিল প্রতিবেদনটি এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের পড়ার মতো উপযোগী করে লেখা হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। তাই জনপরিসরে এটি নিয়ে ভাবার বা তর্ক করার সম্ভাবনা খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। খেয়াল করে দেখবেন, এখন পর্যন্ত এই প্রতিবেদন নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল (দু-একটি দলের বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়া ছাড়া), সুশীল সমাজ বা অন্য কোনো পক্ষ থেকে বিশদভাবে কোনো পর্যালোচনা আসেনি। প্রত্যাশিত ও নির্দিষ্ট কিছু পপুলিস্ট বিষয় নিয়েই সবাই বারংবার কথা বলে যাচ্ছে। ৩ মে হেফাজতের মহাসমাবেশেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।
প্রতিবেদনটির ১৫টি অধ্যায়ে বিভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিগত ও জনজীবন নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি অধ্যায়েই নারীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন বিষয় নিয়েও সুপারিশ করা হয়েছে, যা প্রতিবেদনটিকে জটিল করে তুলেছে।
যেমন সংবিধান সংশোধন বিষয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অনুচ্ছেদ ৯,১৫, ২৩ ক, কিংবা মৌলিক অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ ৩২,৩৫ (৫), ৩৯ (২) (খ) কোনোভাবেই নারীবিষয়ক কোনো অনুচ্ছেদ নয়, তবু এ বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সেগুলো ভালো সুপারিশ, কিন্তু এই প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলো অপ্রাসঙ্গিক এবং মূল বিষয় থেকে পাঠককে বারবার সরিয়ে নিয়ে গেছে প্রতিটি অধ্যায়েই। বিভিন্ন অধ্যায়ের সুপারিশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য; দ্বিতীয়ত, নির্বাচিত সরকারের পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন কাম্য; এবং তৃতীয়ত, দীর্ঘ মেয়াদে নারী আন্দোলনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা।

বাস্তবিক অর্থে আমরা যদি ধরে নিই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সর্বোচ্চ আর এক বছর ক্ষমতায় আছে, তবে তাদের পক্ষে এই প্রতিবেদনের বেশির ভাগ সুপারিশই নানা কারণে পূরণ করা সম্ভব নয়। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করা, হিন্দু ব্যক্তিগত আইন সংস্কার করা, বৈবাহিক ধর্ষণ কিংবা যৌন পেশাকে স্বীকৃতি দেওয়া—এই প্রতিটি সুপারিশই বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংবেদনশীল বিষয় যা পরিবর্তন বা পরিমার্জনের আগে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি আলোচনার দাবি রাখে। কমিশনের সদস্য নিয়োগ যদি লিঙ্গ ও দক্ষতার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতো, তাহলে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা বিচারে নানামুখী আলোচনার সুযোগ থাকত।
৩.
অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে এই কমিশনের পার্থক্য হলো, অন্য কমিশনগুলো মূলত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য গঠিত, কিন্তু এটিই একমাত্র কমিশন, যা ব্যক্তি বা মূলত নারীদের জীবন ও জীবিকাসংক্রান্ত নানা বিষয় উন্নয়নের জন্য গঠিত। আর তাই ‘সম-অধিকার’ নিয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়ন কখনোই পুরুষদের মতামত ও অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, আমরা আলাদা কোনো ‘নারী রাষ্ট্রে’ বসবাস করি না।
শুধু সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়, সংযুক্তিতে দেখা যায় যে বিভিন্ন পরামর্শ সভায়ও একই অবস্থা বিদ্যমান। যেমন সংযুক্তি ২-এ (পৃ.১৯২) বিশেষজ্ঞ ও পর্যালোচকদের তালিকায় ২০ জনের মধ্যে ২০ জনই নারী। কিংবা সংযুক্তি ৮.৬-এ (পৃ.২৬৫) এনজিও প্রতিনিধিদের পরামর্শ সভায় ১৮ জনের মধ্যে ১৫ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ অংশ নেন। সংযুক্তি ৮.১২-তে (পৃ.২৭৫) খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান ও আইন সমতাবিষয়ক সভায় ১৯ জনের মধ্যে ১৮ জন নারী ও ১ জন পুরুষ অংশ নেন।
এই পরিসংখ্যান উল্লেখের অর্থ এই নয় যে এসব বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা নারীরা করতে পারবেন না। বিষয়টি হলো এ ধরনের আলোচনায় বহুমাত্রিক বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তি ভীষণ জরুরি ছিল।


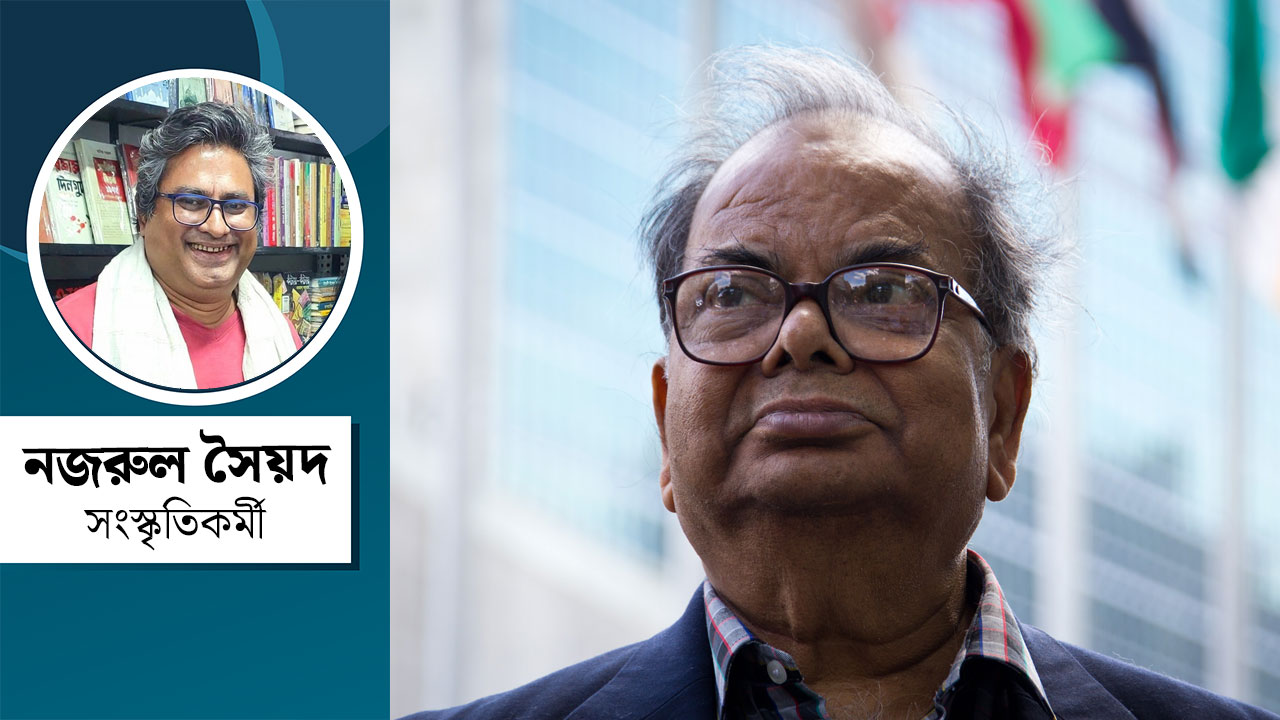
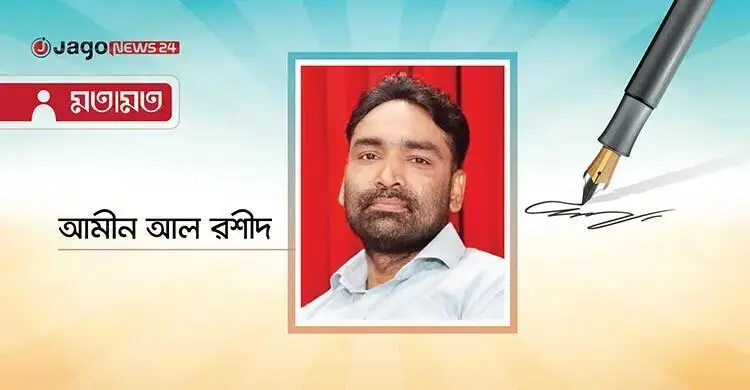

-699b8e6511dac.jpg)







