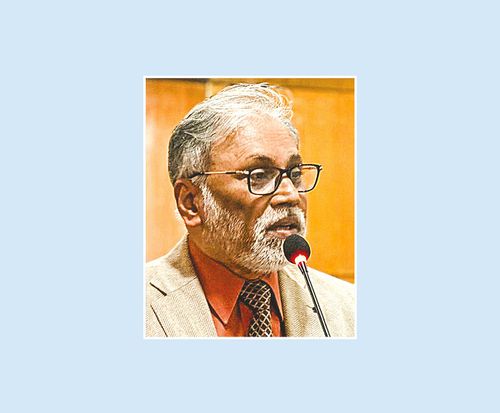
স্বাস্থ্যে সবকিছু ভেঙে সাজাতে পারলে ভালো হতো
দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা বা জঞ্জাল কী দেখলেন, কোথায় কোথায় দেখলেন?
মো. সায়েদুর রহমান: প্রথমে চোখে পড়েছে পরিকল্পনার অভাব। এই মন্ত্রণালয়ের কোনো কিছু অর্জনের লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য না থাকায় পরিকল্পনাও হয়ে ওঠেনি। অনেক কিছু হয়েছে দাতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নিয়ন্ত্রিত হয়ে। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি। অনিয়ম যা দেখছি তা নেতৃত্বের এই দুর্বলতার ফল। অনেক কিছু অপরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় বা ভুল নির্দেশনায় হয়েছে। জনবল সৃষ্টি, অবকাঠামো স্থাপন, যন্ত্রপাতি কেনাকাটা বা পদায়ন-পদোন্নতির সব ক্ষেত্রেই। আর আছে দলীয়করণ, রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার ফলে দুর্নীতি।
এ সময়ের মধ্যে কি দু-একটা জঞ্জাল সরানোর উদ্যোগ নিতে পেরেছেন? কোনো উদাহরণ আছে?
মো. সায়েদুর রহমান: রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না থাকা সত্ত্বেও যেসব বিষয় হাতে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সরানো হচ্ছে। পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপগুলোকে সংশোধন করা হচ্ছে। সব জেলার সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার পদে এমন হয়েছিল। এগুলো ঠিক করা হচ্ছে।
অন্যটি হচ্ছে, দাতা নির্ভরতার কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসা। এটা স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি বা হেলথ সেক্টর প্রোগ্রাম নামে পরিচিত। অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) ভিত্তিক কাজে ওভারল্যাপিং হয়েছিল, প্রশাসনের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল, দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছিল। কর্মসূচিটা বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা করেছি স্বাস্থ্যের পুরো স্টিয়ারিং থাকবে সরকারের হাতে।
স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে হাত দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন?
মো. সায়েদুর রহমান: স্বাস্থ্য খাতের খোলনলচে পাল্টানোর সুযোগ এসেছে। অল্প সময়ের জন্য দায়িত্বটা পেয়েছি। আমাদের রিপেয়ার ওয়ার্ক করতে হচ্ছে। খুব সন্তুষ্টির সঙ্গে কাজটা করছি বা করতে পারছি, তা–ও না। তারপরও চেষ্টা করছি কিছু দিক পরিবর্তন করার। আমরা মনে করছি পরবর্তী সময়ে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা এগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন।
রাষ্ট্রীয় একমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইডিসিএলের উৎপাদন সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ওষুধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি-দুর্বলতা কমিয়ে ক্রয় সক্ষমতা বাড়ানো হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। মূল লক্ষ্য ব্যক্তির নিজস্ব স্বাস্থ্যব্যয় কমানো, বিপর্যয়মূলক স্বাস্থ্যব্যয় থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া।
রেফারেল পদ্ধতি, জিপি মডেল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিষয়গুলো কী হতে যাচ্ছে?
মো. সায়েদুর রহমান: রেফারেল পদ্ধতিতে আছে, কিন্তু এটা কার্যকর হয়ে ওঠেনি, দৃশ্যমান নয়। ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। বলতে চাই যে ‘প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান’ এ শব্দটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। তাঁরা রোগীর সংস্পর্শে আসা প্রথম ব্যক্তি। গ্রাম ও শহরে নামের পার্থক্য হতে পারে। রোগী প্রথমে যাবেন ‘প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান’–এর কাছে। তাঁর সামর্থ্য ও দায়িত্বের বাইরে হলে তিনি রোগী স্থানান্তর করবেন। গ্রামাঞ্চলে যেসব স্থাপনায় চিকিৎসক থাকবেন, সেখান থেকেই রেফারেন্সটা শুরু হবে। শহরাঞ্চলে জিপি সেন্টারের কথা ভাবা হচ্ছে।
জিপি সেন্টার হতে পারে ওয়ার্ডভিত্তিক বা জনসংখ্যা অনুপাতে। রেফারেল কখনোই জরুরি রোগীর জন্য প্রযোজ্য নয়। গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ফিজিশিয়ানের সঙ্গে কমিউনিকেট করে উপজেলা হাসপাতালে আসতে হবে। শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিত্তিক যে জিপি সেন্টার, কন্ট্যাক্ট করে ওপরে উঠতে হবে। তার ওপরে থাকবে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি স্তরের চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান। পুরো বন্দোবস্তটা ডিজিটালাইজড হবে।
ডিজিটালাইজড হেলথ বা স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আপনার বিশেষ আগ্রহের জায়গা বা বিষয়। এখানে কী করতে যাচ্ছেন?
মো. সায়েদুর রহমান: অনেক সেবার ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, ভূমি, ব্যাংকিং বা টিকিট কাটা ইত্যাদি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জনবল ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, সেবার ক্ষেত্রে হয়নি।
কিন্তু স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটালাইজেশনের অর্থ, মানুষ অসুস্থ হলে বাসা থেকে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেন। যুক্ত হওয়ার পর তিনি যে সেবা গ্রহণ করবেন প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের কাছে, সেখান থেকে তাঁর একটি ইউনিক হেলথ আইডি তৈরি হবে। সেখান থেকে তিনি স্থানান্তর হতে পারেন। এই পুরো তথ্যগুলো ডিজিটালাইজড এনভায়রনমেন্টে সংরক্ষিত হবে। এই তথ্যগুলো শেয়ারেবল হওয়া।
এ বন্দোবস্তটা একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে নেওয়া দরকার। যেমন এনআইডি একটা এনভায়রনমেন্ট। একইভাবে ইউনিক হেলথ আইডির মাধ্যমে দেশের সব মানুষের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সব তথ্য, কোথায় সেবা নিয়েছেন, কার কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন, সব পরীক্ষার তথ্য সংরক্ষিত হবে। স্বাস্থ্যের ডিজিটালাইজেশন বলতে বোঝায় জন্মের আগে প্রসবপূর্ব সেবা থেকে শুরু করে মৃত্যু হওয়ার কারণ এবং দাফন হওয়ার সময়টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা–সম্পর্কিত তথ্য।
এখানে সেবাদাতাদের যাঁর যেটুকু প্রয়োজন, তিনি ততটুকুই অ্যাকসেস করতে পারবেন। গোপনীয়তা ও নৈতিকতার নীতিমালা মেনেই তথ্যগুলোকে জাতীয় তথ্যভান্ডারে আনা হবে।
এর সঙ্গে ডায়াগনস্টিক ও ফার্মেসি নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেটেড থাকবে। সরকারের এই ভান্ডারের সঙ্গে বেসরকারি স্বাস্থ্যকাঠামোগুলো যুক্ত হতে পারবে। এর ফলে তাদের প্রেসক্রিপশন অডিট করা সহজ হবে। প্রত্যেক চিকিৎসককে ব্যক্তিপর্যায়ে বা হাসপাতাল পর্যায়ে ফিডব্যাক দেওয়া যাবে যে কোন হাসপাতাল ভালো করছে, গাইডলাইন বা প্রটোকল মেনে কাজ করছে ইত্যাদি।
এটি হবে স্বাস্থ্যের তথ্যের ‘খনি’। এই ‘খনি’ গবেষণার প্রয়োজনীয়তাই কমিয়ে দেবে। আপনার হাতে থাকা তথ্য নিয়ে আপনি যেকোনো সময় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



