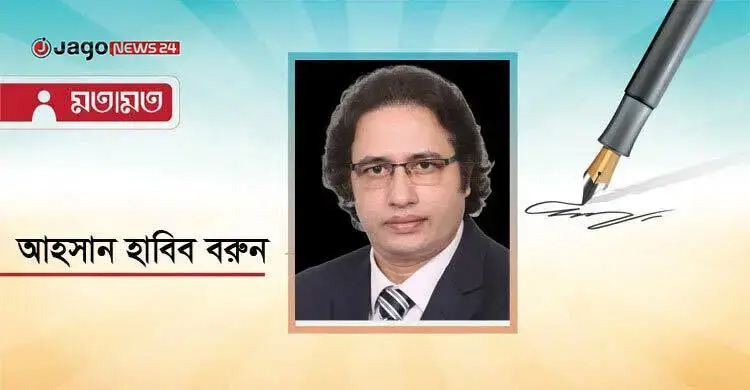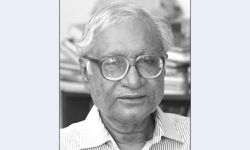সব বিদেশি বিনিয়োগকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না
অর্থনীতিবিদ সৈয়দ আখতার মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রভাষক ও যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিশ্বব্যাংকে প্রায় তিন দশক বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ ও বেসরকারি খাতের উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের ‘বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ’ বিষয়ক টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন তিনি। প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন সংস্কার, বিনিয়োগ ও শুল্কযুদ্ধ নিয়ে।
উত্তরাধিকারসূত্রে একটা ভেঙে পড়া অর্থনীতি পায় অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের সাড়ে আট মাসে অর্থনৈতিক খাতে সংস্কারের প্রশ্নটিকে কতটা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন? শ্বেতপত্র কমিটিই অভিযোগ করেছে, অর্থনৈতিক খাতের সংস্কারে সরকারের মনোযোগ কম।
সৈয়দ আখতার মাহমুদ: অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনাটা জরুরি ছিল। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেশ কিছু সময় ধরে ক্রমে কমে যাচ্ছিল। রিজার্ভ যাতে না কমে এবং আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে, সে ব্যবস্থা করার দরকার ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক সে ব্যবস্থাগুলো নিয়েছে। আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হারও নিয়ন্ত্রণে আনার দরকার ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির মাধ্যমে, বিশেষ করে সুদের হার বাড়িয়ে সামগ্রিক চাহিদা কমিয়ে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টাও সরকার করেছে।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যায়, আরেকটু মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি যে সংস্কারগুলো করা দরকার ছিল, সেগুলোর প্রতি সরকারের মনোযোগ হয়তো একটু কম ছিল। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ভেতরে–ভেতরে কাজ হচ্ছে, যেটা আমরা বাইরে থেকে জানি না। কয়েক দিন আগে অর্থ উপদেষ্টা একটি সাক্ষাৎকারে এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে শ্বেতপত্র কমিটি যে অভিযোগটি করেছে, সেটি হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে সরকারের উচিত ভেতরে–ভেতরে যে কাজটি তারা করছে, সেটা সবাইকে জানানো।
আপনার কাছে কি মনে হয়, সংস্কারের ব্যাপারে সরকার তার মেয়াদ নিয়ে দ্বিধার মধ্যে আছে?
সৈয়দ আখতার মাহমুদ: সরকারের কেউ কেউ মনে করতে পারেন, আমাদের মেয়াদ এক বছর বা তার কমও হতে পারে, তাই সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া ঠিক হবে না, সংস্কারের কাজগুলো পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো হবে। এ রকম ধারণা করাটা ঠিক হবে না। তার কারণ হলো, বিশ্ব দ্রুত বদলাচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেক ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী ঘটনাও ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে শুল্কের ঘোষণা দিয়েছেন, চীন তার প্রতিশোধে পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে তো আগে থেকেই একটা অনিশ্চয়তা ছিল। প্রযুক্তির কারণেও বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এর ওপরে পাল্টাপাল্টি শুল্কের কারণে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হলো।
এই অনিশ্চয়তা কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুযোগ তৈরি করছে না?
সৈয়দ আখতার মাহমুদ: এসব অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের জন্য যে সুযোগ আসছে না, সেটা নয়। শুল্কযুদ্ধের কারণে চীন থেকে হয়তো বিনিয়োগ অন্যান্য অনেক দেশে যাবে। সেটা আমাদের দেশেও আসতে পারে। সে কারণে সংস্কারের একটা জরুরি প্রয়োজনীয়তাও আছে। আমাদের যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়, আর ঝুঁকি যদি সামাল দিতে হয়—দুই ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক নীতিমালা ও বিধিবিধানে অনেক সংস্কার দরকার। আমরা সেটা আরও ৯ মাস বা এক বছর পিছিয়ে দিতে পারব না। এ ছাড়া ২০২৬ সালে আমরা এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাব। সুতরাং, সংস্কারগুলোর সব কটি না হলেও অনেকগুলো এখনই শুরু করা দরকার।

একটা বিষয় হলো, কোনো সংস্কারই রাতারাতি করে ফেলা যায় না। কোনো একটা সংস্কার প্রস্তাব সরকারের মধ্যে প্রথমে অলোচিত হয়। একসময় সেটা সরকারের আনুষ্ঠানিক এজেন্ডায় স্থান পায়। তখন সরকার একটি কমিটি করে, অন্যান্য প্রক্রিয়া শুরু করে। তখন সংস্কার কাজটি কারা করবে, কী ধরনের রিসোর্স দরকার হবে—এর সবকিছুই ঠিক হয়। বিশ্বব্যাংকের এক কর্মকর্তা হিসেবে বিদেশেও অনেক সংস্কারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি জড়িত থেকেছি। অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, প্রথম ধাপের কাজটি মানে সংস্কার প্রস্তাব সরকারের আনুষ্ঠানিক এজেন্ডায় পরিণত করাটাই এবং কে কোন দায়িত্বে থাকবে, সেটা ঠিক করাটাই সংস্কারের ৫০ শতাংশ কাজ।
আমি মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক সরকারের টানাপোড়েন থেকে অনেকটাই মুক্ত। সে কারণে সংস্কারের প্রাথমিক ধাপের কাজগুলো তাদের শুরু করা প্রয়োজন।
এ মাসেই ঢাকায় একটি বিনিয়োগ সম্মেলন হয়ে গেল। বিনিয়োগ সম্মেলন ঘিরে একটা বড় প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সামগ্রিকভাবে আপনি কীভাবে এ সম্মেলনকে মূল্যায়ন করবেন?
সৈয়দ আখতার মাহমুদ: বিনিয়োগ সম্মেলন আমরা আগেও অনেক দেখেছি। আমাদের দেশেও হয়েছে, বাইরেও অনেক রোড শো করা হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রচুর সময় ব্যয় করে, প্রচুর টাকা ব্যয় করে এমন সম্মেলন হয়েছে। সেখানেও কিন্তু প্রত্যাশা তৈরি হতো। বলা হতো যে অনেক বিনিয়োগকারী আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, বিনিয়োগ সেভাবে আসেনি। এবার ঢাকায় বিনিয়োগ সম্মেলনটি একটু অন্যভাবে করা হয়েছে। যারা সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, তাদের শুধু ঢাকায় নয়, ইপিজেড ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এ ধরনের সম্মেলনের একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। বিনিয়োগকারীরা, বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয়। এটা হুট করে হয় না। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রথমে একটা লম্বা তালিকা করেন, সেখানে ১০-১৫টা দেশ থাকে। এরপর তারা সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে ৪-৫টি দেশের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে। সবশেষে তাঁরা একটি বা দুটি দেশে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।
বাংলাদেশের সমস্যাটা ছিল, আমরা অনেক সময় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘ তালিকাতেও জায়গা পেতাম না। এ বাস্তবতায় এ ধরনের বিনিয়োগ সম্মেলনের উপকারিতা হচ্ছে অনেক বিনিয়োগকারীর লম্বা তালিকায় আমরা হয়তো স্থান পাব। আবার যেসব বিনিয়োগকারীর লম্বা তালিকায় আমরা আগে থেকেই স্থান পেয়েছিলাম, এবার তারা সম্মেলনে আসায় তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেও আমরা স্থান করে নিতে পারি।
কিন্তু একটা বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নেওয়া আর প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ করা—এর মধ্যে অনেকগুলো ধাপ আছে। যে দেশগুলো খুব সফলভাবে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, তারা কিন্তু সব সময় ট্র্যাকিং করে। আজকে আমাদের সম্মেলনে কারা কারা এলেন, এরপর তাঁরা কী করলেন, কোথায় তাঁরা ঠেকে গেলেন—এগুলো তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন। বিনিয়োগকারীরা কোথাও আটকে গেলে সেই বাধা দূর করার ব্যবস্থা তাঁরা করেন। আমাদের দেশে এ ধরনের ট্র্যাকিং করার ব্যবস্থা খুব একটা নেই। সাধারণত বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ থাকে। কারণ, সেসব আয়োজন নিয়ে পাবলিসিটি হয়, সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। কিন্তু যে প্রক্রিয়াগুলো আসলে কাজে দেবে, সেগুলো নীরবে হয়, তাতে আমাদের আগ্রহ কম থাকে।
একটা বিনিয়োগ সম্মেলন হয়েছে, প্রত্যাশাও তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিনিয়োগকারী যাঁরা আসবেন, তাঁদের সামনে যত বাধা আছে, সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কী করছি, সেটাই আসল কথা।