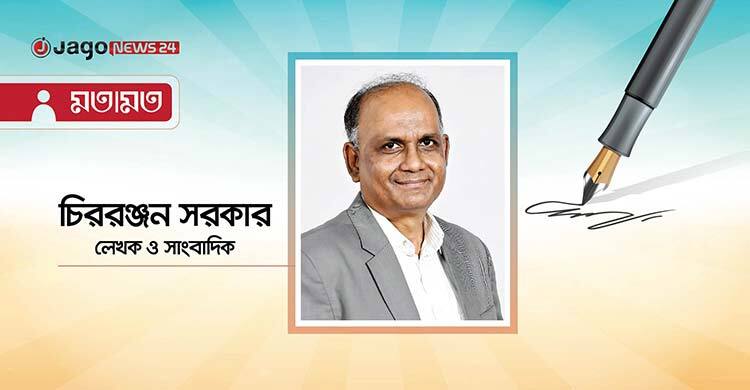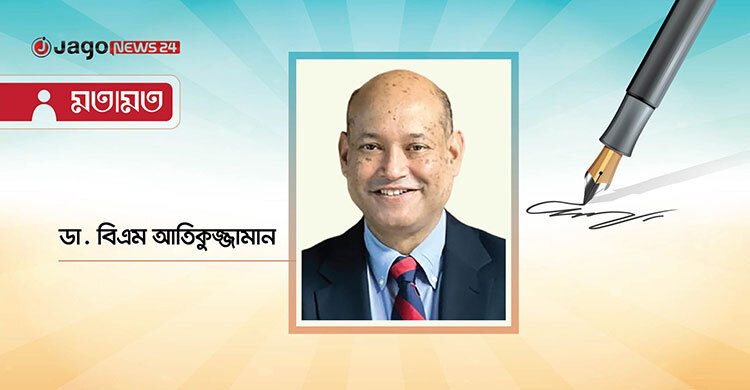রাজনৈতিক দল করে অভ্যুত্থানের তরুণেরা কি ব্যর্থ হতে চলেছেন
বাংলাদেশের গ্রাম-শহরজুড়ে গত আট মাস রাজনৈতিক মনোযোগের প্রধান বিষয় হয়েছিলেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সামনের সারির সংগঠকেরা। ‘৩৬ জুলাই’ একটা অধ্যায়ের সমাপ্তির পর মানুষ দেখতে চেয়েছিল, পরের অধ্যায়ে এই তরুণেরা কী করেন। সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলো পার হচ্ছে বাংলাদেশ।
প্রশ্ন উঠেছে, রাজনৈতিক দল গঠন করে অভ্যুত্থানকর্মী তরুণেরা ব্যর্থ হতে চলেছেন কি না? রাষ্ট্রের মৌলিক কোনো সংস্কার ছাড়াই যদি নির্বাচনী তোড়জোড় শুরু হয়, তাহলে অভ্যুত্থানের কর্মীদের জন্য করণীয় কী? কীভাবে তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন? কেবল অভ্যুত্থানকর্মী ওই তরুণদের জন্য নয়, জাতীয় স্বার্থেও এসব বিষয়ে পথ খোঁজার সময় এখন।
এনসিপির সামনে চ্যালেঞ্জ
প্রায় দুই মাস হলো ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি’র। এর আগে এই দলের সংগঠকদের বড় অংশ কাজ করছিলেন ‘জাতীয় নাগরিক কমিটি’ নামে। গত সেপ্টেম্বরে ওই কমিটি ঘোষিত হয়। জাতীয় নাগরিক কমিটির আদি কাফেলা ছিল ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’, যা গড়ে ওঠে কোটা আন্দোলনের ছাত্র-তরুণদের সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০২৪–এর লাল জুলাইয়ে।
পুরো হিসাব মিলিয়ে বলা যায়, আজকের জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির সংগঠকদের রাজনৈতিক পথচলার ৮-৯ মাস হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা সাংগঠনিক তিনটি কাঠামো পাল্টেছেন। এ রকম পরিবর্তনের আরও কিছু অধ্যায় বাকি আছে বলেও মনে হয়। এনসিপির অনেক কর্মী মনে করেন, তাঁদের নেতৃত্ব পর্যায়ে আরও পরিবর্তন ঘটবে সামনে। আরও কিছু ‘তারকামুখ’ যুক্ত হবেন তাতে। তবে সাংগঠনিক এসব পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে জনগণের কৌতূহল এবং ভাষ্যকারদের মনোযোগ মূলত দলটির রাজনৈতিক পদক্ষেপের দিকে।

দল হিসেবে আবির্ভাবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর এখনো ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করতে পারেনি বা করেনি এনসিপি, কেবল ৬৯৭ শব্দের একটা ‘ঘোষণা’ ছাড়া। যেখানে বাংলাদেশে ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এনসিপি ২৮ ফেব্রুয়ারিতে সেকেন্ড রিপাবলিক-এর যেসব লক্ষ্য ঘোষণা করেছে, অন্যান্য বড় দল, যারা নিজেরাও অভ্যুত্থানে শরিক ছিল, তাদের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন মিলছে না। এ রকম অবস্থায় এনসিপি এককভাবে তাদের লক্ষ্য ও ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানকালে চাওয়া কীভাবে অর্জন করতে সক্ষম? তাদের বর্তমান সাংগঠনিক ও সামাজিক কৌশলে আদৌ সেটা বাস্তবসম্মত?
রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে বাংলাদেশে এখন যে ধরনের গভীর টানাপোড়েন চলছে, তাতে এনসিপির ছাত্র-তরুণেরা দেখছেন, সংস্কার প্রশ্নে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোকে তাঁদের মিত্র হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার সমাজ-রাজনীতি-প্রশাসনের প্রচলিত কাঠামো বদলের জন্য চাপ তৈরির জোরও কমছে তাঁদের। পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো পরিস্থিতিকে যেকোনো উপায়ে নির্বাচনমুখী করে ফেলতে আগ্রহী। এ রকম অবস্থায় অভ্যুত্থানকারী কর্মী দলের হতবিহ্বলতা তাদের নেতাদের জটিল এক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। দেশজুড়ে তাই কৌতূহল, কী করবে এখন এই দল।
এনসিপির সংকট যে কারণে ‘জাতীয় সংকট’ও বটে
এনসিপির সংগঠকেরা এখন যে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জে পড়েছেন, এটা তাঁদের একার অভ্যন্তরীণ সমস্যা হলে এ নিয়ে অন্যদের ভাবনার প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের এই কোণঠাসা অবস্থার একটা জাতীয় চরিত্র আছে। জাতীয় তাৎপর্যও আছে। চলমান রাজনৈতিক মেরুকরণে সঠিক কৌশল গ্রহণে এনসিপির ব্যর্থতা একই সঙ্গে জাতীয় ব্যর্থতাও হয়ে দাঁড়াতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের পর সবচেয়ে মেধাবী তরুণেরাও একবার এ রকম অপচয়ের শিকার হন।
সংস্কার প্রশ্নে বর্তমান টানাপোড়েনে যদি পুরোনো-প্রথাগত-সংস্কারবিমুখ মনোভাব জয়ী হয় এবং তার মোকাবিলায় এনসিপি যদি অসফল হয়, তাহলে জাতির দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে নতুন পালকই কেবল যুক্ত হবে; যেমনটি ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের পর জাসদের ব্যর্থতায় এবং ১৯৯০-এর পর ‘তিন জোটের রূপরেখা’ বাস্তবায়নে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর সচেতন উদাসীনতায়।