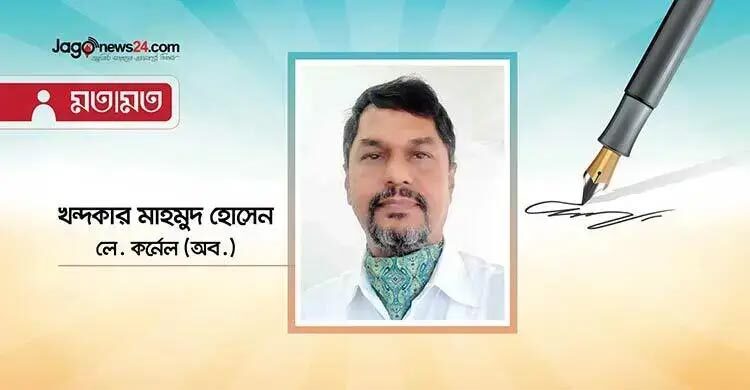-68080c23edf28.jpg)
আমাদের অর্থনীতি হতাশা পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে এবং আমরা আশাবাদী। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে সার্কুলার জারি করা হয়েছে সেটা খুবই আশাব্যঞ্জক। এ সার্কুলার জারির কারণে ভালো ব্যাংকগুলো, যাদের মন্দ ঋণ ২-৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে, তারা গ্রাহককে ভালো ডিভিডেন্ড দিতে পারবে। ইতোমধ্যে সেটা দেওয়া শুরুও করেছে অনেক ব্যাংক। আগে তো ৩০ শতাংশের বেশি কোনো ব্যাংকই ডিভিডেন্ড দিতে পারত না। এখন ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশও দিতে পারবে, যারা ভালো করছে ব্যাংক খাতে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই সার্কুলারের মাধ্যমে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাই আমি বলব, বাংলাদেশ ব্যাংক একটা সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে এখন থেকে ভালো ব্যাংকের ওপর মানুষের আস্থা আসবে। মানুষের আমানত বাড়বে। এখন দুর্বল ব্যাংকগুলো নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। আমি জানি না দুর্বল ব্যাংকগুলোকে নিয়ে কী ভাবছে সরকার। তবে বর্তমান সরকারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।
বিগত স্বৈরাচার সরকার অযোগ্য লোকদের হাতে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন কোম্পানিকে তুলে দিয়েছিল। প্রকৃত ও দক্ষ ব্যক্তি, যারা সৎভাবে ব্যাংক চালাতে পারবে, তারা কেউই কোনো ব্যাংকের লাইসেন্স পাননি। ফলে ওইসব অযোগ্য লোকের দ্বারা ব্যাংক কোম্পানিগুলোর বারোটা বেজেছে। আবার ওইসব অযাচিত লাইসেন্সধারীর মধ্য থেকে অনেকেই লাইসেন্স বিক্রি করে দিয়েছে। সোজা কথায়, লাইসেন্স বাণিজ্য হয়েছে আর কী! এমন ঘটনা বহু আছে। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এসব অনিয়ম অনেকটাই বন্ধ হয়েছে। ব্যাংক খাতে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে বলা যায়। অনেকে বলছেন এবং আমিও একমত যে, রেপো রেট গত সময়ে অনেক উচ্চ ছিল। রেপো রেটটি ১০ শতাংশের চেয়েও বেশি ছিল, যা আমরা ৩০-৪০ বছরেও দেখিনি। যেটাকে পলিসি রেট বলে। এই রেপো রেট কমানোর চেষ্টা করা হয়েছিল সুদের হার বাড়িয়ে। কারণ সুদের হার বাড়ালে ইনফ্লেশন ডিমান্ড কমে এবং কনজাম্পশন কমলে ইনফ্লেশন কমে। এটা একটা অর্থনৈতিক লিটারেচার। অর্থনীতিশাস্ত্রে এটা লেখা আছে। এটা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সের একটি অংশ। তবে কথা হচ্ছে, অর্থনীতিশাস্ত্রের এ নীতি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব একটা কাজ করে না। তা-ই হয়েছে। এটা কাজ করেনি।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সমস্যা, সেটা হচ্ছে বিনিয়োগের গতি মন্থর হয়ে যাওয়া। ফলে অর্থনীতি একটু নিম্ন প্রবণতার দিকে চলে গেছে। অর্থনীতির সূচকগুলো যে পর্যায়ে থাকা উচিত ছিল, সেটা সেখানে নেই। বর্তমানে যারা নীতি নির্ধারণে আছে, যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, তাদেরই এটা জানার কথা। সুতরাং অবস্থা বুঝে তারা অবশ্যই একটা ব্যবস্থা নেবেন। আমার কাছে মনে হয়, ভবিষ্যতে সুদের হার কমবে। কেননা কিছুদিন আগে ট্রেজারি বন্ডে সুদের হার কম ছিল, সামনে হয়তো ওটা আরও কমবে, বাড়বে না।

যা হোক, দেশের অর্থনীতি যেহেতু একটা পর্যায়ে গেছে, তাই ঘুরে দাঁড়াতে আর বাধা নেই। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও একটু গ্যাপে ছিল, ‘কী হয় দেখি’র মধ্যেই আটকে ছিল। সেটা এখন আর নেই। আরেকটা আশাব্যঞ্জক দিক হচ্ছে, আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। কোনো কোনো বাজারে আমাদের রপ্তানি ৩০-৪০ শতাংশ, আবার কোথাও কোথাও ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নেও বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে। আমাদের রেমিট্যান্স ৩০ শতাংশ বেড়েছে। এটি মাসে ২ বিলিয়ন ডলার থেকে আড়াই বিলিয়ন ডলারে উঠে গেছে। গত ঈদে এটা কত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। প্রতি মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলার বাড়লে বছরে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। ৩০ বিলিয়ন না হলেও ২৮-২৯ বিলিয়ন ডলার তো হবেই। সুতরাং আমাদের রিজার্ভের টানাপোড়েন আর থাকবে না। কারণ আমাদের অর্থনীতির প্রাণশক্তিই হলো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি। আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছু মিলিয়ে আমি অর্থনীতিতে একটা প্রাণ দেখছি। কারণ অনিয়ম-লুণ্ঠন বন্ধ হয়েছে।
এবার শেয়ারবাজারের কথায় আসা যাক। বর্তমানে শেয়ারবাজারে ৪০০-৪৫০ কোটি টাকা টার্নওভার হচ্ছে, এটা প্রকৃত বিনিয়োগ। আগে যেটা হয়েছে, সেটার ৯৯ শতাংশই হতো জুয়া খেলা থেকে। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে, সেটা প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের দ্বারা হচ্ছে। বর্তমানে রেট অফ রিটার্ন বেশি। ডিভিডেন্ড ঋণের মুনাফার হার শেয়ারবাজারে কিছুটা বেড়ে গেছে। প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা এখন সেগুলো ক্রয় করছে। যেহেতু পুঁজিবাজারে এখনো একটা তারল্য সংকট রয়েছে, সেজন্য শেয়ারের দাম অনেকটা কমেছে। শেয়ারের দাম কমার কারণে অনেক প্রতিযোগী প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য শেয়ার ক্রয় করছে। বর্তমানে শেয়ার মার্কেটে ৫০০-৫৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৯০ শতাংশই হচ্ছে প্রকৃত বিনিয়োগ। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের আগে যেটা প্রায় ১১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, সেটার ৯০ শতাংশই হয়েছিল গ্যাম্বলিং করে। ফলে প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের একটা ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। যা হোক, আমরা ভালো আইপিওর জন্য সরকারকে বলেছি। সরকার জানে ভালো আইপিও এখন কীভাবে আনতে হবে। বর্তমান সরকারকে শেয়ারবাজারে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। ভালো প্রণোদনা দিয়ে হলেও বড় বড় কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।
কিছুদিন আগে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান বলেছেন, কিছু প্রণোদনা না দিলে বিদেশি কোম্পানি কেন আসবে। তার কথার সঙ্গে আমিও একমত। ট্যাক্স রিলেটেড কিছু প্রণোদনা থাকতেই পারে। যেসব ভালো কোম্পানি তালিকায় আসছে, সেগুলোর করপোরেট আয়কর ১০-৫০ শতাংশেরও কম ছিল। সেটা এখন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণফোন, বার্জার, তারপর এসেছে মেরিকো। মেরিকো ছিল সর্বশেষ তালিকাভুক্ত কোম্পানি। যখন রবি এসেছে, তখন করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স উঠে গেছে। সেটার জন্য তারা দরবারও করেছে-আমাদের পিসকালীন ইনসেন্টিভ দাও। তাই তারা পেয়েছে। আমার কাছে মনে হয়, এগুলো জেনুইন। কেন পিসকালীন ইনসেন্টিভ ছাড়া মেট লাইফ, নেসলে, স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড তালিকায় আসবে? মেট লাইফ, নেসলে, স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড মুম্বাই, করাচির শেয়ারবাজারে আছে, অথচ আমাদের দেশে নেই। কেন নেই? কারণ তারা সুবিধা পাচ্ছে না, তাই তারা আসছে না। স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ডের মতো কোম্পানিগুলোর সাবসিডিয়ারি হওয়া উচিত। এগুলো তো ব্রাঞ্চ কোম্পানি। তাই লোকাল সাবসিডিয়ারি হয়ে ওদেরকেও যদি বলা হয় যে, তোমরা তো অন্যখানে শেয়ারবাজারের তালিকায় আছো, এখানেও হও, অন্তত ১০ শতাংশ অফলোড করো-আশা করি তারা করবে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- শেয়ারবাজার
- বাংলাদেশের অর্থনীতি