
সংসদীয় গণতন্ত্র নাকি ‘মৌলিক গণতন্ত্রের’ অন্য রূপ
শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে আমার একটা লেখা প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয়। এরপর সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ইমরান সিদ্দিক তাঁর একটি লেখায় আমার সঙ্গে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁর এ লেখার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।
২.
ইমরান সিদ্দিক লিখেছেন, ‘...সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বরাবরই মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করে থাকেন।’ লক্ষণীয় হলো, রাষ্ট্রপতির মহা–হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বাছাই করার কোনো এখতিয়ার নেই। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিতে হয়। সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, ‘কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।’ অতএব বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় মহা–হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ দিতে পারেন না।
ইমরান সিদ্দিকের মতে, বাস্তবে এসব (রাষ্ট্রের উচ্চতর পদগুলোয়) নিয়োগপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে না। কিন্তু সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে মহা–হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জন্য তাঁকে কারও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে না। তিনি তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় এ নিয়োগ দিতে পারবেন।
কমিশনের এ সুপারিশের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো, এটা বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাধীন নিয়োগ প্রদানের এই ক্ষমতাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।
ইদানীং ভারতের বিরোধী দলগুলো বারবার নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোদি সরকার দেশটির সিএজি দপ্তরের একটি প্রতিবেদনকে ব্যবহার করে আম আদমি পার্টিকে বেকায়দায় ফেলেছিল—এমন অভিযোগ উঠেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সিএজি দপ্তরকে ব্যবহার করে যেভাবে একটি রাজ্য সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিও একই ধরনের কাজ করতে পারেন—এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।
একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সংবিধান সংস্কার কমিশন সব সাংবিধানিক পদের নিয়োগের ক্ষমতা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলকে (এনসিসি) দেওয়ার সুপারিশ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম সিএজি। সিএজি নিয়োগের ক্ষমতা কেন রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হলো, তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আমার মতে, সিএজি নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে এনসিসির ওপর ন্যস্ত করা প্রয়োজন। তা না হলে সিএজি দপ্তরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যে আশঙ্কা, সেটা রয়েই যাবে।
- সিএজি নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে এনসিসির ওপর ন্যস্ত করা প্রয়োজন। তা না হলে সিএজি দপ্তরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যে আশঙ্কা, সেটা রয়েই যাবে।
- মৌলিক গণতন্ত্রীরা যেভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও একইভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন।
৩.
ইমরান সিদ্দিক জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে সঠিক নয় বলে তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সাংবিধানিক কাউন্সিলের নয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজন সরকারি দলের, তিনজন বিরোধী দলের এবং তিনজন নিরপেক্ষ। আমি আমার লেখায় বলেছিলাম, কাউন্সিলের মোট সদস্যের পাঁচজন বিরোধীদলীয় এবং এর ফলে কাউন্সিলের কাজে একধরনের ভারসাম্যহীনতা দেখা যেতে পারে।
ইমরান সিদ্দিক সম্ভবত উচ্চকক্ষের স্পিকারকে সরকারি দলের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি যেটা হিসাবের মধ্যে নেননি, তা হলো, উচ্চকক্ষের স্পিকার ও নিম্নকক্ষের স্পিকারের নির্বাচন একইভাবে হবে না। নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারিত হবে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে। যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করবে, সেই দল থেকে প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকার নির্বাচিত হবেন।
অন্যদিকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চকক্ষের আসন বণ্টন হবে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে (পিআর পদ্ধতিতে)। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেসব দেশে উচ্চকক্ষ আছে, তার মধ্যে বেশির ভাগ দেশেই কোনো দল এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায় না। এর ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে পদগুলো (স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, হুইপ) ভাগাভাগির বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়।
- ট্যাগ:
- মতামত
- সংবিধান সংশোধন


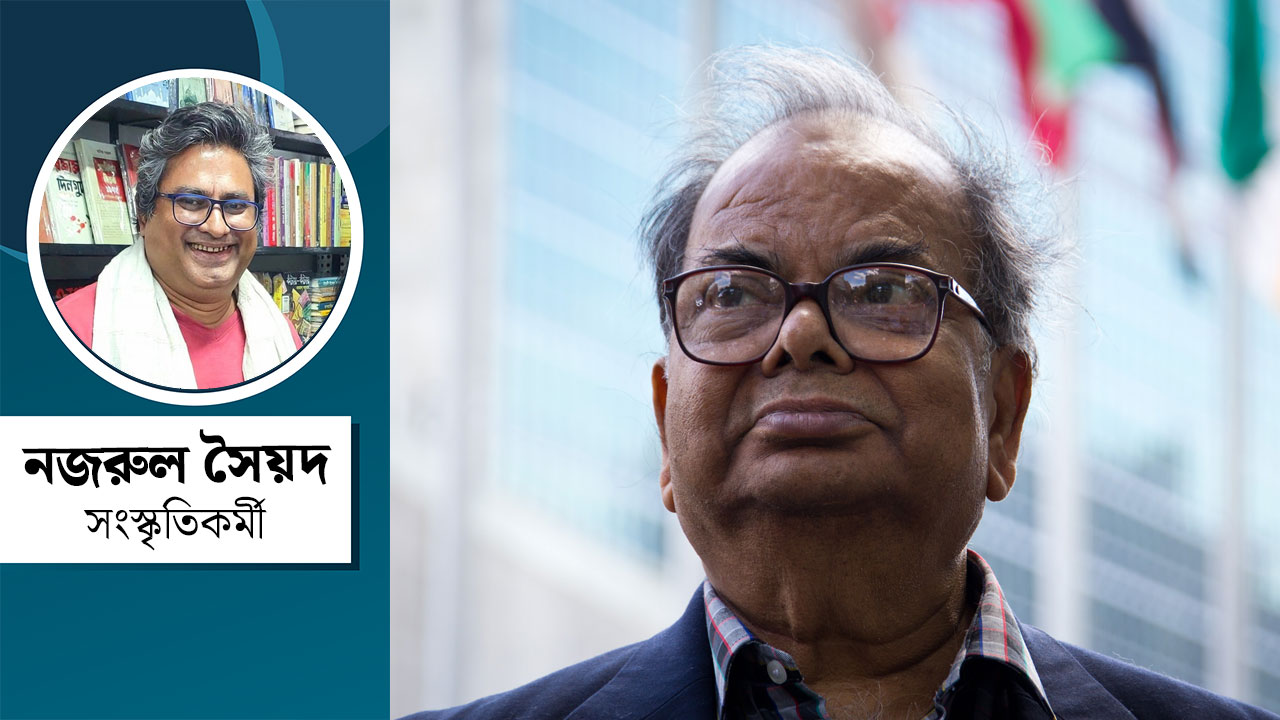
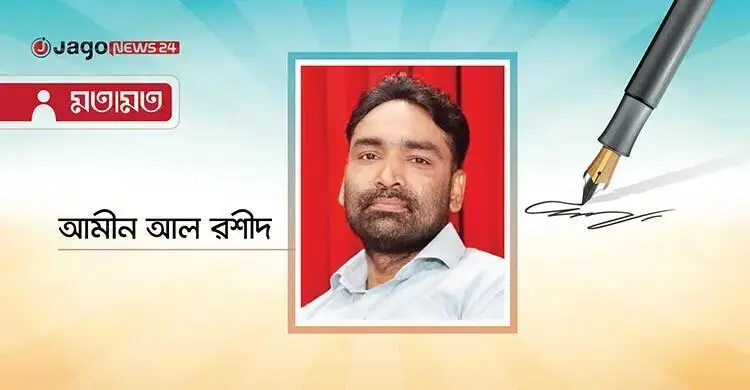

-699b8e6511dac.jpg)

