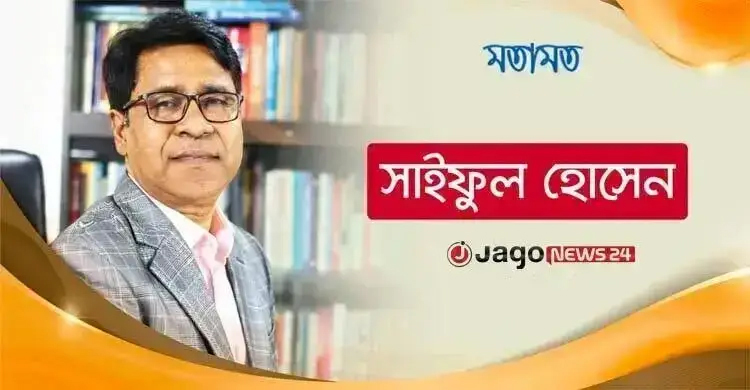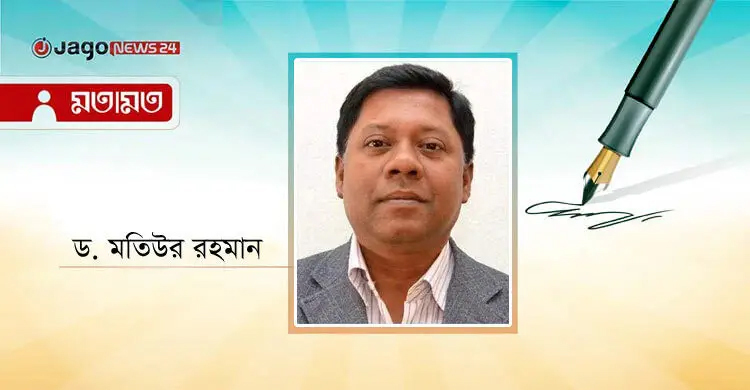নয়ন সমুখে তুমি নাই
আজ ৪ এপ্রিল দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সন্জীদা খাতুনের ৯৩তম জন্মদিন। মাত্র কয়েক দিন আগেই গত ২৫ মার্চ তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সন্জীদা খাতুন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার শামিল। তবে আজীবন দেশমাতৃকার মঙ্গল কামনায় ব্রতী এই মহীয়সী নারী সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়।
আপামর বাঙালির কাছেই তিনি বাঙালি সংস্কৃতির সেবক, ধারক, বাহক, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাতিঘর ও আপসহীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর আত্মজীবনী ‘জীবন বৃত্ত’ থেকে জানা যায়, আজীবন তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল শৈশবেই, পারিবারিকভাবেই। উপমহাদেশখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ, মুক্তচিন্তক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিখ্যাত দাবারু কাজী মোতাহের হোসেন ও মা সাজেদা খাতুনের ১১ সন্তানের মাঝে একটি একান্নবর্তী ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই তাঁর বেড়ে ওঠা। মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন রক্তের সম্পর্কহীন মানুষকে হৃদয়ে ও গৃহে স্থান দেওয়ার শিক্ষা। ছোটবেলায় বাবার নির্দিষ্ট আয়ের মাঝে ১১ ভাইবোনের মধ্যবিত্ত পরিবারেও গ্রামের আত্মীয়স্বজনের ভিড় লেগেই থাকত বাড়িতে। এই যে পরকে আপন করার শিক্ষা, সেটা বয়ে বেড়িয়েছেন সারা জীবন। কর্মজীবনেও প্রচুর মানুষের ঠাঁই হয়েছে তাঁর গৃহে। তাঁদের অধিকাংশই এখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বপরিমণ্ডলে। ‘জীবনবৃত্ত’-তে এক জায়গায় লিখেছেন—‘মায়ের সূত্রেই আজীবন এই শিক্ষা পেয়েছিলাম যে, রক্তের সম্পর্ক দিয়েই শুধু আত্মীয়তা হয় না মন-মানসিকতার মিল থাকলেই আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হওয়া সম্ভব।’
১৯৪৭ সালের দ্বিজাতিতত্ত্বের বিপরীতে ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল তার একদিকে যেমন ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন, তেমনি অপর দিকে ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আর সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন সন্জীদা খাতুন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদ্যাপন থেকে তাঁর পথচলা। তারপর ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর হাত ধরে ১৯৬৭ সালে রমনা বটমূলে বাঙালির নববর্ষকে শহুরে বাঙালির চিত্তে প্রোথিত করার যে প্রয়াস নিয়েছিলেন গুটিকয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে তিনি এবং ওয়াহিদুল হক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিল্পীদের নিয়ে কণ্ঠযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত পটপরিবর্তনের পর স্বাধীন দেশে যখন রবীন্দ্রচর্চা অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ হতে চলেছিল, আমাদের প্রাণের জাতীয় সংগীত প্রায় পরিবর্তন হতে চলছিল, তখনই সন্জীদা খাতুন ও তাঁর অনুগামীরা এর প্রতিবাদ করলেন এবং গঠন করলেন জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ। এর ৮০টি শাখা আজ দেশজুড়ে বিস্তৃত। এ ছাড়া নালন্দা বিদ্যালয়, অঙ্কুর ও ব্রতচারী আন্দোলনকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।
আজ বাঙালির এই ক্রান্তিকালে বাঙালি সংস্কৃতি যখন আবার রাহু-আক্রান্ত, তখনই আমাদের মতো লাখো বাঙালিকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন আমাদের সন্জীদা আপা, সকলের মিনু মাসি।
তাঁর প্রয়াণে তাই শুধু কান্না নয়, তিনি যা দেওয়ার তা দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন আমাদের চাওয়ার থেকেও অনেক বেশি। আমাদেরকে তা নেওয়ার যোগ্য হতে হবে।
আজীবন স্বদেশকে ভালোবাসার যে মন্ত্র গেয়ে গেছেন, তাঁর অনন্ত যাত্রায়ও সেটার প্রতিফলন ঘটল। নানাবিধ রাজনৈতিক টানাপোড়েনে হয়তো সেই কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ তিনি পেয়ে যাননি, যা আমরা মুক্তিবুদ্ধির লোকজন চেয়েছিলাম। কিন্তু এই যে নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানে হাজারো অনুরাগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রগানেই তাঁর অন্তিমযাত্রা, তা কয়জনের ভাগ্যে জোটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই সৌভাগ্য হয়নি। তিনি জীবিতকালে যা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পরও সেই বিশ্বাসে অটল থাকলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় নিজের নশ্বর দেহ দান করা এই সমাজে চাট্টিখানি কথা না। তিনি জীবিতকালে যেমন এই বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে লড়াই চালিয়ে গেছেন, তেমনি মৃত্যুর পরও সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে নাড়া দিয়ে গেলেন। এর মাধ্যমে তিনি এই সমাজের অচলায়তনে সজোরে ঘা দিয়ে গেলেন। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর গালে একটা চপেটাঘাত করে গেলেন। এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। শুধু বর্তমান বাংলাদেশেই নয়, অনেক উন্নত দেশেও সেটা অচিন্তনীয়। আমরা মুখে ও কাজে এক হতে পারি না, কিন্তু সন্জীদা খাতুন যেন তার ব্যতিক্রম। তিনি সযত্নে তাঁর আজীবন লালিত বিশ্বাসে অটুট ছিলেন। কোনো রক্তচক্ষু তাঁকে দমাতে পারেনি। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই যেন দেশের কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে ঘা দিয়ে গেছে। সেই মহীয়সী আজ চির বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং মুক্তবুদ্ধির মানুষের জন্য হয়ে রইলেন আলোকবর্তিকা। নিজ হাতে গড়া ছায়ানটে অগুনতি ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের অশ্রুসজল চোখে তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গানে গানে বিদায় যেন তাঁর পক্ষেই মানায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বাস করতেন ‘গানে গানে আজ বন্ধন যাক টুটে’-সেই গানে গানেই তাঁর বন্ধন মুক্ত হলো। তিনি পাড়ি জমালেন অমৃতলোকে সেই অনন্ত আকাশের পানে। মুক্তি নিলেন এই চিরচেনা নশ্বর পৃথিবী থেকে তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গানকে চিরসঙ্গী করে।
- ট্যাগ:
- মতামত
- জন্মদিন
- স্মরণ
- সনজীদা খাতুন