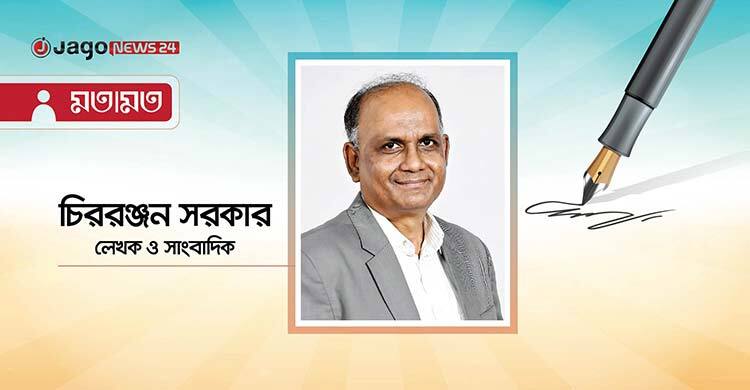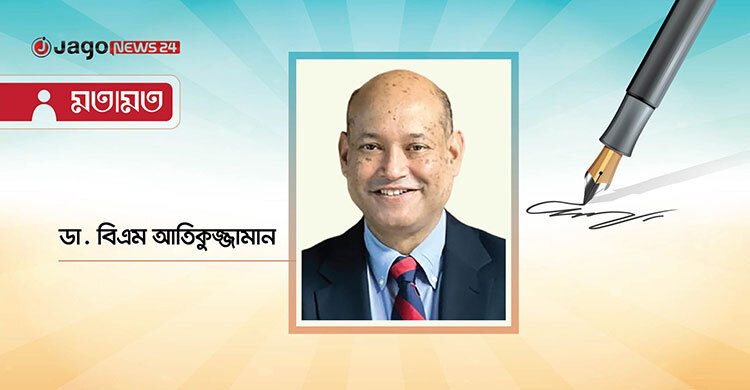গণ-অভ্যুত্থানের ছয় মাস পার হতে না হতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রদের পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ছড়াতে দেখা যাচ্ছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে মঙ্গলবার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই পক্ষের অন্তত শতাধিক জন গুরুতর আহত হন। ছাত্রদের সংঘাতে স্থানীয়রা ও রাজনৈতিক কর্মীরা জড়িয়ে পড়লে সেটা ভয়াবহ রূপ নেয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর ইটপাটকেল, লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করছে। যুবদলের কাউকে কাউকে রামদা-চাপাতির মতো ধারালো অস্ত্র নিয়েও হামলা করতে দেখা গেছে। এই সংঘর্ষ ও হামলা নিয়ে ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরস্পরকে দায়ী করেছে।
কুয়েটের এই সংঘর্ষের উত্তাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি মিছিল হয়। বুয়েটে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারেও একদল শিক্ষার্থী প্রতিবাদ মিছিল করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুয়েটে ছাত্ররাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ, হামলাকারীদের শাস্তি এবং উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের পদত্যাগের দাবি জানান। অন্যদিকে ছাত্রদলের দাবি, ‘বৈষম্যবিরোধী আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানার অপব্যবহার করে গুপ্ত সংগঠন শিবির “মব” তৈরি করছে।’

কুয়েটের ঘটনায় কোন পক্ষ দায়ী, তা নিয়ে ফেসবুকে পরস্পরবিরোধী ভাষ্য আসছে। কে প্রথম উসকানি দিয়েছে, তা নিয়েও পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। বুধবার ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কুয়েটে সব ধরনের রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট।
ছাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলো, যারা জান বাজি রেখে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অভূতপূর্ব এক ঐক্যের নজির স্থাপন করেছেন, তাঁরাই কেন এ রকম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন? তাঁদের মধ্যে কেন এমন অবিশ্বাস, চাপা অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হলো?
কুয়েটের ঘটনাকে রোগ নয়, রোগের লক্ষণ হিসেবেই দেখা দরকার। কেননা, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন সব ঘটনা ঘটেছে যেগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ কম।
দুই.
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়টির হল ও একাডেমিক ভবনগুলোর নাম পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দেওয়ার কারণ আমরা বুঝতে পারছি। এখানে ‘ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা’র বিষয়টি আছে; কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আলীম চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু থেকে শুরু করে নিতান্ত নিরীহ কবি জীবনানন্দ দাশের নাম পরিবর্তনের কারণ কী থাকতে পারে? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রল হয়েছে; প্রতিবাদ, সমালোচনাও হয়েছে।
বাংলাদেশের ইতিহাসে নাম পরিবর্তনের ব্যাপারটা রাজনৈতিকভাবে পপুলিস্ট বা জনতুষ্টিবাদী প্রকল্প। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও নাম পরিবর্তনের হিড়িক চলে। কেননা, এখানে মূলধারার রাজনীতি মূলত এক নেতার ভাবমূর্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে চলতি হাওয়াপন্থীরা খুব ভালোভাবেই জানেন, নামকরণের রাজনীতি তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিনিয়োগ।
- ট্যাগ:
- মতামত
- নাম পরিবর্তন
- অরাজনৈতিক দল