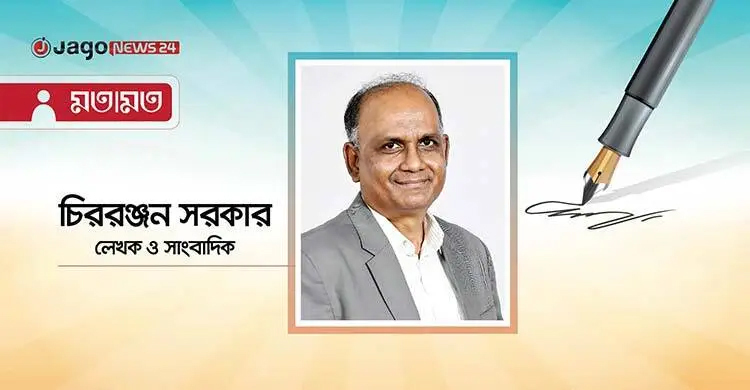মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়
প্রায় তিন বছর পার হতে চলল অথচ মূল্যস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা কমছে না। বস্তুত সব সরকারেরই প্রথম টার্গেট থাকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। কারণ এর ধকল সবচেয়ে বেশি বহন করে গরিব শ্রেণি। এই শ্রেণির নুন আনতে পান্তা ফুরায়—বাজারে ঊর্ধ্বমুখী দামে দুটিই বেহাত হতে বাধ্য।
আমাদের দেশে গরিব খানাগুলো মোট আয়ের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ঢালে ভোগ্য পণ্য ক্রয়ে—চাল কেড়ে নেয় ৪০ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি তাই অসহনীয়। মুখরা রমণীকে বশ করতে না পারলেও সংসার হয়তো কোনোভাবে টিকে থাকে, কিন্তু লাগামহীন মূল্যস্ফীতি বশে আনতে না পারলে সমাজের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে; এমনকি ঊর্ধ্বগামী মূল্যস্ফীতি রাজনৈতিক ডিনামাইটে রূপ নিতে পারে। একবার দিল্লির সরকার গদি হারিয়েছিল শুধু পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক চড়ে গিয়েছিল বলে।
দিল্লি দূর-অস্ত, বাংলাদেশে বিগত জুলাই-আগস্ট বিক্ষোভের আংশিক চালক ছিল কিন্তু মূল্যস্ফীতিজনিত জনরোষ, সে কথা যেন ঘুণাক্ষরেও ভুলে না যাই।
যা হোক, সরকার গেল সরকার এলো, কিন্তু মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী অনড় অবস্থান থেকেই গেল। ভুল বা শুদ্ধ, মানুষ মনে করে, অবস্থা অনেকটা যেই লাউ সেই কদু। আমরা অবশ্য তা মনে করি না।
কারণ সরকারের চেষ্টার কমতি নেই, যদিও যথেষ্ট নয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশের চলমান ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি কয়েক কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণা বলছে। নিম্ন আয়ের মানুষ প্রকৃত আয় পড়ে যাওয়ায় কম পুষ্টিকর খাবার কিনছে কিংবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বাদ দিচ্ছে। মোটকথা, মূল্যস্ফীতি মানবপুঁজি সৃষ্টিতে বাধা দিচ্ছে, দীর্ঘ মেয়াদে যার মাসুল গুনতে হবে জাতিকে।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে শুল্ককাঠামো যৌক্তিক করার সময় এসেছে এবং সেটি শুধু সমকক্ষদের সঙ্গে সমতুল্য করার জন্য নয়, বরং আমাদের রপ্তানিকে আরো প্রতিযোগিতামূলক করা।

সংরক্ষণে রপ্তানি-বৈরিতা পরিহার করার জন্যও তা দরকার। কারণ বৈরী শুল্ক কাঠামো দীর্ঘকাল ধরে আমাদের রপ্তানি বৈচিত্র্য করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। তবে শুল্কের হার কমানো বা যৌক্তিক করার ক্ষেত্রে একগুঁয়ে মনোভাবের পেছনে থাকা যুক্তি অজানা নয় : এক. রাজস্ব হারানো (আহরণের বিপরীতে) এবং দুই. তথাকথিত ‘শিশুশিল্প’ যুক্তি—এগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে বেড়ে ওঠার জন্য।
দুই.
স্মরণ করা যেতে পারে যে ২০২২ সালে একই সময়ে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয়—এক. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত সাপ্লাই চেইন, যার ফলে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্য, জ্বালানি ও সারের এবং দুই. মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার তির্যক অবমূল্যায়ন, যা ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩০ শতাংশের মতো। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কিছুটা হ্রাস পেলেও এই দুই উৎসর দ্বিতীয় পর্বের প্রভাব অনুভূত হতে থাকল। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে সরকার কর্তৃক জ্বালানির দাম ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করেও লাভ হলো না। মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের নিচে থাকলেও খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশের ওপর চড়তে লাগল।
এটি এখন পরিষ্কার যে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি প্রধানত ব্যয় বৃদ্ধিতাড়িত (cost-push) । বিপর্যস্ত সাপ্লাই চেইন এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন একটি সরবরাহ ধাক্কা নিয়ে আসে (supply shock), যা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয় এবং গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো অর্থ সম্প্রসারণ দ্বারা পুষ্ট হয়। অবশ্য দ্বিতীয়টি প্রচলিত পদ্ধতি/সুপারিশ; যথা—আর্থিক সংকোচন এবং সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ওল্টাতে প্রয়াস চালাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে জুলাই ২০২৩ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারি ঋণ (মূলত টাকা ছেপে নিরেট মূল্যস্ফীতিমুখী পদক্ষেপ) নেওয়ার তাগিদ স্থগিতকরণ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে একটি নিরপেক্ষ রাজস্বনীতি প্রত্যাশিত, যা রাজস্ব ঘাটতি মানিটাইজেশন সীমিত রাখবে।
বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন সংকোচন নীতি হয়তো চাহিদা সংকোচনে ভূমিকা রাখবে, কিন্তু আমদানির মূল্যবৃদ্ধি ও টাকার অবমূল্যায়ন সঞ্জাত সরবরাহ অভিঘাত মোকাবেলায় উপযুক্ত নয়। বস্তুত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত প্রকট আমদানি সংকোচনের ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে (স্বল্পতার সুযোগে) এবং এভাবেই সময়ের বিবর্তনে কস্ট-পুশ ইনফ্লেসনে অতিরিক্ত একটি উপাদান হিসেবে যোগ হয়। মূল্যস্ফীতির একটি বিশেষ চালকের দিকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে মনোযোগ দেওয়া জরুরি এবং সেটি হলো বিনিময় হারে ব্যাপক অবমূল্যায়ন।
- ট্যাগ:
- মতামত
- মূল্যস্ফীতি
- বাজার নিয়ন্ত্রণ