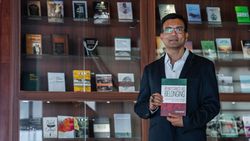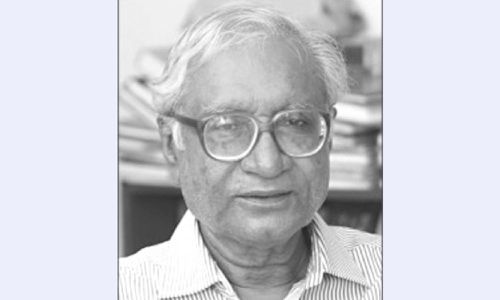
চেতনার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা
এই দেশ এখনো কতটা স্বাধীন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবশ্য অসংগত নয়। এবং অসঙ্গত যে নয়, তার অন্য সব প্রমাণের একটি হচ্ছে এই সত্য যে বাংলা ভাষা এখনো সর্বজনীন হয়নি। বাঙালির নববর্ষ এখনো সব বাঙালির নয়। কেবল বিত্তবানদেরই, গরিবদের নয়।
গরিব মানুষ চৈত্র-বৈশাখের আগমনে উত্ফুল্ল হয় না। সকালে নবজীবন দেখে না, প্রচণ্ড রোদের আশঙ্কা দেখে, চৈত্রদিনে তারা যে সর্বনাশটা দেখতে পায়, সেটা প্রিয়ার চোখে নয়, প্রকৃতির চোখে বটে। বড়লোকদের যে অংশ ক্ষমতাধর, তারা ইংরেজি নববর্ষই পালন করে। পহেলা বৈশাখ পালন করে না।
সেটাও এই কথাটাই বলে দিচ্ছে যে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অনেক অনেক দূরে, তারা পহেলা বৈশাখে নেই, থার্টিফার্স্ট যে কোথায় ঘটে, কোন আলোকিত অন্ধকারে সে খবর তো তারা রাখেই না। স্বাধীনতা পূর্ণ হয়নি, মুক্তি তো আরো পরের কথা। অর্থনীতি পঙ্গু ও আবদ্ধ, সংস্কৃতি আগ্রাসনকবলিত এবং সার্বিকভাবে ভবিষ্যৎ বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন; এই পরিবেশ বাঙালি সংস্কৃতির সাতসকালে কোন বাণী নিয়ে আসে কে জানে। বাণী অবশ্য আছে।
সেটা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা যে বাণী দেবেন সেটা নয়, গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমে যা নিয়ে হইচই করতে থাকবে তা-ও নয়, সেটা হচ্ছে এই যে তোমরা আত্মসমর্পণ কোরো না, তোমরা রুখে দাঁড়াও এবং ঐক্যবদ্ধ হও। ঐক্য ছাড়া শক্তি নেই, ব্যক্তিগত উদ্যম বা বিদ্রোহে কাজ হবে না, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা চাই।
এই কথাগুলো বাংলা ভাষার যারা চর্চা করছেন, তারাও বলে গেছেন বিভিন্নভাবে, সুরে ও কণ্ঠে। তাদের কথাই বলছি, যারা আমাদের গর্ব। তাদের কারণে আমাদের মাতৃভাষা আজ এতটা পর্যন্ত আসতে পেরেছে।
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, মীর মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, শরত্চন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ—এরা এক মাপের ছিলেন না, কিন্তু সবাই মনীষী ছিলেন এবং ছিলেন বাঙালিয়ানার পক্ষে। আধিপত্য মানেননি। অথচ লিখেছেন তারা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসারিত থাবার নিচে বসে।

আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের কথা বলি। গণতন্ত্রের একেবারে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিপেক্ষতার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, কিন্তু সেটা যে অর্জন করতে পেরেছি, তা বলতে পারব না। সাম্প্রদায়িকতা কমেছে, কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বরং বৃদ্ধি পেয়েছে, কমার কোনো লক্ষণ নেই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সর্বপ্রথম যে কথাটা বলে, সে কথা ধর্মনিরপেক্ষতার। ব্যক্তির জীবনে ধর্ম আছে, থাকুক, কিন্তু সমষ্টিগত পরিচয়টা ধর্মের ভিত্তিতে হবে না, হবে মাতৃভাষার ভিত্তিতে। কথা তো এটাই।
যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যুদ্ধ করলাম, সে রাষ্ট যে ধর্মনিরপেক্ষ হবে, এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। হানাদার পাকিস্তানিরা ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা একটি ধর্মযুদ্ধে নেমেছে; আমরা বলেছি, তারা নিয়োজিত হয়েছিল বাঙালি নিধনে, গণহত্যায়। আমাদের ওই বক্তব্য কোনো তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙালির ওই প্রতিরোধ শুরু বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। মনীষী বাঙালি লেখকদের যে বক্তব্য একুশে ফেব্রুয়ারি তাকেই আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে রাষ্ট্রে ও সমাজে। বড় লেখকরা বাঙালির হৃদয়ে যে সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন সেই সহমর্মিতাকেই আরো প্রসারিত করতে চেয়েছে, শ্রেণির বন্ধন ও বিভেদ ভেঙে দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল ওই আন্দোলনেরই যৌক্তিক পরিণতি।
কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা পেল না কেন? পেল না নেতৃত্বের কারণে। সাধারণ মানুষ ধর্মের কাছে যায় আশ্রয়, ন্যায়বিচার ও ভরসার প্রয়োজনে। রাষ্ট্র ও সমাজে এসবের কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। যে ব্যবস্থায় লোকে পুলিশকে দেখলে চোর-ডাকাতের চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়, আদালতের ওপর আস্থা যেখানে ন্যূনতম, সেখানে ঈশ্বর ছাড়া কে তাকে বাঁচাবে? কিন্তু তবু লোকে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে এক করে দেখে না। বাঙালি কৃষকের সকাল তাকে বলে ক্ষেতে যেতে হবে হালচাষের জন্য। অথবা যেতে হবে দিনমজুরির খোঁজে। যত্ন নিতে হবে গরুর, যদি গরু থেকে থাকে। মসজিদের ইমাম সাহেব ভালো লোক, কিন্তু তিনি যে থানার দারোগাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, এই খবর বাংলাদেশের কোন মানুষটি না জানে, শুনি? ১৯৪৬ সালে দেশের মানুষ ভোট দিয়েছে জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে মুক্তির আশায়। ১৯৭০ সালে ভোট দিয়েছে পাকিস্তানি শোষকদের চাপিয়ে দেওয়া জোয়ালটাকে কাঁধ থেকে নামাতে পারবে এই ভরসায়। উভয় ক্ষেত্রেই তার আচরণ বিশুদ্ধরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।
কিন্তু নেতৃত্বের আচরণ ভিন্ন রকমের। ১৯৪৬ সালে নেতৃত্ব ছিল মুসলিম লীগের হাতে। মুসলিম লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নয়, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম করেছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ যে গঠিত হয়, সেটা মুসলিম লীগের আদর্শকে পরিত্যাগ করে নয়, ওই আদর্শকে ধারণ করেই। মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র যে ইসলামভিত্তিক হবে, এটাও স্মরণ করিয়ে দিতেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আওয়ামী মুসলিম লীগের কারণে ঘটেনি, ঘটেছে ছাত্রদের কারণেই। আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে আরো পরে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়ের পথ ধরে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নেতৃত্ব ছিল পিছিয়ে, জনগণ ছিল এগিয়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নেতাদের বেশির ভাগই তো এসেছে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে। ওই রাজনীতির অভ্যাস ও ঐতিহ্য নেতারা যে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি, সেটা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তাদের বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তারা ধর্মকে ব্যক্তিগতকরণের পরিবর্তে বরং বুঝেছেন সব ধর্মের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মের আরো অধিক চর্চা। পঁচাত্তরের পর থেকে তো ধর্মনিরপেক্ষতা সাংবিধানিকভাবেই বাদ পড়ে গেছে। কাজটা বিএনপি করেছে এবং আওয়ামী লীগ মেনে নিয়েছে। পরবর্তী সময়ে উভয় দলই ভোটের জন্য ধর্মকে প্রতিযোগিতামূলকভাবেই ব্যবহার করেছে। কে কাকে দেখে?
- ট্যাগ:
- মতামত
- নেতৃত্ব
- ধর্ম নিরপেক্ষতা
- চেতনা