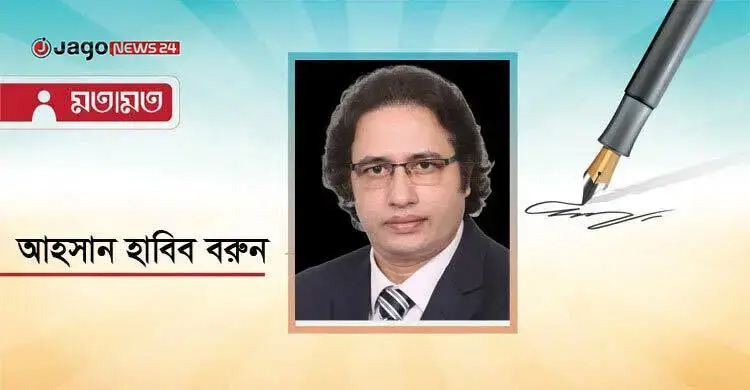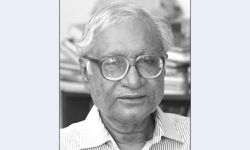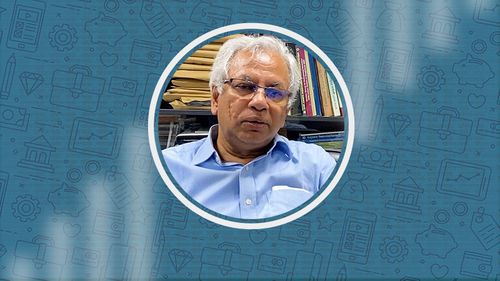
অস্থির চালের বাজার ও কারসাজির অর্থনীতি
চালের বাজার অস্থির। অস্থির বাজার শেষ পর্যন্ত কী পরিমাণ অস্বস্তির কারণ হতে পারে তা আশা করি সবাই জানে। নভেম্বরের পরও সরকারি গুদামে চালের স্থিতি বাড়ছে না। নভেম্বরেও দাম কমেনি। বিষয়টি চিন্তনীয়। এরই মধ্যে ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম বাজারমূল্যের অনিশ্চয়তা কী করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। কথা প্রসঙ্গে এসে গেল উৎপাদনের অনিশ্চয়তাও কি বাজারকে প্রভাবিত করে? বললাম অর্থনীতিতে যেকোনো অনিশ্চয়তা কী করে বাজারে প্রভাব ফেলে। তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করলাম—কী করে অনিশ্চয়তার ফলে উৎপাদনও হ্রাস পায়।
এদিকে সকালের পত্রিকায় দেখলাম, নভেম্বরেও খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কমেনি। নবান্নের মাস গেল। এখন নতুন চালের পিঠা উৎসবের সময়। অথচ বাজারে চালের দামই কমেনি। কী করে সম্ভব? প্রশ্নটি রেখেই ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলাম, অ্যাডাম স্মিথের দেয়া ‘বাজারের অদৃশ্য হাত’-এর অর্থ কী? ছাত্ররা ব্যাখ্যা দিল। কেউ বলল, এ হাতের মাধ্যমে বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। কেউ বলল, এর মাধ্যমে বাজারে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বিশ্ববরেণ্য চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করলে সেও জানাল যে অদৃশ্য হাতের মাধ্যমে বাজারে পাঁচটি কাজ সম্পন্ন হয়। এক. বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় থাকে, দুই. এর ফলে ব্যক্তির নিজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় ইত্যাদি। বুঝলাম চ্যাটজিপিটি এখনো ততটা জ্ঞানী হয়নি। বললাম, পণ্য বাজারে আসে অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে। প্রতিটি ধাপে মূল্য চাহিদা ও জোগান দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রতিটি বাজার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সম্পর্ককেই স্মিথ সাহেব বলেছেন অদৃশ্য হাত। অর্থাৎ এই যে নভেম্বরেও চালের দাম কমেনি। তার মানেই হলো এক বাজার অন্য বাজারকে বলে দিচ্ছে কী হতে যাচ্ছে। দাম কমছে না মানেই হলো পৃথিবীতে এবার ধানের ফলন ব্যাহত হয়েছে। তাই বাজারে দাম কমছে না। আগামীতে হয়তোবা দাম আরো বাড়বে—এ আশঙ্কায় দাম কমছে না।
বাড়ি এসে প্রথমেই ঢুকলাম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবপেজে। আমাদের দেশে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিদিন বাজারদর প্রকাশ করে। তাদের হিসাবমতে মাঝারি চালের বাজারদর আজ ৬ ডিসেম্বরে ৪৭ থেকে ৫২ টাকার মতো। এক মাস আগে একই দিনে তা ছিল ৬২ থেকে ৬৬ টাকার মতো। তারও এক মাস অর্থাৎ অক্টোবরে তা ছিল ৪৭-৫৩ টাকা। অর্থাৎ ডিসেম্বরে দাম কমেছে। কিন্তু বাজারদরের অন্যান্য সূত্র বলছে তা সঠিক নয়। চালের দাম কমেনি। আগোরায় দাম পরীক্ষা করে নিলাম। মিনিকেট চালের দাম ৯০ টাকা প্রতি কেজিতে। কিছু একটা গোলমেলে ঠেকছে। ভাবলাম সেপ্টেম্বরের দাম দেখে নিই। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাবে তা ছিল ৪৭-৫২ টাকা কেজি। কিছুটা আশ্চর্য হলাম। তবে কি ভুল দেখলাম। এমনিতেই আজকাল চোখে কম দেখছি! দেখলাম নাহ। চোখের ভুল নয়। বিপণন বিভাগ বাজারদর সিটি করপোরেশনের সব বাজারে টাঙ্গিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আপনারা কী ভাবছেন জানি না, তবে এ ৪৭-৫২ সংখ্যাটি সন্দেহের উদ্রেক করেছে। প্রসঙ্গটি আপাতত তুলে রাখি।

চাল এমন একটি পণ্য যা বছরে মাত্র দুইবার উৎপাদন হয়। তাই ভাবলাম মজুদদারি আইনে কী করলে মজুদদার হয় তার কি বিধান রয়েছে তা কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। ২০১৮ সালের কৃষি বিপণন আইনটি পাওয়া গেল। সেখানে লেখা রয়েছে—কোনো বিক্রেতা পণ্য ক্রয়ের রসিদ দেখাতে না পারলে ১ লাখ টাকা জরিমানা এবং এক বছরের কারাদণ্ডের বিধান আছে। দেখে কিছুটা আক্কেল গুড়ুম। আরো লেখা রয়েছে কোনো কৃষিপণ্য বাজারে বিক্রয় করতে হলে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায় ১ লাখ টাকা জরিমানা ও এক বছরের কারাবাস। কী আশ্চর্য! আমাদের মোহর আলী যখন তার ঘরের মুরগি বা তার ডিম বাজারে নিয়ে যাবে তখন কি মুরগির কাছ থেকে রসিদ নিয়ে যাবে? কৃষকের কি তার পণ্য বাজারে বিক্রির অধিকার নেই? আরো বলা আছে, পণ্যের মোড়কে পুষ্টিগুণ উল্লেখ করা না হলে ১ লাখ টাকা জরিমানা ও এক বছর কারাদণ্ড। কিন্তু মোহর আলীর পক্ষে কি তা সম্ভব? সে কি লেখাপড়া জানে? তার কি মোড়ক থাকে?
ভাগ্যক্রমে ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান আমলের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণে ১৯৮৭ সালের সংশোধনীটি পাওয়া গেল। যা দেখলাম তাতেও আক্কেল গুড়ুম। আইন অনুযায়ী একজন পাইকারি বিক্রেতার পাঁচ হাজার মণের অধিক এবং খুচরা বিক্রেতার ২৫০ মণের অধিক খাদ্য সংরক্ষণের অধিকার নেই। এ হিসাবে দেশে প্রতি মৌসুমে এক লাখ চালের মজুদদার প্রয়োজন অর্থাৎ প্রতি জেলায় ১ হাজার ৫০০ লাইসেন্সধারী চালের পাইকারি ব্যবসায় থাকতে হবে। সেই সঙ্গে আইন অনুযায়ী তারা ২০ দিনের বেশি কোনো মজুদ ধরে রাখতে পারবেন না এবং একই জায়গায় ‘সাতদিনের বেশি মজুদ রাখতে পারবেন না’। আরো উল্লেখ আছে, কোনো আমদানিকারক ৩০ দিনের বেশি পণ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন না। ২০১১ সালের একটি সংশোধনীও দেখলাম। আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে চালের মজুদ ৩০ দিন থেকে ১০০ দিন করা হয়েছে। কল্পলোকের গল্প মনে হলো সবকিছুই। নভেম্বরের পর বোরো ধান কাটা হবে মে মাসে। অর্থাৎ ১৮০ দিন পর। অথচ মজুদ রাখা যাবে মাত্র ৩০ দিন। তাহলে তো প্রায় ছয়বার এই ধান বিক্রি করতে হবে। একবার কিনবে একবার বিক্রি করবে। প্রতিবারে দাম কেবল বাড়বেই। তা না হলে রয়েছেন সেই বিখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট! তিনি ক্যামেরা নিয়ে আসবেন আর হাঁকবেন রসিদ কই? রসিদ দেখান। নচেত জরিমানা। ভাবলাম আমাদের কৃষক মোহর আলীর কী হবে? সে কি তার মুরগির কাছ থেকে রসিদ নিয়ে বাজারে আসবে!
আমাকে বলুন নভেম্বরে যদি আপনি ধান কেনেন তবে তা রাখতে হবে সর্বোচ্চ ১৮০ দিন নচেত বাজারে চাল থাকবে না। কিন্তু আইন বলছে রাখবেন ৩০ দিন। ব্যত্যয় হলে ১ লাখ টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ড! এখন কী করবেন? আপনাকে আপনার চাল আপনার বন্ধুর কাছে বিক্রয় করতে হবে ৩০ দিনের মাথায়। বাজারে তখন নতুন ধান পাবেন না। পরবর্তী ফসল হবে মে মাসে। তাহলে? এবার আপনার বন্ধুর ধান আপনি কিনবেন। কারণ তারও ৩০ দিন হয়ে গেছে। হবে অদলবদল। ধানের গোলা পরিবর্তন করতে লাগবে ট্রাক। লাগবে লোকবল। বাড়বে খরচ। দাম আরো বাড়বে। এভাবে হবে আরো চারবার। কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এ আইন তৈরি হলো। সরকারি কর্মচারীর ঘুসের বহর বাড়ানো আর চালের দাম বাড়ানোর মহাপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। শুধু সরকারি কর্মচারী নয়, রাজনীতিবিদরাও ভাগ পাবেন। যেখানে এক ফসল থেকে আরেক ফসলের মৌসুমের ব্যবধান ১৮০ দিনের, সেখানে মজুদ কীভাবে সর্বোচ্চ ৩০ দিন রাখা হয়? বোধগম্য হলো না। আমদানিকারকের ক্ষেত্রেও একই জাতীয় নিয়ম রয়েছে। ভাবলাম আমদানির বাজার দেখে আসি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- কারসাজি
- অস্থিরতা
- চালের বাজার