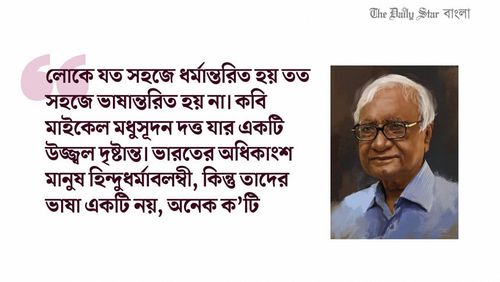
ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ অবাস্তব ও বিপজ্জনক
ব্রিটিশ-বিরোধী অনেক নিম্নবর্গীয় আন্দোলনেরই প্রকৃত গুরুত্ব এখনো অনুধাবন করা হয়নি। সে-ইতিহাস অলিখিতই রয়ে গেছে। যেমন গোড়ার দিকে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, পরে ১৯৪৫-৪৬-এর তেভাগা আন্দোলন এবং ১৯৪৫-৪৬ এ কলকাতায় শ্রমজীবী ও ছাত্রদের আন্দোলন- এদের ব্যর্থতার কারণ-অনুসন্ধান তাৎপর্যপূর্ণ সত্যের সন্ধান দিতে পারে। ১৯৪৭-৫১-র তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। সাতচল্লিশের পরে পূর্ববঙ্গের নাচোলে, সিলেটে, ময়মনসিংহে প্রান্তবর্তী মানুষদের যেসব অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলোও যথার্থ পর্যালোচনার অপেক্ষায় রয়েছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে গবেষণা অত্যাবশ্যক। এমনকি ১৯৪৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘটও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যা নিয়ে অনুসন্ধান চলতে পারে।
নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদের একটি বিশেষ গুণ সাহিত্যে তাদের আগ্রহ। ইতিহাস নিয়ে লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধকে তাঁরা সাহিত্যের আবেদনে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের রচনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য। সেটা যে কেবল গবেষণা-সমৃদ্ধ উন্মোচনের কারণে তা নয়; সঙ্গে রয়েছে উপস্থাপনার দক্ষতা। বাগ্বৈদগ্ধ্য এঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য; কৌতুকের প্রসন্ন একটি বোধ অনেক রচনাতেই পাওয়া যাবে। ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে এঁদের প্রায় সব রচনাই ইংরেজিতে লেখা, এবং এঁদের প্রত্যেকের ইংরেজি জ্ঞান ও ব্যবহারদক্ষতা ঈর্ষণীয়। ইতিহাস এঁদের কাছে বর্ণনার ব্যাপার নয়, অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা এবং সর্বোপরি পাঠের ব্যাপার। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, এঁরা তথ্য-প্রমাণ দলিল-দস্তাবেজ সব কিছু পাঠ করেন অনেকটা সাহিত্যসমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে। কথাটা সত্য। প্রকাশ্য অর্থের পেছনে লুকানো আছে যে গোপন অর্থ, কখনো হয়তো-বা উল্টো অর্থই, তা এঁরা খুঁজে বের করেন। এঁরা মহাফেজখানার সংরক্ষক নন, প্রাণবন্ত পাঠক। জ্যাক দেরিদা যেভাবে রচনাকে 'বিনির্মাণ' করেন এবং বোঝাতে চান যে ট্রেক্সটই সব, যা পড়তে পেয়েছি সেটাই যথেষ্ট, তার বাইরে যাবার কোনো আবশ্যকতা নেই, সেই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের নয়, তদুপরি বিনির্মাণবাদীদের মতো এঁরা রাজনীতিবিমুখ নন, বরঞ্চ রাজনৈতিক ইতিহাস রচনাই এঁদের লক্ষ্য।
কিন্তু এই ইতিহাসবিদদের অসুবিধার জায়গাও রয়ে গেছে- একটি নয়, বেশ কয়েকটি। এবং সেগুলো যে নেহায়েৎ নগণ্য তা নয়, বেশ বড় বড় বটে। প্রথম অসুবিধার জায়গা হচ্ছে যে এঁরা পুঁজিবাদের মহান বায়ানকে (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ) নাকচ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি বৃহৎ ও সর্বজনীন ধারণাকে তাঁদের ইতিহাসের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন। এই ধারণাটি হলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের। নিম্নবর্গ ইতিহাসচর্চার যে ঘোষণাপত্রের সারসংক্ষেপ আমরা উদ্ধৃত করেছি সেটি রচনার সময় রণজিৎ গুহের স্মরণে ছিল গ্রামসি লিখিত 'নোটস অন ইটালিয়ান হিস্ট্রি'র প্রস্তাবনার কথা, যা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। আমরা এও জানি যে, ইউরোপের যখন বেশ কয়েকটি দেশে জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ইতালির বুর্জোয়ারা যে তখন তেমন একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি সেই ব্যর্থতার বিষয়ে গ্রামসি সচেতন ছিলেন।
অনুরূপভাবে নিম্নবর্গ ইতিহাসপাঠের ঘোষণাপত্রে বলা হচ্ছে ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসপাঠের সমস্যার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুটি হচ্ছে এই সত্য যে, ভারতবর্ষের মানুষেরা ঔপনিবেশিকতাকে পরাভূত করে নিজেদেরকে একটি জাতিতে পরিণত হতে ব্যর্থ হয়েছে। এটিকে এঁরা বলছেন একটি ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। মনে করেছেন ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষে একটি জাতিতে পরিণত হওয়া আর ইতালিয়দের পক্ষে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করা তো এক ব্যাপার হতে পারে না। ভারত ছিল পরাধীন, আর ইতালি ছিল স্বাধীন; তাছাড়া যে ইউরোপীয় রেনেসাঁন্স স্বতন্ত্র জাতিগঠনের ধারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তার জন্মভূমিও ইতালিই বটে। সেখান থেকে ভারত অনেক দূরে। এই দুই পার্থক্য তো ছিলই। আরো পার্থক্য রয়েছে এইখানে যে, ভারতবর্ষ কেবল যে বৈচিত্র্যপূর্ণ তা নয়, সমসময়েই বহুত্ববাদী; এই উপমহাদেশ কখনো এক জাতির দেশ ছিল না, এবং এখনও যে সকল ভারতীয় এক জাতিতে পরিণত হয়েছে তা কিছুতেই বলা যাবে না।
প্রশ্ন দাঁড়ায় জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তিটা কি। ভাষা, নাকি ধর্ম? ধর্ম অবশ্যই একটি ভিত্তি, কিন্তু মূল ভিত্তি কোনটা? না, সেটা ধর্ম নয়, সেটা হলো ভাষা। একই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকতে পারে, থাকেও; ভাষার ঐক্য তাই ধর্মের ঐক্যকে ছাড়িয়ে যায়। তাছাড়া সত্য তো এটাও যে, লোকে যত সহজে ধর্মান্তরিত হয় তত সহজে ভাষান্তরিত হয় না। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতের অধিকাংশ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাদের ভাষা একটি নয়, অনেক ক'টি। এই যে বিভিন্ন ভাষা তাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাই বলে দিচ্ছে যে ভারত এক জাতির দেশ নয়। কখনো ছিল না, এখনও নয়। অশোক একটি সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। পরে মোগলরা আরেকটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল; তারা ফার্সি ভাষাকে রাজ-ভাষা করেছে, আন্তঃধর্ম বিবাহও চালু করেছিল, ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্য আনবার জন্য আকবর একটি নতুন ধর্ম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু এসব কাজ ভারতে একটি অভিন্ন জাতি গড়ে তুলতে পারেনি, ভারতীয়রা একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয়নি। তার প্রধান কারণ ভাষাগত বিভিন্নতা। চাপিয়ে-দেওয়া ভাষা স্থানীয় ভাষাগুলোকে স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে সমর্থ হয়নি।
- ট্যাগ:
- মতামত
- ধর্মীয় মৌলবাদ
- জাতীয়তাবাদ








