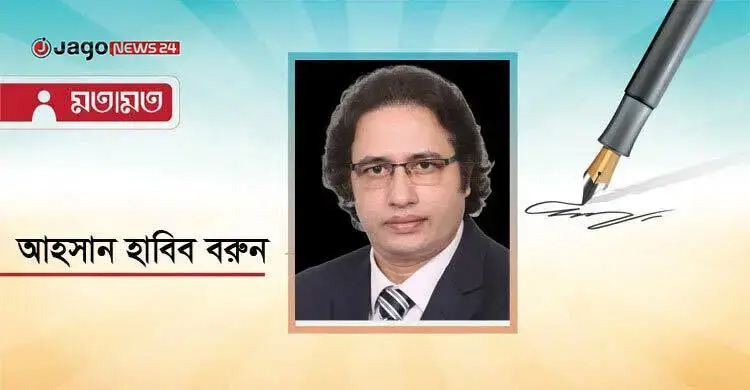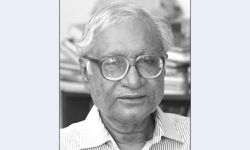দক্ষতা, মেধা ও প্রতিযোগিতার ওপর ‘বাজার অর্থনীতি’ দাঁড়াচ্ছে না
উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন কে না চায়, কিন্তু চাইলেই তো হবে না। উন্নয়নের কাজটা কে করবে? সাধারণ মানুষ, শ্রমিক শ্রেণী, কৃষককুল, উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরা? এ ব্যাপারে একেক দেশের অভিজ্ঞতা একেক রকমের। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, কল্যাণকামী অর্থনীতি ইত্যাদির কথা আমরা সবসময়ই শুনি, কিন্তু মূল প্রশ্ন কোন পথে হবে উন্নয়ন? এ পথ ও পন্থা নিয়ে পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) আলোচনা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ-পন্থা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা ছিল। আমার মনে আছে, ১৯৬৫-৬৬ সালের দিকে আমরা তখন বাণিজ্যের (কমার্স) ছাত্র তখন আমাদেরকে চারটি দেশের অর্থনীতির অভিজ্ঞতা পড়ানো হতো। স্যারদের জিজ্ঞেস করলে বলতেন, বাণিজ্যের ছেলেমেয়েদের অর্থনীতি পড়া দরকার। কারণ বাণিজ্য হচ্ছে ফলিত অর্থনীতি (অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিকস)। অর্থনীতি শুধু পড়লেই হবে না, তার নীতিমালা বাজারে কীভাবে কাজ করে তা জানা দরকার। ব্যবসা কীভাবে সংগঠিত করতে হয়, মালিকানা কীভাবে ব্যবসাকে প্রভাবিত করে, ব্যবসা ক্ষেত্রে আইন-কানুন কী কী আছে, হিসাবপত্র কীভাবে রাখতে হয়, কীভাবে নিরীক্ষণ চালাতে হয়, উৎপাদিত পণ্যের খরচ কত, পণ্য বাজারজাতকরণ কীভাবে হবে, পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ফাইন্যান্স কীভাবে জোগাড় হবে, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে, সবই জানতে হয়। শুধু চাহিদা ও সরবরাহ তত্ত্ব জানলে চলে না। স্যারেরা এসব বলতে বলতে চলে যেতেন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে। মনে আছে চারটি দেশের অর্থনীতি এবং তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের পড়ানো হতো। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপান। তখনকার দিনে ওই দেশ চারটিই ছিল সবচেয়ে উন্নত। ঢাকার বাজার ছিল জাপানি পণ্যে বোঝাই। ইলেকট্রনিকস, জামাকাপড় থেকে শুরু করে কিনা ছিল। আজকের ভারত ও চীন কোনো আলোচনাতেই ছিল না। ভারতকে বলা হতো হাতির মতো শ্লথ গতির দেশ, আর চীন হচ্ছে ড্রাগনের দেশ। উন্নত বা উন্নয়নের ছোঁয়া তখনো তাদের গায়ে লাগেনি। ইংল্যান্ড বা যুক্তরাজ্য উন্নত দেশগুলোর মধ্যে পুরনো। তাদের দেশের প্রাথমিক পুঁজি এসেছে ভূমি থেকে, আর এসেছে উপনিবেশ থেকে। লুণ্ঠন করা টাকা। বণিক নাবিকরা তাদের দেশে উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ইমিগ্র্যান্ট ইহুদি বণিকেরা। এদের ছিল ব্যবসায়িক বুদ্ধি, ছিল অফুরন্ত পুঁজি। আবার বহু প্রবাসী ইউরোপ থেকে যায়, উন্নয়নে গতি সঞ্চার করে তারা। রাশিয়া বা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার মাধ্যম ছিল পুঁজিবাদ। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের পথ ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ ধরে। সমাজতন্ত্রই তাদের পাথেয়।
ভারী শিল্পের পথ তাদের উন্নয়নের মাধ্যম। রাষ্ট্র পুঁজি, ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করে। তারা ‘ব্লেড’ তৈরি না করলেও চাঁদে যায় ঠিকই। জিনিসপত্রের মূল্য সরকার নির্ধারিত। শ্রমিকদের শাসন। তাদের একনায়কত্ব। ভিন্ন এই পথে তারাও শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। এদিকে পুবের দেশ হচ্ছে জাপান। সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করে তারা অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে। পুঁজি সরবরাহ এবং উদ্যোক্তা সরবরাহ ঘটে কিছুসংখ্যক পরিবার থেকে। টয়োটা, ইয়ামাহা ইত্যাদি তার উদাহরণ। জাপানে কেউ চাকরিতে ঢুকলে চাকরি আর যেত না।
লাইফ লং এমপ্লয়মেন্ট বা পশ্চিমা ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপান এখন ম্রিয়মাণ অর্থনীতির দেশ। এখন এগিয়ে যাচ্ছে উদীয়মান দেশের অর্থনীতিগুলো। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিশেষ করে চীন এবং এর পরই রয়েছে ভারতের নাম। চীন জাতি এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ, ভারত পঞ্চম। চীন বস্তুত একটা চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। তারা কম্যুনিস্ট শাসিত সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত। কিন্তু বাজার অর্থনীতি তাদের পাথেয়। ভারত, ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশেরও তা, আমাদেরও তা। চীন যে নীতি গ্রহণ করে আজকের এ সাফল্য এসেছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি কথা। কিছু লোককে ধনী হতে দাও, তারা ঝুঁকি কমাক। তারাই উন্নয়নের চাবিকাঠি হবে। ফলে দেখা যায় বর্তমান চীনে শতকোটি ডলারের মালিক অগনিত। বড় বড় ব্যবসায়ী হাউজের জন্ম হয়েছে। তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়াও তাই।
- ট্যাগ:
- মতামত
- প্রতিযোগিতা
- দক্ষতা
- পুঁজিবাদ
- পুঁজিবাদী