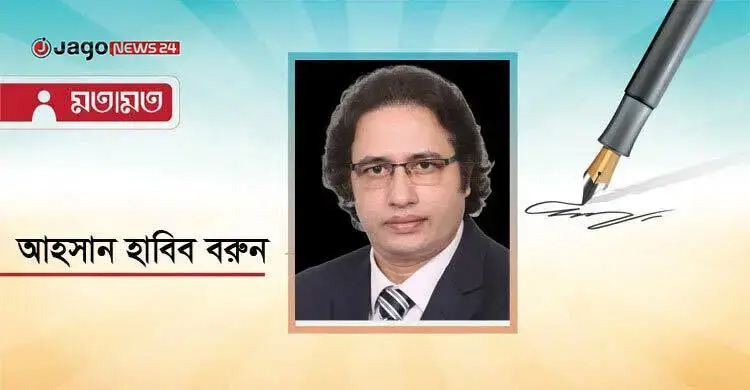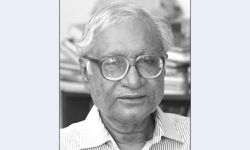নানাকালে মহাজনের নানা মুখ
সব পেশার মধ্যেই স্থান-কালের ছাপ থাকে। স্থান-কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে-ভেতরে পেশারও নানা পরিবর্তন ঘটে। পেশার ধরন বুঝতে গেলে সেই কাল ও সেই স্থানের সমাজ অর্থনীতি গঠন, সেই সঙ্গে সংস্কৃতি, আইন কাঠামো, শাসনব্যবস্থাও বিবেচনায় রাখতে হবে। সে জন্য কৌটিল্যের কালের অনেক পেশার নাম আমাদের সময়ের অনেক পেশার সঙ্গে একই রকম মনে হলেও দুইয়ের ভেতর অনেক পার্থক্য।
'মহাজন' শব্দটি সাধারণভাবে একটি পেশাগত অবস্থান নির্দেশ করে। বাংলাদেশে চলতি অর্থে শব্দটি নির্দেশ করে এমন এক জনগোষ্ঠীকে, যারা নির্যাতনমূলক অর্থ ব্যবসায়ী, সুদের কারবারি। উচ্চ হারে এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদানকারী। এ রকম গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও বহু অঞ্চলে দেখা যায়। বাংলা অঞ্চলেও এই পেশার দাপট দীর্ঘ সময় গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য মানুষের জীবনকে তছনছ করেছে। গত শতকের ত্রিশের দশকে এ অবস্থা আরও তীব্র হয়। বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সংকট সর্বব্যাপী হয়। ক্ষোভেরও বিস্তার ঘটে। চল্লিশের দশকে যখন সারা বাংলায় তেভাগা আন্দোলন চলছিল; তখন কৃষক-জনতার প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্রিটিশরাজ ছাড়াও উচ্চারিত হতো জমিদার, জোতদার ও মহাজনের নাম। সে সময়ের বহু কবিতা, পুথি, গান, যাত্রা, নাটক, পোস্টারে তাই 'মহাজন' চরিত্র পাওয়া যায়।
এখন সেই পেশার দাপট নেই, তবে তার রেশ আছে। তারই ধারাবাহিকতায় আছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সামন্তবাদী অর্থনীতিতে জমিদার ও মহাজন অবিচ্ছেদ্য। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন, গরিব কৃষকের জমি হারানো, ঋণগ্রস্ততার নির্মম জালবিন্যাসের মাধ্যমে মালিকানা স্থানান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহাজনের ভূমিকা ছিল কঠিন ও নির্মম। বাংলা সাহিত্যে মহাজনদের নিয়ে অনেক লেখা আছে, গবেষণা আছে। ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে যখন দলীয় রাজনীতির শুরু, সে সময় শোষণ-নিপীড়নে বিপর্যস্ত কৃষক সমাজের ক্ষোভের বিস্তারের প্রভাবে মহাজনবিরোধী ইস্যু রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়। একে ফজলুল হকের উদ্যোগে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন এবং ঋণের বোঝা থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষা করার কিছু ব্যবস্থার কারণে তার বিপুল জনপ্রিয়তা তৎকালীন পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে।
এরও আগে এই মহাজনি অত্যাচারে বিপর্যস্ত কৃষকদের দম ফেলার সুযোগ দিতে বাংলায় ভিন্ন ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা যায়। এর পথিকৃৎ ছিলেন আবার জমিদার পরিবারের সন্তান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে পতিসরে তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। তার উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল প্রচলিত মহাজনি সুদের হারের অনেক কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে মহাজনের একচ্ছত্র দাপট ও জাল থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। নিজে মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাংক স্থাপন করেন। কৃষকদের জন্য এখানে ঋণের সুদের হার ছিল বছরে ১২ শতাংশ, যেখানে মহাজনদের সুদের হার ছিল মাসেই ১১-১২ শতাংশ, তার ওপর তা ছিল চক্রবৃদ্ধি হারে। কবির নোবেল পুরস্কারের টাকাও এই ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এই ব্যাংকের বিস্তার না ঘটলেও এর কারণে কয়েকটি গ্রামের গরিব কৃষক নিঃস্ব হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে এই ব্যাংক টিকতে পারেনি। '৩০-এর দশকেই তা বন্ধ হয়ে যায়।
- ট্যাগ:
- মতামত
- পেশা
- সুদের ব্যবসা